ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত কী?

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী তিথি সরকারকে কারাদণ্ড দেওয়ার রায়ের পর আবারও আলোচনায় 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতে'র বিষয়টি। এই লেখার উদ্দেশ্য তিথির মামলাটি নিয়ে আলোচনা করা নয়, বরং সমস্যাটি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত আইনগুলো নিয়ে আলোচনা করা।
অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান জানানো আধুনিক সভ্যতার অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর নানা প্রান্তে, বিশেষত ইউরোপে নিরবচ্ছিন্ন ধর্মযুদ্ধ থেকে সারা বিশ্বের মানুষ অনুধাবন করেছে যে পারস্পরিক সহনশীলতার চর্চা শুরু না হলে এই সহিংসতা ও যুদ্ধের অবসান হবে না এবং মানবজাতির উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাও অর্জন হবে না। এই সহনশীলতার চর্চা শুরু হয়েছে অন্যের ধর্মবিশ্বাস ও প্রথা মেনে নেওয়ার মাধ্যমে।
আমি নিজে এবং দ্য ডেইলি স্টার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের বিপক্ষে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেকোনো ভাবেই যদি কেউ অন্য কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে তাহলে আমরা তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।
পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংস ও দীর্ঘ ধর্মযুদ্ধ ছিল প্রথম ক্রুসেড, যা পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বানে ১০৯৫ সালে শুরু হয়। তিনি খ্রিস্টানদের একতাবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের হাত থেকে জেরুজালেম শহরের দখল ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান। আমি এই ঘটনার উল্লেখ করছি যে কারণে সেটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—প্রথম ক্রুসেডের প্রথম ভুক্তভোগী ছিল ইউরোপীয় ইহুদিরা, মুসলমানরা নয় এবং ইহুদিদের ওপর হামলা চালায় খ্রিস্টান রোমান ক্যাথলিক সেনাবাহিনী।
এভাবে ইতিহাসের শুরু থেকেই দেখা গেছে যে যাদেরকে লক্ষ্য করে ধর্মের নামে যুদ্ধ শুরু করা হয়, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বদলে অন্য কোনো জনগোষ্ঠী এর ভুক্তভোগী হয়, যারা কোনোভাবেই লক্ষ্য ছিল না। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে শুরু হওয়া সংঘাতকে স্বার্থান্বেষী মহল দেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ হিসেবে এবং এতে যোগ দেয়। মানুষের আবেগ ও অন্ধ আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। মানব ইতিহাসে এই শিক্ষা বারবার প্রমাণিত হয়েছে।
'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতে'র সঙ্গে ধর্মযুদ্ধের তুলনা চলে না। তবে এসব ক্ষেত্রে পরিণতি কী হতে পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে; যার উদাহরণ আমরা দেখেছি বসনিয়া-হার্জেগোভিনা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অতীত ও বর্তমানের অসংখ্য দাঙ্গায়। প্রতিটি দাঙ্গা থেকে আরও বড় সংঘাতের স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়।
ধর্মীয় সহনশীলতা অর্জনের দুটি উপায় আছে—একটি সামাজিক এবং অপরটি আইনি।
সামাজিক উদ্যোগটি নেওয়া সম্ভব পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষা থেকে। সব ধরনের শিক্ষার শুরু হয় পরিবার থেকে। সেখানেই অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করার মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পবিত্র দায়িত্ব হলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি শিশু অবশ্যই নিজের ও অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে।
বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং এই ধর্মের মানুষ হিসেবে আমরা নিজ ধর্মবিশ্বাস নিয়ে গর্ববোধ করি। সেইসঙ্গে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে এ দেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও যেন একই অনুভূতি নিয়ে থাকতে পারেন। প্রতিটি হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস নিয়ে গর্ববোধ করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এমন একটি সহনশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে সব ধর্মবিশ্বাসের মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং সহজে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। এটাই ধর্মীয় সহনশীলতার মূলনীতি এবং সমাজের সবাইকে এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। এটা একইসঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ, সংবিধান এবং নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রেরও ভিত্তিমূল। আর এসব কিছুই শুরু হতে হবে পরিবার থেকে।
এরপর আসবে সমাজের প্রসঙ্গ। প্রতিটি সমাজে ধর্মীয় সহনশীলতার মূল্যবোধকে প্রথায় রূপান্তর করতে হবে। আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে যে ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ আর ধর্মীয় উগ্রতা কোনোভাবেই এক জিনিস নয়। নিজের ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করা খুবই স্বাভাবিক এবং এতে আপত্তিরও কিছু নেই। কিন্তু সেই গর্ব যখন এমন এক বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়, যার ফলে অবচেতন মনেই অন্য ধর্মকে নিচু দৃষ্টিতে দেখতে শেখায়, তখনই ধর্ম নিয়ে গর্ব পরিণত হয় ধর্মীয় উগ্রতায়। এভাবেই বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন না থেকেও আমরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ি।
ধর্মীয় সহনশীল সমাজ সৃষ্টির তৃতীয় উপকরণ হলো শিক্ষা। এ ক্ষেত্রে আমাদের সর্বশেষ প্রণীত শিক্ষা নীতিমালা ২০২১ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। 'ধর্মীয় শিক্ষা' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজ ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, যাতে তারা যথাযথভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে এবং ধর্মে যা বলা আছে, তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে।
নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদের জানতে হবে যে কীভাবে অন্য ধর্মের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো যায়। এতে করে এমন একটি সমাজ তৈরি হবে যেখানে জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।
শিক্ষা নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, নিজের ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত সত্যগুলো জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে কেউ অযাচিত বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কাউকে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে।
সহনশীলতা, সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ধর্মীয় সহনশীলতার বিষয়টি এখন বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখছি, সারা বিশ্বে গোত্র, বর্ণ, জাত ও ধর্মভিত্তিক সংকীর্ণ মানসিকতা, বৈষম্য ও ঘৃণা বাড়ছে। প্রায়শই উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসকে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে কার্যত অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। যার ফলে, সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে এবং এখনই সংঘাতে না জড়ালেও ভবিষ্যতে অস্থিরতা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।
সবশেষে রয়েছে ধর্মীয় অনুভূতিতে 'আঘাত হানা' প্রতিরোধে আইনি কাঠামো তৈরি। এমন কোনো নতুন আইন তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আইনটি সুস্পষ্ট এবং এই আইন নিয়ে কোনো ধরনের দ্বিধা সৃষ্টির সুযোগ নেই।
এ ক্ষেত্রে আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) নিয়ে আলোচনা করতে পারি, যে আইনের বিষয়ে আমাদের অনেক আপত্তি ছিল। হ্যাঁ, এই আইনের নতুন সংস্করণ সাইবার নিরাপত্তা আইনে (সিএসএ) সাংবাদিকদের কিছুক্ষেত্রে রেহাই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বিষয়টি নিয়ে অস্পষ্টতা থেকে যাওয়ায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব সাংবাদিকতার ওপর পড়ছে। এই আইনে 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত'র স্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।
একটি আইন তখনই অর্থবহ হয় যখন এর সংজ্ঞাগুলো সুস্পষ্ট হয় এবং এর লঙ্ঘন কীভাবে হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়। একজন নাগরিকের স্পষ্ট ধারণা পেতে হবে যে তার সীমা কতটুকু এবং কী করলে আইন লঙ্ঘন হবে। অস্পষ্ট হলে আইনের অপব্যবহার হতে পারে, এমনকি এটাকে অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা হতে পারে।
সাইবার নিরাপত্তা আইনে বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করিবার বা উসকানি প্রদানের অভিপ্রায়ে ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এইরূপ কিছু প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করান, যাহা ধর্মীয় অনুভূতি বা ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।'
'আঘাত'র বিষয়টি কীভাবে নির্ধারণ করা হবে? এটা নিশ্চিতভাবেই ব্যক্তি ও প্রেক্ষাপট ভেদে আলাদা হবে। একটি যৌক্তিক ও আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ প্রশ্নও কাউকে আঘাত করতে পারে। কোনো 'পীর', ইমাম অথবা ধর্মগুরু বা ধর্মীয় শিক্ষকের সমালোচনা করলে কি সেটা ধর্মীয় অনুভূতিতে 'আঘাত' হিসেবে বিবেচিত হবে? এ ক্ষেত্রে সমালোচনা করলে তাদের একনিষ্ঠ ভক্তরা 'আঘাত' পেতে পারেন এবং মামলা করতে পারেন।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির অনেক উদাহরণ রয়েছে। এসব দুর্নীতি প্রকাশ করলে কি ধর্মীয় অনুভূতিতে 'আঘাত' করা হবে? কোনো গণমাধ্যম যদি মসজিদ, মাদ্রাসা বা অন্য কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তাহলে কি সিএসএ আইনে মামলা হবে? এক কথায়, আইনটির এই অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়নি খুব সহজেই সেক্ষেত্রেও ব্যবহার করা সম্ভব।
আমরা চাই না কারো ধর্মীয় অনুভূতি আঘাত আসুক। একইসঙ্গে আমরা এটাও চাই না যে এর মাধ্যমে গবেষণা, যৌক্তিক সমালোচনা, গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা এবং অবশ্যই, অনিয়ম-অন্যায়কে প্রকাশ্যে নিয়ে আসার উদ্যোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হোক।
'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে সতর্ক করে আলোচনা শেষ করতে চাই। সাধারণত একটি দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠদের আবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এসব বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ক্ষেত্রে যতটা দ্রুত ও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়, সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে তা হয় না।
বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য বর্তমান সময়ের ভারতের উদাহরণ দেখা যেতে পারে। সেখানে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের ঘটনায় ন্যায়বিচার পেতে হিন্দুদের কতটা সময় লাগতে পারে আর মুসলিমদের কতটা সময় লাগতে পারে? এই বিপরীত অবস্থা যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হলে এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাবের বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে এবং এ দেশে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়ানো যাবে।
মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার
ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান





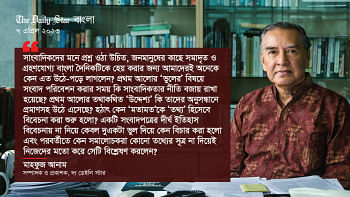





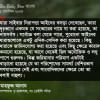



Comments