ছাত্রদের নতুন দলকে কত শতাংশ মানুষ ভোট দেবে?
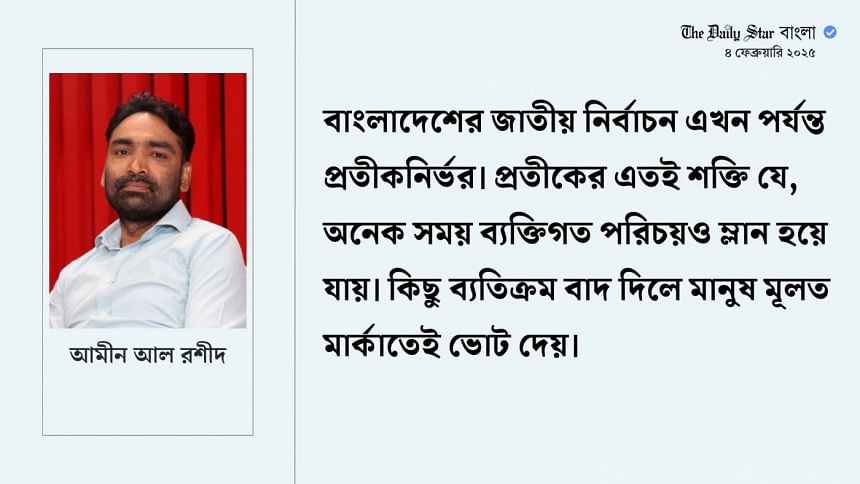
জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে গড়ে ওঠা জাতীয় নাগরিক কমিটির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এ মাসেই একটি নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।
সেই দলের নাম কী হবে, দলের প্রধান কে হবেন—তা নিয়ে রাজনীতির মাঠে নানা আলোচনা আছে। অনেকে বলছেন, এটি হবে আরেকটি 'কিংস পার্টি'। পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলা হয়, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিও কিংস পার্টি। কেননা এই দুটি দলও গঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে এবং দল গঠিত হওয়ার পরেই যে নির্বাচন হয়েছে, তাতে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে।
সুতরাং কিংস পার্টি হলেই যে জনগণ তাদের ভোট দেবে না বা তারা সরকার গঠন করতে পারবে না, তা নয়।
এক-এগারোর সরকারের সময়েও কিছু 'কিংস পার্টি' হয়েছিল। কিন্তু তার একটিও পরবর্তীতে দেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকেনি। পক্ষান্তরে নানা অত্যাচার-নিপীড়নের পরেও বিএনপি এখনও প্রাসঙ্গিক।
জাতীয় পার্টির জনপ্রিয়তা বেশ কমলেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। তার কারণ, দীর্ঘদিন সরকারে ও বিরোধীদলে থাকায় দুটি দলেরই জনভিত্তি তৈরি হয়েছে। সুতরাং এখন আর বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে 'কিংস পার্টি' বলার সুযোগ নেই।
বাংলাদেশের মানুষ প্রথম একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও তুলনামূলক ভালো নির্বাচনের স্বাদ পায় ১৯৯১ সালে। কেননা এই প্রথম একটি জাতীয় নির্বাচন হয় নির্দলীয় সরকারের অধীনে। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দল ভোটের মাঠে কোনো বাড়তি সুবিধা পায়নি।
এরপর ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচন নিয়েও মোটা দাগে সমালোচনা কম। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম সংসদ নির্বাচনটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলেও পরবর্তীতে অনেকেই এই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সে কারণে ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনকে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় তুলামূলক ভালো নির্বাচন বলে মনে করা হলে এই তিনটি নির্বাচনে দেশের প্রধান চারটি দল (বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলাম) কী পরিমাণ ভোট পেয়েছে—সেটি দিয়ে দলগুলোর জনপ্রিয়তা মাপা যায়।
সেই হিসাবে অনেকেই মনে করেন, বাংলাদেশে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ভোট কাছাকাছি। অর্থাৎ দুটি দলেরই ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ ভোট রয়েছে। বাকি ভোট অন্যান্য দলের। কিছু ভোটার সুইং। মানে তারা কোনো দলের ফিক্সড ভোটার নন।
গত বছরের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্বতনের পরে আওয়ামী লীগের ভোট অনেক কমেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু তারা যদি আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে এবং যদি একটি অবাধ-সুষ্ঠু-গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন না হয়, তাহলে বোঝা যাবে না যে তাদের ভোট বা জনসমর্থন সত্যিই কমেছে না বেড়েছে।
ধরা যাক, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারলো না বা তাদেরকে অংশ নিতে দেওয়া হলো না। তাহলে তাদের ভোটাররা কোথায় যাবেন? তারা কি ভোটদানে বিরত থাকবেন? নাকি বিএনপিকে ভোট দেবেন? নিশ্চয়ই তাদের ভোট জামায়াত কিংবা ছাত্রদের দলকে দেবেন না। কারণ, ছাত্ররাই আওয়ামী লীগ পতনের আন্দোলনে সম্মুখ সারিতে ছিলেন।
বিএনপির যদি ৩০ শতাংশ ভোট থাকে, সেই ভোটের একটিও ছাত্রদের দলের পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার মানে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ ভোট যদি থাকে, তার বাইরের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট নিয়ে কথা বলতে হবে। এই ভোটের সব একটি দল পাবে না।
তাহলে কি ছাত্রদের দল এবং জুলাই অভ্যুত্থানে সক্রিয় জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামিক দল, এমনকি বিএনপির বাইরে আরও যেসব দল সক্রিয় ছিল, তারাও ছাত্রদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হবে? জোটবদ্ধ হলেই কি তারা বিএনপির চেয়ে বেশি আসন পাবে?
অনেকে মনে করেন, আওয়ামী লীগের ভোটার হলেও যারা বিগত দিনে আওয়ামী লীগের নানাবিধ কাজে বিরক্ত, বিশেষ করে গত বছরের জুলাই-আগস্টে সরকার যেভাবে আন্দোলন দমন করতে চেয়েছে; যেভাবে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছেন, তাতে আওয়ামী লীগের অনেক ভোটার কমেছে। যদি তাই হয়, তাহলে এই মানুষগুলো কি ছাত্রদের দলকে ভোট দেবে? তারা কি কোনো ইসলামিক দলকে ভোট দেবে নাকি বিএনপিকে?
এটি নির্বাচনের সাধারণ অংকের প্রশ্ন। কিন্তু দেশে যে একটি বিরাট অভ্যুত্থান হয়ে গেল, তারপরে কি আগামী নির্বাচনের অংক ও সমীকরণ আগের মতোই স্বাভাবিক হিসাবে চলবে? নির্বাচনটি কি আদৌ অবাধ-সুষ্ঠু-সরকারি প্রভাবমুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য হবে?
গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীরা যদি রাজনৈতিক দল গঠন করে, সেই দলকে ৪০ শতাংশ মানুষ ভোট দেবেন। আর শিক্ষার্থীদের দলকে ভোট না দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৪৪ শতাংশ মানুষ। বাকি ১৬ শতাংশ মানুষ এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) 'পালস সার্ভের' দ্বিতীয় ধাপের জরিপের ফলাফলে এমন চিত্র দেখা গেছে।
গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশে (পিআইবি) বিআইজিডির একটি অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ১৫ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত চালানো জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, জরিপে অংশ নেওয়া ৩৮ শতাংশ মানুষ তখন পর্যন্ত কাকে ভোট দেবেন বা ভোট দেবেন কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেননি। যারা ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই বাকি ৬২ শতাংশ মানুষের মধ্যে ৪০ শতাংশ মানুষ বলেছেন, গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীরা যদি রাজনৈতিক দল গঠন করেন, সেই দলকে তারা ভোট দেবেন। এ ছাড়া, ১৬ শতাংশ বিএনপিকে, ১১ শতাংশ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে এবং ৯ শতাংশ ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগকে, ৩ শতাংশ মানুষ অন্যান্য ইসলামী দল ও এক শতাংশ জাতীয় পার্টিকে ভোট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।
এখানে কয়েকটি প্রশ্ন—
১. জুলাই অভ্যুত্থানের দুই মাস পরে ছাত্রদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের যে মানসিকতা বা তাদের যে জনপ্রিয়তা ছিল, তা কি এখন আছে? এখন যদি এই একই জরিপ পুনরায় চালানো হয়, তাহলে ফলাফল কী আসবে?
২. ৪০ শতাংশ মানুষ ছাত্রদের দলকে ভোট দেবেন—এটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য বা বাস্তবসম্মত? তারচেয়ে বড় প্রশ্ন, মাত্র ১৬ শতাংশ মানুষ বিএনপিকে ভোট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। অথচ বিএনপির অন্তত ৩০ শতাংশ ভোট আছে বলে মনে করা হয়। তাহলে বিএনপির বাকি ভোট কোথায় গেলো? বিএনপির ভোট কি কমেছে? ১১ শতাংশ মানুষ জামায়াতকে ভোট দেবে—সেটিও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা তাদের এত ভোট নেই।
৩. ছাত্রদের সম্ভাব্য দল বা তাদের জনপ্রিয়তা প্রমাণের জন্যই কি এই জরিপটি চালানো হয়েছে?
বস্তুত যেকোনো জরিপ নিয়েই নানাবিধ প্রশ্ন তোলা যায়। অনেক সময়ই জরিপের সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল থাকে না। কিন্তু এ মুহূর্তে বড় প্রশ্ন হলো জাতীয় নির্বাচনটি কবে হবে?
বিএনপি চাইছে আগামী ৫ আগস্ট নির্বাচন দিয়ে শেখ হাসিনার পতনের তারিখ স্মরণীয় করে রাখতে। কিন্তু আগস্টে নির্বাচন হবে না—প্রথমত, সরকার চায় না বলে; দ্বিতীয়ত, তখন বৃষ্টি-বন্যার মৌসুম। বরং এই বছরের ডিসেম্বর সামনে রেখে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন—এরকম কথা বলা হচ্ছে।
কিন্তু মনে রাখতে হবে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্য দুটি সময়ের কথা বলেছেন—এ বছরের ডিসেম্বর অথবা আগামী বছরের জুন।
বাস্তবতা হলো, যদি নির্বাচন এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে না হয়, তাহলে নির্বাচনটি আগামী বছরেরও জুনেও হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেননা তখন আবার বৃষ্টির মৌসুম চলে আসবে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনটি চলে যাবে আগামী বছরের শেষদিকে।
প্রশ্ন হলো, বিএনপি কি নির্বাচনের জন্য এতদিন অপেক্ষা করবে বা এটি মানবে? বিএনপি না মানলে কী হবে বা তারা কী করবে? তারা কি সরকার পতনের আন্দোলনে নামবে বা সব রাজনৈতিক দল কি দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির সঙ্গে মাঠে আন্দোলন শুরু করবে? সেই সম্ভাবন ক্ষীণ। কারণ, দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি যতটা সোচ্চার, জামায়াতসহ অন্যান্য দলগুলো ততটা সোচ্চার নয়।
অন্তর্বর্তী সরকার যে দ্রুত নির্বাচন দিতে চায় না, সেটি তাদের কথাবার্তায় স্পষ্ট। বরং তাদের অগ্রাধিকার জুলাই অভ্যুত্থানে হত্যা, গণহত্যাসহ নানা অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ ও তাদের নেতাদের বিচার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। নির্বাচন তাদের তিন নম্বর এজেন্ডা। ফলে আগামী ৬-৭ মাসের মধ্যে নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না, যদি বড় কোনো ঘটনা না ঘটে।
তবে এটা ঠিক, নির্বাচনের তারিখ নিয়েই বিএনপির সঙ্গে সরকারের দূরত্ব বাড়বে। তার বিপরীতে ছাত্রদের গঠিত রাজনৈতিক দল নতুন মেরুকরণ তৈরি করতে পারবে কি না—সেটিই দেখার বিষয়।
২.
যেকোনো রাজনৈতিক দলের সফলতা অনেকটা নির্ভর করে দলীয় প্রধানের ওপর। বিএনপি ও জাতীয় পার্টি দল গঠনের পরপরই ক্ষমতায় আসতে পেরেছিল, কারণ তাদের প্রধানই নির্বাচনের আগে নানাবিধ কাজ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এবং সেইসঙ্গে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করায় তাদের দল নানাবিধ সুবিধা পেয়েছে।
কিন্তু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যরা যে দলটি গঠন করবেন বলে শোনা যাচ্ছে, তার নেতৃত্ব কে দেবেন? দেশের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা কেমন হবে? জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন—শুধুমাত্র এই পরিচয়ের কারণেই জাতীয় নির্বাচনে সাধারণ মানুষ এই দলের নেতাদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে—ব্যাপারটি কি এত সহজ হবে?
জিয়াউর রহমান এবং এইচ এম এরশাদ—দুজনেরই সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল। তারা সহজেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারতেন। ফলে তারা যে দুটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেখানে তাদের ব্যক্তিগত ইমেজ বা ক্যারিশমার বিরাট ভূমিকা ছিল। এরশাদকে স্বৈরাচার বলে গালি দেওয়া হলেও তার জনপ্রিয়তাও ছিল—এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। সুতরাং ছাত্ররা যে দলটি করবেন, তার প্রধান কে হবেন, সেটি বিরাট প্রশ্ন।
এই দলের শীর্ষ নেতৃত্বে কারা থাকবেন, সেটি মোটামুটি ধারণা করা যাচ্ছে। যেমন: জুলাই অভ্যুত্থানে সামনের সারিতে থাকা হাসনাত আব্দুল্লাহ, সারজিস আলম, আখতার হোসেনরা এই দলের শীর্ষ পদে থাকবেন। সেইসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের তিনজন ছাত্র উপদেষ্টাও এই দলে যুক্ত হতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে।
ছাত্ররা মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন, যেহেতু তারা একটি বড় অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, অতএব একটি দল গঠন করে সেটিকে বিএনপির মতো বড় দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তৈরি করার সক্ষমতা তাদের রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আন্দোলন করে সরকার হটানো আর নির্বাচনে সরকার গঠনের মতো আসন পেয়ে জয়ী হওয়া এক নয়।
বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন এখন পর্যন্ত প্রতীকনির্ভর। প্রতীকের এতই শক্তি যে, অনেক সময় ব্যক্তিগত পরিচয়ও ম্লান হয়ে যায়। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে মানুষ মূলত মার্কাতেই ভোট দেয়। সুতরাং আগামী নির্বাচনে প্রধান ফ্যাক্টর যদি বিএনপি, তথা তাদের প্রতীক ধানের শীষকে ধরা হয় এবং আওয়ামী লীগ যদি মাঠে না থাকে, তাহলে তার বিপরীতে জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা, ইসলামি আন্দোলনের হাতপাখা কিংবা ছাত্রদের নতুন দলের নতুন প্রতীক কতটা প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরি করতে পারবে, তা বলা কঠিন।
নির্বাচন যদি অবাধ-সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে বিএনপিকে হারিয়ে অন্য কোনো দলের সরকার গঠনের সম্ভাবনা কম। আবার দেশের মানুষ যদি মনে করে যে, তারা তিনটি দলকে দেখেছে, সেনা শাসনও দেখেছে—অতএব তারা এবার পরিবর্তন চায়; তরুণরা যদি সেই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সত্যিই জনমনে গেঁথে দিতে পারে এবং তাদের আচরণ, কথাবার্তা, শারীরিক ভাষা ও কর্মকৌশল দিয়ে নির্বাচন পর্যন্ত সেই জোয়ার ধরে রাখতে পারে, তাহলে হয়তো নতুন কিছু ঘটবে।
সুতরাং আগামীতে কী হবে, সেটি মোটামুটি আন্দাজ করা গেলেও উপসংহারে পৌঁছানো কঠিন। কেননা নির্বাচন কবে হবে—এই ইস্যুতেই সামনের দিনগুলোতে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হবে এবং সরকার সেই পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করবে, তার ওপর নির্ভর করছে রাজনীতির গতিপথ।
আমীন আল রশীদ: সাংবাদিক ও লেখক










Comments