জীবনের ছন্দ কোথায়
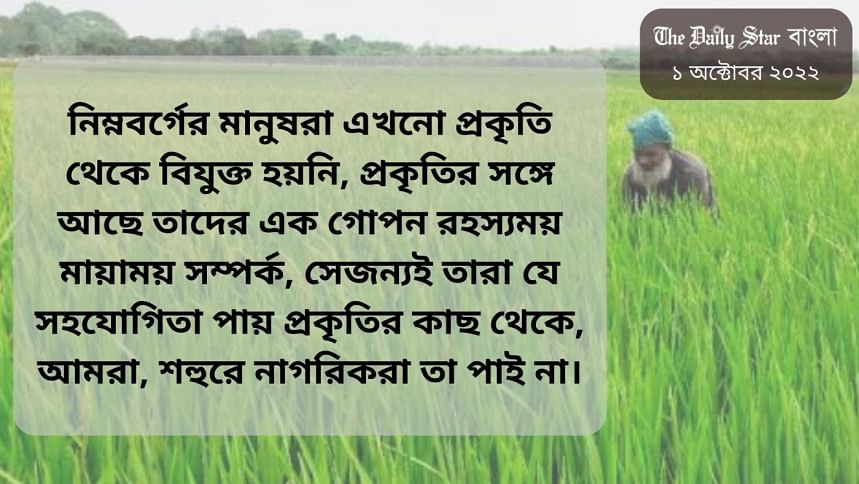
গুন্টার গ্রাসের একটা চমৎকার বই আছে : 'শো ইওর টাং' ('জিভ কাটো লজ্জায়')। এক বছর কলকাতায় থাকবেন বলে সস্ত্রীক তিনি চলে এসেছিলেন জার্মানি থেকে, কিন্তু সম্ভবত মাস চারেকের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, ফিরে গিয়েছিলেন নিজ দেশে। এই বই তার কলকাতা-যাপনের অপূর্ব বর্ণনা। তখনও নোবেল পুরস্কার পাননি তিনি, তবু বিশ্ববিখ্যাত লেখক। কলকাতায় থাকার জন্য এবং এই শহরবাসীর জীবন দেখার জন্য তার কৌতূহল এবং আগ্রহ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সত্যিই তার সস্ত্রীক চলে আসার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আমাদেরকেও কৌতূহলী করে তোলে। কী দেখতে চেয়েছিলেন তিনি আর কী-ইবা দেখেছেন?
কলকাতায় এসে তারা বাসা নিয়েছিলেন শহরের বাইরে, প্রতিদিন লোকাল ট্রেনের ভিড়ে যাতায়াত করার অভিজ্ঞতা নেবেন বলে। ঘুরে বেড়িয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মাদ্রাজের নানা প্রান্ত। একবার ঢাকায় এসেও ঘুরে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন কলকাতায় এবং তার আশেপাশে। সেখানে মানুষের দুর্দশা, দুরবস্থা আর অমানবিক জীবন-যাপন দেখে তার মনে হয়েছিল, পুরো ইউরোপের লজ্জায় জিভ কাটা উচিত। সেই সভ্যতার কী মূল্য যেখানে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষের জীবন এত বিভীষিকাপূর্ণ? মা কালীর সেই জিভ কাটা মূর্তি দেখে তার মনে হয়েছিল, মানবতার এই বিপর্যয়ে লজ্জা পেয়েই তিনি জিভে কামড় দিয়ে আছেন।
কালীদেবীর এই মূর্তিটি যে তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তা বোঝা যায় বইয়ের বিভিন্ন অংশে বিষয়টির একাধিক উল্লেখ দেখে এবং বইটির নামকরণ দেখে। তিনি কেন জিভে কামড় দিয়ে আছেন তার পৌরাণিক ব্যাখ্যা তিনি জানতেন, সেটি উল্লেখও করেছেন, কিন্তু ওই যে তার লেখক-মন, সেটি তাকে এটা ভাবতে প্রলুব্ধ করেছে যে, মানুষের দুঃসহ গ্লানি-বেদনা-হাহাকার-অপমানের লজ্জাই তাকে জিভ দংশন করতে বাধ্য করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি মহান পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সেই জিভ বের করা অদ্ভুত ছবিটির কথাও উল্লেখ করেছেন। হয়তো আলোকচিত্রশিল্পীরা তাকে প্ররোচিত করেছিলেন ওরকম ভঙ্গি করতে, নইলে তিনি ওরকম বিকটভাবে জিভ বের করে ছবি তুলবেন কেন? অথবা, কে জানে, হয়তো তিনি নিজে থেকেই ওরকম করেছিলেন! গুন্টার গ্রাস সেই ছবিটি সম্বন্ধে লিখেছেন : 'আবর্জনাপ্রেমী যে মানুষগুলো স্বরচিত জঞ্জালের মধ্যে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে তাদের কারণে সঞ্চারিত লজ্জাই আইনস্টাইনকে জিভ দংশনে বাধ্য করেছে।'
অত্যন্ত সুলিখিত বইটি পড়ার পর আমার মনে হয়েছিল, গুন্টার গ্রাসের দেখার চোখ অতি তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ণ, কোনোকিছুই চোখ এড়িয়ে যায় না তার, এবং বর্ণনাভঙ্গিও অসামান্য সুন্দর। একটা ছোট্ট উদ্ধৃতি দিই :
'পোস্টার রাখবার স্ট্যান্ডের পাশে খোয়ার একটা ঢিবির ওপর নিষ্কর্মা লোকগুলো উবু হয়ে বসে আছে। হাতদুটো ঝুলছে নয়তো জড়োসড়ো করে রাখা। গোড়ালিতে নিশ্চিন্তে ভর দিয়ে বসে আছে। ওদের মুখের মধ্যে যে ভাবটা ফুটে উঠেছে সেটা ধৈর্য নয়, কারণ ধৈর্যধারণ করবার দরকার হলেও সেক্ষেত্রে মানুষের কোনো না কোনো অভীষ্ট লক্ষ্য থাকে। ওদের কোনো লক্ষ্য নেই, ওরা গতানুগতিক অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে, আবহাওয়ার কাছে মানুষকে যেমন সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হয়, তেমনি। এইরকম কতগুলো লোক যখন বটগাছের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে থাকে তখন তাদের দেখে অবধারিতভাবে মনে হবে তারা যেন বটগাছেরই বাতাসে ছড়ানো শিকড়। আমি ছবি আঁকি। হাঁটু মুড়ে বসা অপেক্ষমাণ মানুষ, জঞ্জালের পাহাড়ে মানুষ, গাছের তলায় মানুষ।'
কী সুন্দর বর্ণনা! কিন্তু এই জীবনের ছন্দ কোথায়, এরা কী নিয়ে বাঁচে- এই প্রশ্ন যদি করি, অবধারিতভাবে কেউ বলে উঠবে, এখানে জীবনই বা কোথায়? এ তো এক স্তব্ধতা, এক স্থিরচিত্র, বটগাছের শিকড়। জীবন তো থেমে গেছে এখানে।
আসলেই কি থেমে গেছে জীবন? যায় কখনো? এরকম তো আমরাও দেখি অহরহ, শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে। দেখি স্তব্ধ মানুষ, অলস মানুষ, কর্মহীন মানুষ, নৈরাশ্যপীড়িত মানুষ, রোগাক্রান্ত মানুষ। এবং মনে মনে ভাবি, এদের কোনো জীবন নেই। সত্যিই নেই? নাকি আছে ঠিকই কিন্তু আমাদের দেখার চোখ নেই?
তিনি যখন লেখেন : 'সবসময় দেখতে পাই ফুটপাতের পাড়ে বসে বুড়িগুলো সারাক্ষণ হয় বোতল পরিষ্কার করছে না হয় সারাদিন কারো জন্যে হাপিত্যেশ করে বসে আছে। যেন সময় বলে আদৌ কিছু নেই।' তখন বোঝাই যায়, সংবেদনশীল লেখকের মন কেঁদে উঠেছিল এইসব মানুষের জীবন দেখে। কিন্তু তবু, পড়া শেষে আমার মনে হয়েছিল, গুন্টার গ্রাস একটা ব্যাপার বোধহয় ধরতে পারেননি। নিজেকে প্রশ্ন করেননি, এত গ্লানি, এত বিপর্যয়, এত দুর্দশা নিয়েও মানুষ হাসে কীভাবে, প্রেম করে কীভাবে, উৎসব করে কীভাবে, জীবনকে উদযাপন করে কীভাবে? মানে প্রাণের স্পন্দনটা তিনি খুঁজে পাননি। অর্থাৎ ওই নোংরা-ঘিঞ্জি-দরিদ্র শহরটির বাসিন্দাদের জীবনের ছন্দটি আবিষ্কার করতে পারেননি।
না, তাকে দোষ দিচ্ছি না, এই সমস্যা তার একার নয়, আমাদেরও এবং আমারও। কলকাতার জীবনকে আমি এমনিতেও চিনি না, কিন্তু ঢাকার কথা যখন ভাবি, কিংবা আরেকটু বড় করে বাংলাদেশের কথা, বুঝতেই পারি না, এত দারিদ্র এত হতাশা এত অনিশ্চয়তা নিয়ে এই দেশের মানুষ বাঁচে কী করে? কেবল যে বাঁচে তাই নয়, ভীষণভাবে বাঁচে; স্বপ্ন দ্যাখে, প্রেমে পড়ে, গান শোনে, গান গায়, হাসিমুখে ফসল ফলায়, সন্তানের জন্ম দেয়, অপত্য স্নেহে তাদের লালনপালন করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কোথাও কোনো ঘাটতি নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের জীবনই তো এরকম। গৌরবহীন অতীত, ম্লান-অনুজ্জ্বল বর্তমান, অন্ধকারাচ্ছন্ন-অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তবু তারা বাঁচতে চায় এবং বাঁচে, জীবনকে কেবল যাপনই করে না, নিজেদের মতো করে উদযাপনও করে। কীভাবে করে, আমরা সেই রহস্য বুঝে উঠতে পারি না।
মনে পড়ে, প্রায় বছর-বিশেক আগে, হবিগঞ্জ শহরে যাচ্ছিলাম ওখানকার এক সাহিত্য-উৎসবে যোগ দিতে। ঢাকা থেকে দশ-বারোজনের একটা দল রওনা দিয়েছি। সেই দলে হাসান আজিজুল হক, মোহাম্মদ রফিকের মতো অগ্রজরা যেমন আছেন তেমনই শামীম রেজা বা আমার মতো তরুণরাও আছেন। ট্রেনের শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কম্পার্টমেন্টে বসে তুমুল আড্ডা জমিয়ে আর বাইরের অপূর্ব সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের মন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। আমি বসেছিলাম হাসান আজিজুল হকের পাশে। আড্ডা একটু থিতিয়ে এলো একসময়। দেখলাম দিগন্ত-বিস্তৃত ফসলের মাঠের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন তিনি। সত্যি বলতে কি আমিও চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। দ্রুতগামী ট্রেন থেকে কোনো দৃশ্য স্থিরভাবে দেখার উপায় নেই, সবই অপসৃয়মান, তবু চোখে পড়ছিল, ফসলের মাঠে কৃষকরা কাজ করছেন, হয়তো ফসলের পরিচর্যা করছেন তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে, সেইসব দৃশ্যও অতি মনোহর বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু একটু আগেই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই কক্ষ থেকে বেরিয়েছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে। তখন দেখেছি, বাইরে প্রচণ্ড রোদ আর গরম, লু হাওয়া বইছে হুহু করে, যেন শরীর পুড়িয়ে দেবে এমন জেদি ভঙ্গিতে। ওরকম রোদে, গরমে, লু হাওয়ার ভেতরে কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে না কৃষকদের? হঠাৎ মনে হলো, হাসান আজিজুল হকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একটু আলাপ করা যাক।
আলাপ হলো অনেকক্ষণ ধরে। দৃশ্যগুলো যে মনোহর, চোখ আর হৃদয় জুড়িয়ে যায়, এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হলেন তিনি। অত রোদে আর গরমে যে কৃষকদের কষ্ট হচ্ছে, তাও স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু আনন্দও কি নেই তাদের? মাঠভরতি বাড়বাড়ন্ত ফসলের সমাহার তাদেরকে কি সন্তানদের বড় করে তোলার আনন্দও দিচ্ছে না? এই প্রশ্নে তিনি নিরুত্তর থেকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন, এরপর কোনো একটা মারাত্নক মন্তব্য করতে যাচ্ছি আমি। তাকে বললাম, আমার কী মনে হয় জানেন, হাসান ভাই? মনে হয়, আমাদের সাহিত্যচর্চা আসলে এইরকমই, এই যে এসি কম্পার্টমেন্টে বসে কৃষকদের জীবন দেখার সাহিত্য। ওখানে দেখাটা আছে, তাও বহুদূর থেকে, যাপনটা নাই। মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুম থেকে নিম্নবিত্তের জীবনের খুব সামান্যই দেখা যায়, আমরা ওটাকেই সাহিত্য করে তুলি। তাদের যাপনের কথা আসলে আমরা জানি না। তিনি বললেন, কেন এরকম মনে হয় তোমার? বললাম, ধরুন আপনার গল্পের কথাই। পড়লে মনে হয়, এ জগতে ফুল ফোটে না, পাখিরা গায় না, শিশুরা হাসে না, মানুষ সংসারযাপন করে না। জীবন কি সত্যিই এরকম? তিনি বললেন, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো। তবে এখন নয়।
উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। সেই সাহিত্য-উৎসবে বক্তৃতায় আমি ফের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলাম, আর তিনি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কথা বলেছিলেন বিষয়টি নিয়ে। যা বলেছিলেন, তার মোদ্দাকথা হলো এই যে, আমি সব মানুষের জন্য মুক্ত জীবন চাই। সেই কারণেই বর্তমানের প্রচণ্ড ধ্বংসের ছবি আঁকি।
এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি। হ্যাঁ, আমি প্রচণ্ড ধ্বংসের ছবি আঁকতেই পারি। পাঠককে বলতেই পারি, এই জীবন আমাদের কাম্য হতে পারে না, একে বদলাতে হবে। কিন্তু মুশকিল হলো, গল্প লিখে কিছু বদলানো যায় না। তারচেয়ে বরং চোখের কোণে একটু মায়া থাকা ভালো, একটু আর্দ্রতা থাকা ভালো। বলেছিলাম তাকে এই কথা।
যাহোক, এতক্ষণ ধরে এত কথা বললাম এইটুকু বোঝানোর জন্য যে, নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে ছন্দটা কোথায় থাকে, কোথায় লুকিয়ে থাকে আনন্দ-সূত্র, বেঁচে থাকার সূত্র, তা আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি বোধহয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের যে নিবিড়-অলিখিত-দিব্যকান্তি সম্পর্ক, সেটির মধ্যেই লুকানো আছে এইসব সূত্র।
কথাটি কেবল গ্রামের মানুষের কথা ভেবে বলিনি। শহরের বস্তিগুলোতে বা সেইসব এলাকায় যেখানে নিম্নবর্গের মানুষের বসবাস, পরিবেশ এতই অস্বাস্থ্যকর এবং অমানবিক- সুপেয় পানি নেই, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নেই, পুষ্টিকর খাবার নেই, পরিচ্ছন্ন ঘর নেই - যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের পক্ষেও বোঝা সম্ভব নয়, মানুষগুলো বেঁচে আছে কী করে?
একটা উদাহরণ দিই। করোনা মহামারির সময় স্বাস্থ্যবিধির নামে যেসব অদ্ভুত নিয়মকানুন জারি করা হয়েছিল- সামাজিক দূরত্ব, সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়া, পরিচ্ছন্ন থাকা, কেউ আক্রান্ত হলে আইসোলেশনে রাখা ইত্যাদি- তার কোনোটিই বস্তিবাসীদের পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না। এও আশঙ্কা করা হয়েছিল, এরকম ঘিঞ্জি এক দেশ, গায়ে গা লাগিয়ে মানুষ বাস করে, এখানে হয়তো হাজার হাজার মৃতদেহ পড়ে থাকবে রাস্তায়। সেরকম কিন্তু ঘটেনি। বস্তিবাসীদের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি কিংবা হলেও তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে সুস্থ হয়ে উঠেছে। গ্রামেও সেরকমই ঘটেছে।
এই যে এক ভয়ংকর মহামারিকে ঠেকিয়ে দিলো বস্তিবাসী কোনোরকম স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই, ঘিঞ্জি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গায়ে গা লাগিয়ে বসবাস করেও, স্বাস্থ্য বিভাগের কোনোরকম সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই, কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করলো তারা আমারা তো তা ভেবেই দেখিনি। এত করুণ জীবন-যাপন করেও তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল মানুষদের চেয়ে কেন বেশি, এ নিয়েও হয়নি কোনো গবেষণা।
আমি দারিদ্রকে মহিমান্বিত করছি না, শুধু বলতে চাইছি, নিম্নবর্গের মানুষরা এখনো প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত হয়নি, প্রকৃতির সঙ্গে আছে তাদের এক গোপন রহস্যময় মায়াময় সম্পর্ক, সেজন্যই তারা যে সহযোগিতা পায় প্রকৃতির কাছ থেকে, আমরা, শহুরে নাগরিকরা তা পাই না। আমিও মনে-প্রাণে চাই, তাদের জীবন থেকে দারিদ্রের অভিশাপ কেটে যাক, সচ্ছল-সুন্দর জীবন পাক তারা, সেইসঙ্গে তারা নিয়ে আসুক প্রকৃতির সঙ্গে তাদের দিব্যকান্তি সম্পর্কের গোপন সূত্রাবলী। ছড়িয়ে দিক সবখানে। বিচ্ছিন্নতা নয় বরং প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েই আমরা ফের ফিরে পাবো এক সহজ-নিরুদ্বেগ জীবন আর সেই জীবনে ফিরে আসবে হারিয়ে ফেলা সুর ও ছন্দ।










Comments