বর্তমান পাঠ্যক্রম এবং আমার কিছু মতামত
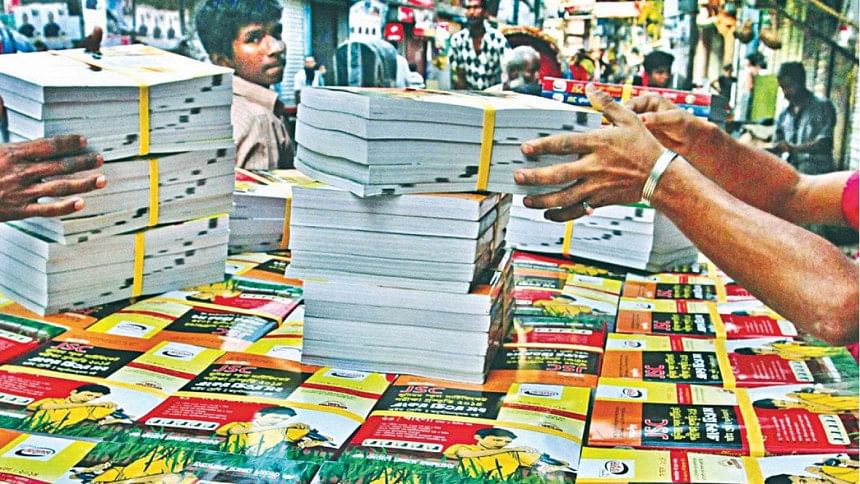
বাংলাদেশের বর্তমান পাঠ্যক্রমটা আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন হয়েছে। এই প্রথম মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সমন্বয় করে পরিপূর্ণ একটি পাঠ্যক্রমের ড্রাফট এই সরকার দিতে চেষ্টা করেছে। এটার জন্য তারা একটা ধন্যবাদ পেতেই পারে।
একটা নীতি করা সহজ, কিন্তু তার প্রয়োগটা কঠিন; বিশেষত বাংলাদেশের মতো একটা জনবহুল এবং রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত একটি দেশের পক্ষে। আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, এই পাঠ্যক্রম নিয়ে অধিকাংশ মানুষের আসলে পরিপূর্ণ ধারণা নেই। অধিকাংশ প্রবাসীদেরও নেই। এমনকি আমারও ধারণা ছিল না।
আমার মনে হয়েছে, হঠাৎ করে এত বড় একটা পরিবর্তনে সরকার কেন হাত দিল। একটা পাঠ্যক্রম করার জন্য কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং লেখকসহ অনেকের সমন্বয় লাগে। এরপর এটা স্কুলে শিক্ষক ও পেশাজীবীদের কাছে মতামতের জন্য পাঠান হয়। প্রয়োগটা সাধারণত হয় পর্যায়ক্রমে।
প্রথমে একসাথে দুই কি তিনটি শ্রেণী দিয়ে শুরু করা হয়। যাতে শিক্ষকদের এই কারিকুলামে পড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিং থাকে। মজার বিষয় হচ্ছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ সালের যে রূপরেখা সরকার প্রদান করেছে, তা ২০১৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং এর প্রতিটি ধাপ সরকারের প্রকাশনায় বিদ্যমান রয়েছে।
সরকার সব নিয়ম মেনেই এটার প্রয়োগের পথে এগিয়েছে। দেশে এবং বিদেশে যারা এই পাঠ্যক্রমের বিরুদ্ধাচরণ করছেন, তাদের কিছু লেখাতে বেশ কিছু পয়েন্ট আছে, যা নিয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে। বাকি লেখাগুলোতে কোনো সারবস্তু নেই, সবই এক্টিভিজম।
মূল বিষয়ে আসি। যেকোনো পাঠ্যক্রম নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কোনো পাঠ্যক্রম আসলে সামগ্রিকভাবে খারাপ হয় না। এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন, সেটাই হচ্ছে মূল বিষয়। বিরুদ্ধাচরণকারীদের যে উদ্বেগ আমি দেখছি সেটা হলো, এই ধারাটি কারিগরি এবং কর্মমুখী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিচ্ছে, সাধারণ ধারাকে নয়। সেটা অবশ্য সঠিক নয়। এ ছাড়া, এটা খারাপ কেন তা আমার বোধগম্য নয়।
সারা পৃথিবীতে শিক্ষায় এটাই এখন লক্ষ্য। আমেরিকার স্কুলে আমাদের সন্তানরা সেভাবেই পড়ছে। থিউরি পড়িয়ে তার প্রায়োগিক বিষয়টা না দেখালে পুরো শিক্ষাটাই বৃথা।
আমাদের সময়ে বিষাদসিন্ধু নামে উচ্চমাধ্যমিকে একটা বইয়ের আংশিক পড়ান হতো। সেখানে আজর নামে একটা চরিত্র ছিল। আজর সীমারের কাছে হোসেনের মস্তক না দেওয়ার জন্য তার তিন পুত্রকে হত্যা করে। আমার মনে আছে, ক্লাসে আমাদের এক বন্ধু বলেছিল, ম্যাডাম, আজরের মতো নিষ্ঠুর এবং গর্দভ টাইপের চরিত্র আমি আর দেখিনি। আমাদের পরীক্ষাতে আসত আজরের চরিত্রের মহত্ত্ব বর্ণনা কর। সেখানে প্রতিটা ছাত্র আজরের চরিত্রের মহত্ত্ব বর্ণনা করত। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করার জন্য যে ব্রেনের চর্চা করতে হয় সেটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল আমাদের সময়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাতে।
আধুনিক বিশ্ব যেভাবে মূল্যায়ন করছে সেই ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনি যদি প্রথাগত ধারণাকে লালন করেন, তাহলে পিছিয়ে পড়বেন। ১৯১৯ সালের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রদের একটি প্রশ্ন ফেসবুকে দেখলাম। একটা প্রশ্ন 'ব্যায়াম কাহাকে বলে? আমাদের দেশে কি কি ব্যায়াম প্রচলিত'। ব্রিটিশ আমল থেকে বাঙালিদের কেরানি বানানোর জন্য যে রসদ তা এই ছোট ক্লাস থেকেই শুরু করেছে। আজকাল এই প্রশ্নগুলো ছবি দিয়ে বিভিন্ন কার্টুন দিয়ে তৈরি করা হবে।
দ্বিতীয় উদ্বেগটি হচ্ছে, এটা ইউরোপিয়ান, আমাদের পর্যাপ্ত রিসোর্স নেই। পর্যাপ্ত রিসোর্স এবং কাঠামো দুটি একসাথে তৈরি করতে হয়। এই মানসিকতাটা নিয়ে কোনো কিছু পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশে কোনো নতুন কিছু করা একদমই সম্ভব নয়। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না।
আমেরিকায় গ্রামে-গঞ্জে বিজ্ঞানের শিক্ষক অপ্রতুল। এ ছাড়া, শহরগুলোর অনেক স্কুলে বিজ্ঞানের পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন পৃথিবীর কোনো দেশেই বেশি নয়। হাতেগোনা কিছু দেশের কথা বলা হয়, সেটাও ইউনিভার্সাল নয়। উন্নত বিশ্বে বিজ্ঞানে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক পাওয়াই কঠিন। বাংলাদেশে হয়ত এই সমস্যা আছে, তবে এলাকাভিত্তিক।
কাজেই বল খেলার মাঠ কখন প্রস্তুত হবে, ভালো রেফারি কখন তৈরি হবে, খেলার জন্য ভালো জুতা আছে কি না, সেটা নিয়ে চিন্তা করলে, খেলোয়াড় মাঠেই নামতে পারবে না। কাঠামো ও প্রয়োগ করার জন্য পর্যাপ্ত টাকা থাকলে ধাপে ধাপে সেটা করাই যুক্তিযুক্ত। প্রথম দু-চার বছর একটু সমস্যা হবেই। স্কুলে কিচেন তৈরি হয়ে গেল স্কুল প্রাঙ্গণে রান্না-বান্নার ভিডিও দেখা যাবে না।
তবে, আমার ধারণা ছিল, নতুন পাঠ্যক্রমটা সব ক্লাসে শুরু হয়ে গেছে। আসলে তা নয়। এটা প্রথমে প্রথম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণিতে শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ক্লাসে শুরু হবে।
এবার প্রধান বিতর্কে আসি। সেটা হচ্ছে, নবম এবং দশম শ্রেণির বিজ্ঞানের সিলেবাস নিয়ে। এই প্রথম নবম এবং দশম শ্রেণিতে বিভাগ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জায়গায় আমার মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে।
আমি মনে করি, বিভাগ উঠিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। আমেরিকাতে ওইভাবে বিভাগ নেই, কিন্তু স্কুলগুলোতে বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, কিছু স্কুল আলাদাভাবে স্টেম (Science, Technology, Engineering and Mathematics) একাডেমি তৈরি করেছে। সেটা নবম শ্রেণি থেকে শুরু হয়। এদেরকে উচ্চতর ক্লাসগুলো ইউনিভার্সিটি এবং কমিউনিটি কলেজগুলোতে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া, এরা যাতে গবেষণার সঙ্গে স্কুল পর্যায়ে জড়িত হতে পারে, তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করার জন্য সুযোগ করে দেওয়া হয়। আমি এই ধরনের প্রায় এক ডজন স্কুল শিক্ষার্থীকে আমার ল্যাবে ইন্টার্নশিপ দিয়েছি। তবে তারা সবাই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।
যারা বেশি ভালো তাদেরকে আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি খুব সহজেই এটা করা সম্ভব। নবম এবং দশম শ্রেণিতে জীবন জীবিকা, শিল্প সাহিত্য আরও কিছু বিষয়কে অপশনাল করে এই সিলেবাসগুলোকে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথকভাবে তৈরি করা সম্ভব।
তবে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সঙ্গে এটার সমন্বয় করতে হবে। তবে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে যেহেতু বিভাগ বিভাজন হবে, সেই পর্যায়েও পৃথকভাবে এটা করা সম্ভব ৯-১০ শ্রেণির একই সিলেবাস রেখে। একটা পাঠ্যক্রম ট্রায়াল অ্যান্ড এররের মধ্য দিয়েই নিখুঁত হয়।
বইয়ের লেখা নিয়ে কথা হচ্ছে। আমরা ট্র্যাডিশনালভাবে বই পড়ে অভ্যস্ত। এই স্টাইলের বাইরে ভিন্নভাবে যে টেক্সট বই লেখা যায়, সেটা বুঝতে হবে। যদি টেক্সট বইয়ে ভুল থাকে তাহলে সেটা শুদ্ধ করতে হবে। আগের আমলের যে বইগুলো ছিল সেগুলোরও অনেক সংস্করণ হয়েছে।
এরপর আসি মূল্যায়নের ব্যাপারে। এই বিষয়ে অনেক কিছু পরিষ্কার নয়। আমি শিক্ষাক্রমের রূপরেখা পড়েছি এবং যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আছে, সেখানে মূল্যায়নের কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে। নবম এবং দশম শ্রেণিতে শিখনকালীন ৫০ শতাংশ এবং সামস্টিক মূল্যায়ন থাকছে ৫০ শতাংশ। তার মানে স্কুলেও পরীক্ষা থাকছে।
এছাড়া দশম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষাও থাকছে। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে দুইটি পাবলিক পরীক্ষা হচ্ছে। প্রাথমিক শ্রেণিতে স্কুল মূল্যায়ন খুবই জরুরি। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে মূল্যায়নের ব্যাপারে প্রতি বছর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। এ ছাড়া, এই পর্যায়ে আমেরিকাতে অনেক হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়। স্কুলে তাদের লার্নিং হচ্ছে কি না, সেটার জন্য চেক অ্যান্ড ব্যাল্যান্স থাকা জরুরি।
টেক্সাস স্টেটে স্টার টেস্ট নামে বছরের শেষে একদিন একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়, সেটার সঙ্গে পাস ফেলের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর ওপর দখলের পরিপূর্ণ একটা পরিসংখ্যান দিতে পারবে। এটা করা গেলে জেলা পর্যায়ে স্কুলগুলোতে ক্লাসরুম শিক্ষার ব্যাপারে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। একটা কারিকুলামের থেকেও আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যাবহার করা বেশি জরুরি। এর জন্য ক্রমাগত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
পরিশেষে বলছি, বাংলাদেশে যদি একটা নিখুঁত পাঠ্যক্রম দেওয়া হতো, সেটা নিয়ে একই সমস্যা হতো। এই পাঠ্যক্রম যা করছে, মনে হচ্ছে এটা লেখাপড়াটা ক্লাসরুমে এবং শিক্ষার্থীদের হাতে নিয়ে আসছে। আগেকার লেখাপড়াটা ছিল ক্লাসরুমের বাইরে কোচিং সেন্টার এবং প্রাইভেট টিউটরদের হাতে।
আমি মনে করি এটা নিম্ন আয়ের জনগণ এবং গ্রামের স্কুলগুলোর জন্য আশীর্বাদ। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই বাংলাদেশে প্রাইভেট টিউশনির চল। এ ছাড়া, এই শিক্ষার্থীদের ক্লাসের পর তিন-চারটি প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে হবে না। স্কুলগুলো বিভিন্ন ক্লাব তৈরি করতে পারবে, তার সঙ্গে এই শিক্ষার্থীরা যুক্ত হতে পারবে।
এই লেখার মূল হচ্ছে হাইস্কুলের শিক্ষা। বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী কলেজে অনার্স এমনকি মাস্টার্স করে। এসব কলেজে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই উচ্চশিক্ষা দেওয়ার মতো। কিন্তু তাদের সিলেবাস দেখলে মনে হবে কত আধুনিক। কিন্তু আসলে কোনো ক্লাস করানো হয় না। বিপুল সংখ্যক বেকার তৈরি হচ্ছে এর মাধ্যমে।
এই কলেজগুলোকে আমেরিকার মতো কমিউনিটি কলেজে রূপান্তরিত করা যায়। এখানে দুই বছরের অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি দেওয়া যাবে। এদের মধ্যে যারা ভালো, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তৃতীয় বর্ষে ট্রান্সফার নিতে পারবে।
এ ছাড়া, বেশ কিছু কলেজ ধাপে ধাপে কিছু বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রির জন্য অনুমতি দেওয়া যেতে পারে সক্ষমতা অনুযায়ী। এখন যেমন ঢালাওভাবে ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স দেওয়া হচ্ছে, সেটা বন্ধ করতে হবে।
এ ছাড়া, কমিউনিটি কলেজগুলোতে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি অথবা পেশাভিত্তিক, এক অথবা দুই বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট টাইপের প্রোগ্রাম তৈরি করা যেতে পারে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে এর বাইরে কোনো বিকল্প নেই।
কোনো একটা পাঠ্যক্রমের ওপর শঙ্কা থাকা খুবই স্বাভাবিক। প্রতিটি অভিভাবক চান তার সন্তানের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সরকারের উচিত এই শঙ্কাগুলো পরিষ্কার করা। আমি মনে করি, সরকার এই বিষয়গুলো পরিষ্কার করার জন্য ক্রমাগত সভা-সেমিনার করতে পারে।
এ ছাড়া, ছোট ছোট ভিডিও ক্লিপ তৈরি করা যেতে পারে। কিছু আছে, কিন্তু মূল শঙ্কাগুলোকে ফোকাস করে আরও করতে হবে। কয়েকদিন আগে দেখলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সভার অনুমতি বাতিল করা হয়েছে এই পাঠ্যক্রমের বিরুদ্ধে যারা বলছে তাদের। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মুক্তবুদ্ধির জায়গা। এখানে একাডেমিক আলোচনা হবে, এটাই স্বাভাবিক। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর সঙ্গে এটাও বলতে চাই, একটা সভা-সেমিনার একমুখী হলে সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যপক্ষের লোক থাকতে হবে।
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে অনেকগুলো পাঠ্যক্রম করার চেষ্টা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমের টিকে থাকার ব্যাপারটা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। এ ছাড়া, রাজনৈতিকভাবে পক্ষ-বিপক্ষে থাকার জন্য একটা ভালো উদ্যোগকে ছুড়ে ফেলতে হবে, সেটা কাম্য নয়। আমাদের অসুস্থ রাজনীতির ডামাডোলে অনেক সময় ভালো উদ্যোগও প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।
ড. সাইফুল মাহমুদ চৌধুরী: যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস এট আরলিংটনের রসায়ন ও প্রাণ রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা করেন।
(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নেবে না।)









Comments