খণ্ডীকরণ রোগে রাজনীতি, অতঃপর...?
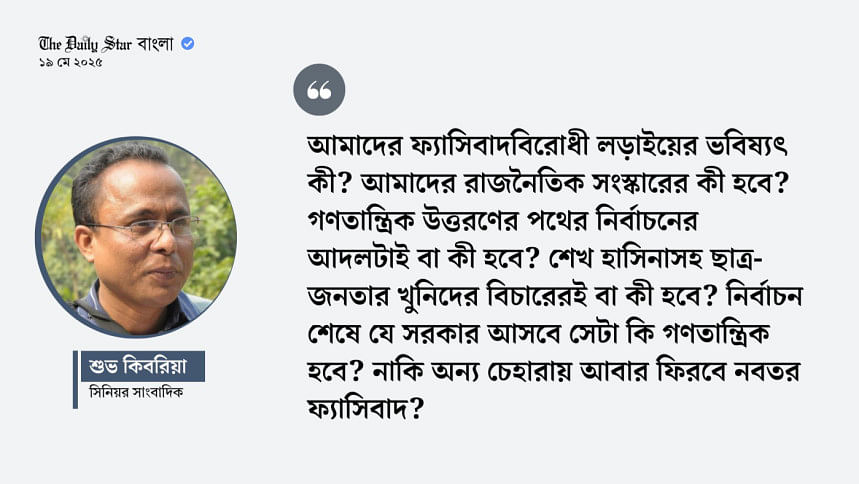
টকশো কিংবা অনলাইনে প্রায় বিপ্লব করেই ছাড়লেন দেশের এক বড় রাজনৈতিক দলের নেতা। কিন্তু বিজ্ঞাপন বিরতিতে অফলাইনে তারই কাতর জিজ্ঞাসা, 'ভাই নির্বাচন কি হবে?' অন্তর্বর্তী সরকার কি যথাসময়েই নির্বাচন দেবে? নাকি তারা তলে তলে অন্য কিছু প্ল্যান করছেন? রাজনীতিতে এই অনিশ্চয়তা এখন বড় আকার পেয়েছে।
ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পরে ফ্যাসিবাদবিরোধী যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, রাজনীতিতে তা এখন 'খণ্ডীকৃত দশায়' অনৈক্য আর বিভাজনের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। বলা ভালো, রাজনীতির যেসব অংশীজনরা মিলে সমষ্টির চাদর তৈরি করেছিল, তারাই এখন টুকরো টুকরো রুমালরূপে আবির্ভূত হয়েছে।
তাহলে এখন আমাদের ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের ভবিষ্যৎ কী? আমাদের রাজনৈতিক সংস্কারের কী হবে? গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথের নির্বাচনের আদলটাই বা কী হবে? শেখ হাসিনাসহ ছাত্র-জনতার খুনিদের বিচারেরই বা কী হবে? নির্বাচন শেষে যে সরকার আসবে সেটা কি গণতান্ত্রিক হবে? নাকি অন্য চেহারায় আবার ফিরবে নবতর ফ্যাসিবাদ?
অন্তর্বর্তী সরকার কি ক্ষমতা ছাড়বে, নাকি এ সরকারের ক্ষমতাকাল আরও দীর্ঘ হবে? তাহলে রাজনৈতিক স্বপ্নভঙ্গই কি এ ভূখণ্ডের মানুষের নিয়তি?
এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে দেখে নেই আমাদের রাজনীতির খণ্ডীকরণের চেহারাটা কেমন দাঁড়িয়েছে এখন।
খণ্ড, টুকরো এবং পরস্পরবিরোধ
১. ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের অগ্রসরমান অংশ ছিল জনতা-শিক্ষার্থী। ফ্যাসিবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় দ্বন্দ্বে বিভক্ত হয়ে যায় এই অংশটি। এরপরই শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক দল এনসিপি গঠনের পরে নিজেদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের উপস্থিতির বিষয়ে বিভাজনের প্রশ্ন উঠতে থাকে। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধকরণে শাহবাগের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এনসিপির ভেতরের প্রগতিশীল অংশ ও ধর্মবাদী অংশের বিভেদ আগুয়ান হয়ে আসে। বাদানুবাদ চলতে থাকে নিজেদের মধ্যেই। দলের বৃহত্তর ঐক্য এই বিভাজনের প্রশ্নে দুর্বল হতে থাকে।
২. দেশের বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি ন্যূনতম সংস্কার শেষে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জোরদার করতে গিয়ে ছাত্র-জনতার নবগঠিত দলকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। অন্তর্বর্তী সরকারও তাদের আক্রমণের মুখে পড়েছে হালে। অভ্যুত্থানের সফলতার কৃতিত্ব দাবি করতে গিয়েও ছাত্র-জনতার নতুন দলের সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। অন্তর্বর্তী সরকার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্বাচন বিলম্বিত করতে যাচ্ছে—এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিএনপি এখন প্রকাশ্যেই কথাবার্তা বলা শুরু করেছে। বলা যায়, সরকার ও ছাত্রদের দলের সঙ্গে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির দূরত্ব এখন প্রকাশ্য ও চোখে পড়ার মতো।
৩. ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অগ্রণী ছিল নারীরা। অভ্যুত্থানের পরে সেই নারীরা মবের শিকার হয়েছেন। অধিকার প্রশ্নে অবহেলিত হয়েছেন। তাদের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে যেসব বক্তব্য তুলেছেন ধর্মভিত্তিক দলগুলো তা নিয়েও তারা দারুণভাবে ক্ষুব্ধ। ঐক্যের ডাকে রাজপথে নামতে হয়েছে নারীদের। আবার ইসলামপন্থি দলগুলোও এ বিষয়ে রাজপথে শোডাউন করে তাদের শক্তি জানান দিয়েছেন। ফলে নারীর অধিকার প্রশ্নে নারী সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে যে বিতর্ক ও উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, সেটাও অভ্যুত্থানের পক্ষের নারীশক্তির নিজেদের মধ্যে তো বটেই নারীদের বড় অংশের সঙ্গে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর দূরত্ব বাড়িয়েছে।
৪. আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল বাদে বাকি বামদলগুলো ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গী ছিলেন সবার সঙ্গে মিলে মিশেই। ইসলামপন্থী দলগুলোর বড় অংশই এই অভ্যুত্থানের অংশীজন ছিলেন। পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যুথবদ্ধভাবে এই গণঅভ্যুত্থানে বড়ভাবে লড়েছিলেন। সেই ঐক্য এখন নানাভাবে, নানা বিবেচনায় অনৈক্যে পরিণত হয়েছে।
৫. রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিএনপির মিত্র ও মৈত্রী ছিল ঐতিহাসিক। জামায়াত-বিএনপি সরকার শাসনও করেছে একসময় দোর্দণ্ডপ্রতাপে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের বিজয়ের পর জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির দূরত্ব ও অনৈক্য প্রকাশ্যে এসেছে ক্রমশ। যে ফ্যাসিবাদী জমানায় এই দুই দল তাদের কাছে বিএনপি-জামায়াত শব্দবন্ধেই উচ্চরিত হতো প্রতিদিন, রাষ্ট্রিক নিপীড়নে টার্গেটও হতো একই বিবেচনায়, সেই ফ্যাসিবাদের পতনের পর, তারাই এখন পরস্পরের সম্পর্কে দূরত্ব বাড়াচ্ছে অতি দ্রুততার সঙ্গে।
অনৈক্য কেন?
প্রথমত, গণঅভ্যুত্থানের বিজয়ের কৃতিত্ব কার—এই প্রশ্নটাই বড় স্টাবলিশ শক্তির সঙ্গে নবউত্থিত রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়েছে। নবগঠিত শক্তির সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের দহরম-মহরম স্টাবলিশ রাজনৈতিক শক্তিকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছে।
দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিবাদী দল আওয়ামী লীগের পতন ও কার্যক্রম নিষিদ্ধের পরে ভোটের রাজনীতিতে তাদের ভোটব্যাংকের হিস্যা পাওয়ার প্রতিযোগিতাও রাজনৈতিক পক্ষগুলোকে অনৈক্যের পথে ঠেলেছে।
তৃতীয়ত, এই গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনীতিতে ধর্মবাদী দলগুলোর প্রকাশ্য অবস্থান ও উপস্থিতি রাজনৈতিক পক্ষগুলোকে নানাভাবে বিচলিত করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন দলের প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধারণ করা অংশটি এর মধ্যে যে বিপত্তি ও বিপদ দেখছেন, সেটাও রাজনৈতিক পক্ষগুলোকে অস্থির করে তুলছে।
চতুর্থত, 'ধর্ম' প্রশ্নটিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ডিল করার যে তরিকা তাতে যে পুরাতন বাম ধারা ছিল, আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে সেটা এখন ক্রমশ দুর্বল হয়েছে। ভোটের প্রশ্নে তারা এখন ডানধারার ওপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিনির্মাণের প্রশ্নে সেই ধারাটি কিছুটা বিব্রত ও দ্বিধাময়। ফলে তাদের নানারকম রাজনৈতিক বিবেচনা, আশংকা ও অনিরাপত্তাবোধও গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বাড়াচ্ছে।
পঞ্চমত, 'ভারত' বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিকভাবে হস্তক্ষেপের যে নজির অতীতে রেখেছে, ফ্যাসিবাদের পতনের পর তাতে ছেদ পড়েছে। পতিত ফ্যাসিবাদী খুনিদের জায়গা দিয়েছে ভারত। অন্যদিকে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 'ভারত' প্রশ্নে অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে 'মর্যাদাময়' অবস্থান নিয়েছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ও স্বার্থের নতজানুকতাকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জ করেছে। ফলে, ভারত এই নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশের রাজনীতির মধ্যে অনৈক্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করার সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। সেটাও আমাদের রাজনৈতিক পক্ষগুলোকে বিভাজিত করছে।
তাহলে কী হবে?
বাংলাদেশের রাজনীতির অতীত বলে, এখানে বিপ্লব, অভ্যুত্থান, লড়াই-সংগ্রামের যে লক্ষ্য বা স্বপ্ন থাকে, বিপুল রক্ত-আত্মত্যাগ-প্রাণ বিসর্জনের পরও তা অর্জন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। কেননা, অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের সুফল মানুষের ঘরে তুলতে হলে যে সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি লাগে, এখানকার রাজনীতি তা দেখাতে সফল হয়নি কখনো। স্বপ্নভঙ্গ হওয়া মানুষকে তাই বারংবার রাজপথে ফিরতে হয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এখানে রাষ্ট্র সংহত হয়নি। এখানকার রাজনীতির বড় দুর্বলতা সিভিল নেতৃত্ব কখনই সুপ্রিম হয়ে উঠতে পারেনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। দৃশ্যমান রাষ্ট্রের ভেতরে 'অদৃশ্য রাষ্ট্র'ই দেশ চালিয়েছে। সিভিল নেতৃত্ব গোয়েন্দা সংস্কৃতি, সামরিক সংস্কৃতির ওপরে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সেটা আবার রাজনীতিকেও শক্তিমান করতে পারেনি।
ফলে চ্যালেঞ্জ আসলে এখানকার রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তা মোকাবিলা করতে পারে না। অনৈক্য, বিভাজন, গ্রুপিং, ছোট ছোট স্বার্থের কাছে বৃহৎ লক্ষ্য পরাভূত হয়। ধর্মের প্রশ্নে, ভারতের প্রশ্নেও আমাদের এখানে রাজনীতি সামর্থ্য নিয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে পারেনি। আমেরিকা-চীন-ভারত যে ত্রয়ী ভূরাজনৈতিক শক্তির মোকাবিলা করে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখে লড়াইটা চালাতে হবে, আমাদের রাষ্ট্র তা করতে সক্ষম হতে পারেনি।
এখানকার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সংস্কৃতির মধ্যেও পরস্পরবিরোধী আদর্শিক বহু এলিমেন্ট আমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে।
আমাদের গোটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশের বদলে 'জেলা'র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিকশিত হয়েছে। ফলে শাসকের সময়কাল অনুসারে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কখনো বগুড়া, কখনো দিনাজপুর, কখনো রংপুর, কখনো গোপালগঞ্জ, কখনো চট্টগ্রাম গোটা দেশের চেয়ে শক্তিমান হয়ে দেখা দিয়েছে। এই খণ্ডিত, বিখণ্ডিত, ক্ষুদ্র হওয়ার প্রবণতাই এখানকার রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য।
অন্যদিকে, বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যে অর্থনৈতিক ও নৈতিক সততা প্রয়োজন, আমাদের রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেটা অর্জন করতেও ব্যর্থ হয়েছে বারংবার। ফলে, সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের ভাষায়, 'দেশের মাটি স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু মাটির মালিকরা স্বাধীন হয় নাই।' এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।
বাংলাদেশ এখন এক অদ্ভুত সময়কাল অতিক্রম করছে। এখন দেশে তরুণ জনগোষ্ঠী সংখ্যা মোট জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ। এখানে রাজনীতিতে পুরাতন জেনারেশন বয়সের কারণে তাদের সময়কালের শেষ দশায়। মোট ১২ কোটি ভোটারের মধ্যে সাড়ে চার কোটি নতুন ভোটার এবার প্রথমবারের মতো ভোট দেবে। বয়সী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে এই তরুণ জেনারেশনের ভাবনার একটা বিরাট জেনারেশন গ্যাপও রয়েছে। ফলে বহু অনৈক্য-আশংকা সত্ত্বেও বিপদের দিনে সব বিভেদ ভুলে তরুণরা ফ্যাসিবাদী হাসিনার পতনের মতো নতুন রাজনীতির গোড়াপত্তনে আবার নেতৃত্ব দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সম্ভবত সেটাই ভরসার একমাত্র জায়গা।
শুভ কিবরিয়া: সিনিয়র সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক










Comments