প্রশ্নকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টাই ফ্যাসিস্টের ধর্ম

বাংলা একাডেমির আয়োজনে চলছে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা। প্রতিদিন মেলায় আসছে নতুন নতুন বই। প্রকাশিত হয়েছে কবি ও গবেষক কাজল রশীদ শাহীনের একাধিক বই। নিজের লেখালেখি, গণঅভ্যুত্থান ও বইমেলা নিয়ে কথা বলেছেন দ্য ডেইলি স্টারের সঙ্গে।
আপনার একটি প্রবন্ধের বইয়ের নাম 'বাংলাদেশের নবজাগরণ'; যা জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের আগে-ওই বছরের একুশের বইমেলায় প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের নবজাগরণ ও এই বই নিয়ে আপনার অভিমত কী?
প্রবন্ধের বইটির পুরো নাম আরেকটু বড়। এর মূল বিষয় অবশ্য বাংলাদেশের নবজাগরণ। বইয়ের প্রধান অনুসন্ধান সেটাই। আমি মনে করি, আমাদের এই ভূগোলে একটা নবজাগরণ সংঘটিত হয়। যার সূচনা বইয়ে আমি উল্লেখ করেছি ১৯২১ থেকে ১৯৭১ অবধি, কিন্তু পরবর্তীতে অধিকতর গবেষণায় মনে হয়েছে-শুরুটা ১৯০৫ থেকে। যার অর্জন হল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। নবজাগরণের কথা উঠলেই ইতালীয়-ইউরোপীয় নবজাগরণের কথা হাজির হয়। বাংলার নবজাগরণের কথাও আসে। কিন্তু বাংলাদেশের নবজাগরণকে বোঝানো হয় না। জাতিগতভাবে এটা আমাদের জন্য ভীষণ বেদনা ও লজ্জার।
যে জাতি তার নবজাগরণকে শনাক্ত করতে পারে না, নবজাগরণের আলোয় জেগে ওঠে না; তাদেরকে নানা দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আকাঙ্ক্ষিত অর্জনের পথে হোঁচট খেতে হয় পদে পদে। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের সেসব মোকাবেলা করতে হচ্ছে দিনের পর দিন।
২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের পর আমরা নতুন আকাঙ্ক্ষার পথে হাঁটতে শুরু করেছি। নানামুখী সংস্কারের আয়োজন চলছে সুশাসন ও গণতন্ত্রের জন্য। আমরা মনে করি, এসব অর্জন তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন নবজাগরণের আলোয়-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দেশটাকে নির্মাণ করা সম্ভব হবে।
বইটা লেখা ও প্রকাশিত হচ্ছে, তখন জাতীয় জীবনে ভোটাধিকার নেই, বাক্ স্বাধীনতা ও সুশাসন কুক্ষিগত, রাজনৈতিক স্বৈরাচার সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কায়েম করেছে দল ও গোষ্ঠীতন্ত্র। তখন মনে হয়েছে, স্বাধীনতার পরপর যদি নবজাগরণকে যথার্থভাবে অনুসন্ধান করা যেত। স্বাধীনতার ইতিহাস নির্মাণ করা সম্ভব হত। তা হলে দেশ ও জাতির পরিণতি এরমক হত না। এই চিন্তা থেকেই 'বাংলাদেশের নবজাগরণ : অন্বেষা-অবলোকন-তত্ত্ব' অনুসন্ধান।
এই বাংলায় ছয় দশকের মধ্যে তিনটা গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনকেও গবেষকদের কেউ কেউ গণ অভ্যুত্থান মনে করেন, তাহলে চারটা। কতবার গণ অভ্যুত্থান হলে আমাদের সামাজিক পরিবর্তন হবে এবং মানসিকভাবেও আমরা গণতন্ত্রমনা হয়ে উঠব?
সংখ্যা দিয়ে তো সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় না। এভাবে ভাবাটা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়। জুলাই-আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের পরও আমরা যা কিছু করছি, যে পথে বৈষম্য নিরসন, বাক্ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সুশাসন চাচ্ছি, এভাবে সেই অর্জন কতটুকু সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
আমরা মনে করি, সবার আগে আমাদের বাংলাদেশের নবজাগরণকে বুঝতে হবে। নির্মাণ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। স্পষ্ট বোঝা পড়া থাকতে হবে 'বাংলাদেশবাদ'সম্পর্কে। শ্রেণী-বর্ণ-গোত্র-দলমত নির্বিশেষে ধারণ করতে হবে 'বাংলাদেশবাদ' এর শুভবোধ, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যয় ও প্রত্যাশাকে। তা হলেই কেবল গণ অভ্যুত্থানের স্বপ্ন ও সাধ বাস্তব হয়ে উঠবে। আমাদের সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তন ইতিবাচক ধারায় প্রবাহিত হবে।
চারপাশের অনেককে দেখা যায় সমাজের ভালো চান, কল্যাণ চান। কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে পাশে পায় না জনগণ। এমন প্রতিশ্রুতি মানুষ কেন দেয়?
সমাজ-রাষ্ট্রে যে যা ভূমিকা পালন করে তার প্রতিদান সে পায়। কুনফুসিয়াসের মতে, 'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়'। এর অর্থ কী? আসলে সে যা চাই সেটা সেই করে দেখায়। এতবড় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যিনি, নিশ্চয় কোন দর্শন থেকেই দিচ্ছেন। ইসলামে তো পরিস্কার করে বলা হয়েছে, 'যার যার ধর্ম তার তার কাছে।' সুতরাং কে কি করবেন-এটাতো একান্তই উনার ব্যাপার। আপনি কেবল দেখতে পারেন উনি ক্ষতিকারক কি না। অন্যের অপকার করেন কি না।
অন্যের ওপর জবরদস্তি দেখান কি না। যদি না করেন তা হলেই উনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। আমাদের সমস্যা হল, অন্যের ওপর নিজেদের স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা চাপিয়ে দিই। অন্যজন চলুক আমার কথামতো-চাওয়ামতো, এই মানসিকতা তো ফ্যাসিস্ট মানসিকতা। এই প্রশ্নের মধ্যে প্রবলভাবে সেই ফ্যাসিস্টের ছায়ায় দৃশ্যমান হয়। এভাবে ভাবাটা আগ্রাসী মনের পরিচয়। মনে রাখতে হবে, অন্যকে অন্যের মতো থাকতে দিতে পারেন যিনি, মহৎ মানুষের কাতারে নিজেকে শামিল করলেন তিনি।
এই যে এতবড় গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত হল। ছয়মাসের মাথায় এসে এর পক্ষের মানুষেরাই বলছেন, গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে না, সেই পথে উপদেষ্টারা হাঁটছেন না। তা হলে যারা এর মাস্টারমাইন্ড, যারা এর সুবিধাভোগী তারা কি বুঝছেন উনারা এই জাতির সঙ্গে কতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করছেন? উনাদের আহবানে যারা জীবন বাজি রাখলেন, তারা কী পেলেন? যারা শহীদ হয়েছে, তারা তো মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। কিন্তু আহতরা, তাদেরকে কেন চিকিৎসার জন্য গভীর রাতে রাস্তায় নামতে হয়? এসব দেখে কি মনে হয় না, এই আন্দোলনের ফসল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কুক্ষিগত করেছে। কেউ উপদেষ্টা হয়েছেন, কেউ মহাপরিচালক, কেউ এমডি; তাদের এসবে কোন যোগ্যতা বা দক্ষতা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। অথচ আন্দোলনের মূল স্পিরিট ছিল যোগ্য ও দক্ষ লোকদের খুঁজে খুঁজে বের করে যথাযথ জায়গায় বসানো হবে-এমনতর। এসব যাদের অভিজ্ঞতায় রয়েছে।
৭১, ৭৫, ৯০ পরবর্তী সময় যারা এসব দেখেছেন বা জেনেছেন এবং ২০২৪-এর পরও যা দেখলেন, সেইসব মানুষেরা কোন মুখে মানুষকে আন্দোলনে ডাকবেন। সমষ্টির স্বর হয়ে কথা বলবেন? একজন বুদ্ধিজীবী কোন ভরসায় সবার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন। আর কত আবু সাঈদের মা'র কোল খালি করবেন? কেননা, তিনি দেখছেন যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। তিনি তো মন্ত্রীর আর উপদেষ্টার কথায়-কাজে বড় কোন পরিবর্তন দেখছেন। মন্ত্রীর মহাপরিচালক, এমডিরা যেভাবে নিজেদের ব্যর্থতাকে বড় গলায় জায়েজ করার বয়ান শুনিয়েছেন, উপদেষ্টার মহাপরিচালক, এমডিরাও তাই, সব ফটোকপি বিশেষ।
এই বাস্তবতায় একজন নির্মোহ বুদ্ধিজীবী যদি মনে করেন কল্যাণ চাওয়ায় নিরাপদ, এবং সেটাকেই এই নিদানকালের আপাত স্বস্তি জ্ঞানে আঁকড়ে ধরেন, সমস্যা কোথায়? এটা আসলে দৃষ্টিভঙ্গির বাপার,। আপনি অন্যভাবে দেখেন-দেখতেই পারেন। কিন্তু পদের পেছনে ছোটার চেয়ে, ভোগ-উপভোগে শামিল হওয়ার চেয়ে এটা কি অনেক বেশি ভাল নয়, তিনি কি সদর্থক অর্থে কুর্নিশ পাওয়ার দাবি রাখেন না?
দেখা যায় সাহিত্য সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও প্রশ্ন নিতে চায় না। 'প্রশ্ন'-এ এত ভয় কেন?
জাতিগতভাবে আমরা 'প্রশ্ন'-এ অভ্যস্ত নই। আমাদের বিদ্যায়তনিক জায়গায় প্রশ্ন চর্চাকে উৎসাহিত করা হয় না। বরং সেখানে রয়েছে প্রশ্নকে দমিয়ে রাখার অপসংস্কৃতি। প্রশ্নমুখী সংস্কৃতি যদি আমরা বিকশিত করতে না পারি, তা হলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্জনসমূহ সব অধরা রয়ে যাবে। গণতন্ত্র, সুশাসন, সাম্য, মুক্তি, স্বাধীনতা যা কিছুই আমরা চাই না কেন প্রশ্নমুখী সংস্কৃতি ছাড়া এসবের কোনটাই বাস্তবায়নযোগ নয়।
প্রশ্নকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হল ফ্যাসিস্টের ধর্ম। যে বা যিনি প্রশ্নকে এড়িয়ে যান, তিনি আসলে ফ্যাসিস্টের ধর্মই পালন করেন। তা ছাড়া, রাষ্ট্রের কোন পদে থেকে প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া সংবিধানসম্মত নয়। এমনটা করা হলে তিনি সংবিধান লংঘনের দায়ী দোষী।
প্রশ্নের চর্চা কিন্তু আমাদের সমাজে সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাহমান। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার নজির রয়েছে ভূরি ভূরি। সভ্যতার এই অগ্রগতি ও উন্নতির মূলে রয়েছে তার প্রশ্ন করার শক্তি। বিজ্ঞানতো প্রশ্ন ছাড়া একপাও নড়ে না, তার ধর্মও নয় সেটা। নবজাগরণ বা রেনেসাঁর মূল বিষয় হল প্রশ্ন। সে প্রশ্ন দিয়ে যুক্তির আলোয় সবকিছু গ্রহণ বা বর্জন করতে চায়-এটাই তার শক্তি। একটা সমাজ বা রাষ্ট্র কতোটা আধুনিক ও প্রজাদরদী তা বোঝার বা নির্ণয়ের আয়না হল, সেই সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রশ্নের সংস্কৃতি কতোটা জারি রয়েছে তা অবলোকন করা।
মানুষ তার স্বভাবের অনেকটাই পায় পূর্বপূরুষ থেকে। স্বভাবে আপনি কী বাবার মতো না মা'র মতো? লেখালেখিতে নিজস্বতা বা অনুসন্ধান কোথায় আপনার?
স্বভাবে বাবা না মা'র মতো, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন আমার পক্ষে। উনাদের পড়ন্তবেলার সন্তান আমি। বাবা-মাকে আবিস্কার করার আগেই ছেড়ে গেছেন ইহজাগতিক পৃথিবী। বাবার লেখালেখি করার অভ্যাস ছিল, কিছু লেখা প্রকাশও করেছিলেন। মা লিখতেন কিনা জানি না, সম্ভবত না, তবে পড়তেন। পড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল দু'জনেরই। মা খুব একটা সময় বের করতে পারতেন না। তারপরও দেখেছি, দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় আশেপাশের অনেকে উনার কিতাব পাঠ বা বইপড়া শুনতে আসতেন। গাজীকালু, সোনাভান, হাতেম তাঈ প্রমুখের কিতাব ছিল মা'র সংগ্রহে। ছিল বিষাদ সিন্ধুসহ আরও কিছু বই। বাবার সংগ্রহে ছিল কবিতা-গল্প-উপন্যাসের বই, এসবের পাশাপাশি প্রচুর পত্র-পত্রিকা পড়তেন। পুরো এলাকার মধ্যে আমাদের বাড়িতেই শুধু স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ ছিল।
বাবা-মা দুজনেই যেমন প্রাক্টিসিং মুসলমান ছিলেন তেমনই ছিলেন প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিমনা। আমাদের সব ভাইবোনেরা বিশেষ করে আমরা তিনভাই যে কিশোর বয়স থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্লাব কালচার ও থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তার প্রধান কারণ বাবা-মা। আমাদের গ্রামের বাড়িটা গত শতাব্দীর আট ও নয়-এর দশকে এবং তার আগে পরেও ফিলিপনগর ও মরিচা ইউনিয়নের সংস্কৃতি চর্চার সূতিকাগার ছিল। ওই বাড়ির প্রাঙ্গণেই আমাদের ক্লাব ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও থিয়েটারের উদ্যোগে একাধিকবার আন্তঃ উপজেলা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজনসহ নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। বাবা-মা, দু'জনের প্রযত্ন ও প্রশ্রয় না থাকলে একটা বাড়িকে ঘিরে এসব করা কখনোই সম্ভব হত না।
আপনার বই 'এই আমি কোথায়ও নেই' মানে কি? এতে পাঠককে কি বার্তা দিতে চেয়েছেন?
এখানে সময়ের স্বর ও সুর ধ্বনিত হয়েছে। কয়েকটি বাদে সবগুলো কবিতা ২০২২-২০২৩-এর মধ্যে রচিত। বাংলা ভাষার লিখিয়েদের যা হয় আর কি, কবিতা দিয়ে যাত্রা। ব্যতিক্রম নয় আমিও। তবে কবিতার পাশাপাশি অন্যবিধ লেখালেখির শুরুটাও কাছাকাছি সময়ে। বিষয় যখন যে মাধ্যমে প্রকাশিত হতে চাই, তাতেই আশ্রয় নেওয়া। ওই সময় মনে হয়েছে, এই কোন্ সময়ে আছি আমি? এই থাকা না থাকার মধ্যে পার্থক্য কী? নিজের জীবনের ওপর যেন কোন কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্য কেউ, রাষ্ট্র-সমাজের শাসক-প্রশাসক বর্গ, বিশেষ করে গোয়েন্দা বাহিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এসবের প্রভাব কতোটা ভয়াবহভাবে পড়ে এবং ব্যক্তিজীবনকে কীভাবে দুমড়েমুচড়ে দেয় – এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে না গেলে অন্যদের পক্ষে কল্পনা করাও দুরুহ।
দুর্বিষহ সেই সময়কে ভাষা দেয়া কঠিন ছিল, কারণ পরিস্থিতি তখন ভাষাহীন হয়ে পড়েছিল। তখন মনে হল, আমি বুঝি কোথাও নেই। লেখা হল 'এই আমি কোথাও নেই'। জীবন যে কতো বড়ো একটা দুঃখের সমুদ্র- তা মনে হয় আমার মতো করে কেউ বুঝিনি। যদিও পৃথিবীর সব নদীই মনে করে তার গভীরতা সবার থেকে বেশি। আমি এসব নিয়ে কোন তর্কে যেতে আগ্রহী নয়।
আমার একটা কবিতার কয়েকটা পংক্তি বললে সেই সময়ের আঁচ কিছুটা বোঝা যাবে। 'আমিই কেবল ফিরব না আর, কখনো কোনদিন/মনে রেখো আমিই পৃথিবীর প্রথম বিপ্লবী/যে লিখে দিল দস্তখত/ফিরব না কোনদিন আমি আর।' সবাই ফিরতে চাই রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের লেখালেখিতে ফেরার আকুতিই উচ্চকিত হয়েছে, কিন্ত আমি ফিরতে চাইনি-চাই না। আরেকটি কবিতার ক'টি পংক্তি 'ইহজাগতিকতা, মৃত্যুর বেদনাও কি অনিবার্য নিয়তি/মারা গেছি লক্ষ নেই কারও, জানাচ্ছে না বিদায়/ব্যাপারটা কি স্বাভাবিক-হবে হয়েতো, যেভাবে /স্বাভাবিক ধর্মের নামে অধর্ম, স্বরাজের দোহায়ে অরাজ/বিচারের আড়ালে অবিচার-মৃতদের নেই/অভিধান-গুগল-উইকিপিডিয়ায় গতায়াতের অধিকার।'





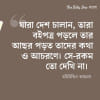




Comments