ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপই ছিল সবচেয়ে ক্ষতিকর

শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরিটাস অধ্যাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। বহু আগে শ্রেণিকক্ষ থেকে অবসর নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র করে তোলার জন্য তার ভাবনা ও কর্মে কখনো ছেদ পড়েনি। একাধিকবার উপাচার্য হওয়ার প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। মনোযোগী হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি প্রকৃত জ্ঞান উৎপাদন ও চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য।
সমাজ-রূপান্তর অধ্যায়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে অধ্যাপক আহমদ কবির প্রথম স্মারক বক্তৃতা দেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ: বিচারের দুই নিরিখে'।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর এই স্মারক বক্তৃতার কথাগুলো ৭ পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে দ্য ডেইলি স্টার বাংলায়। আজ প্রকাশিত হলো তৃতীয় পর্ব।
ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্যের প্রবহমানতা অচ্ছেদ্য রূপে বজায় রাখা সম্ভব না হলেও, সমাজ ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ধারাবাহিকতায় কিন্তু বিরাম ঘটে নি। প্রতিষ্ঠার সময়ে ঢাকা ও কলকাতা উভয় শহর থেকেই স্বার্থবাদীদের বিরোধিতা যেমন এসেছে, যাত্রা শুরুর পরেও তেমনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈরিতার মোকাবিলা করেই এগুতে হয়েছে।
সমাজে দারিদ্র্য ছিল, অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দানের ব্যাপারে পারিবারিক সামর্থ্যের অভাব দেখা গেছে, আবার কুসংস্কার-ব্যবসায়ীদের তৎপরতাও ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু থেকেই ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটা তাও করা গিয়েছিল, কিন্তু ছেলেমেয়েদের মেলামেশার ব্যাপার অলিখিত নিষেধাজ্ঞা কাজ করতো। আবাসিক হলগুলোতে সাংস্কৃতিক কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নাট্যাভিনয়। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে এক সঙ্গে অভিনয় করবে এই ব্যবস্থা চালু হতে বহুদিন লেগেছে। ছেলেরাই মেয়ে সাজতো, আবার মেয়েরা যদি নিজেদের আবাসে নাটক মঞ্চস্থ করতো তবে মেয়েদেরকেই দায়িত্ব নিতে হতো পুরুষের ভূমিকায় অভিনয়ের। একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এটি ১৯২৯ সালের ঘটনা। জগন্নাথ হল ছাত্রসংসদ একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে, তার একটি অংশ ছিল এ রকমের যে, ৮/১০ বছরের একটি মেয়ে কিছুটা সাজগোজ করে মঞ্চে উঠে হাত-পা নেড়ে নৃত্যের ভঙ্গি করবে, পেছন থেকে তার বোন হারমোনিয়াম বাজিয়ে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে। অনুষ্ঠানসূচীর খসড়াতে ড্যান্স কথাটার উল্লেখ ছিল, প্রভোস্ট রমেশচন্দ্র মজুমদার সেটিকে কেটে 'এ্যাকশন সঙ' করে দেন। তাতেও কিন্তু রেহাই মেলেনি। অনুষ্ঠানের পরের দিনই সাপ্তাহিক চাবুক পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে খবর ছেপেছিল, "জগন্নাথ হলে আবার মেয়ে নাচিল।" (আশুতোষ ভট্টাচার্য, একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ, আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৭)
সমাজে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সংঘর্ষ বেড়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তা ঢুকে পড়তে চেয়েছে; শহরে দাঙ্গা শুরু হয়েছে, শিক্ষার্থীরা বিপদে পড়েছে; কলেরা ও বসন্ত যখন রূপ নিয়েছে মহামারির- বিপন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছুটি ঘোষণা করেছে, বাধ্য হয়ে।
তবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপই ছিল সবচেয়ে ক্ষতিকর। স্বভাবগত ভাবেই রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়কে পছন্দ করে না। রাষ্ট্র চায় আনুগত্য, বিশ্ববিদ্যালয় চায় মুক্তি। দুয়ের ভেতর বিরোধ তাই অনিবার্য। এটা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটেছে, বিশেষ ভাবে ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীদের জন্য তো অবশ্যই, শিক্ষকদের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মায়ের মতো; যেন দ্বিতীয় মাতা। পালনকারী মাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও পালক মাতার লালন-পালন-কর্তব্য যথাযথই পালন করেছে, যদিও এই মাতার ওপর দিয়ে বহুধরনের ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে। রাষ্ট্র কিন্তু চরিত্রগত ভাবেই পিতৃতান্ত্রিক, বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষকে যেসকল রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটিই ছিল অসংশোধনীয় রূপেই পিতৃতান্ত্রিক। কর্তৃত্ব করেছে, আনুগত্য চেয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সামাজিক প্রয়োজনে; রাষ্ট্র উৎসাহী ছিল না, তারপরে দুই দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। রাষ্ট্র ওই দুটি যুদ্ধে সরাসরি জড়িত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যে মন্বন্তর ঘটে তাতে বাংলার ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। এদের বেশীর ভাগই ছিল পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা। মন্বন্তর যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট সৃষ্টি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রভাব বলয়ের বাইরে ছিল না। যুদ্ধের অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আর্থিক বরাদ্দ কমিয়ে দেবার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় উৎসাহের কোনো অপ্রতুলতা ঘটে নি। কিন্তু আরও যা দুঃখজনক তা হলো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ।
রাষ্ট্র নামে, আয়তনে এবং বাইরের চেহারাতে বদলেছে; ব্রিটিশ ভারতীয় রাষ্ট্রের জায়গাতে এসেছে পাকিস্তানী রাষ্ট্র, কিন্তু রাষ্ট্রের অন্তর্গত যে স্বভাব-চরিত্র সেটা এক রকমেরই রয়ে গিয়েছে। বরঞ্চ আগেরটির তুলনায় পরেরটি আরও অধিক কর্তৃত্বপরায়ণ রূপ ধারণ করেছে। প্রথম সমাবর্তনে প্রাদেশিক গভর্নর লর্ড লিটন ঢাকাকে যে মুসলমানদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়বার এবং ঢাকার নতুন সাম্প্রদায়িক মানুষের সৃষ্টির কথা বলেছিলেন সেটা যে কেবল তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল তেমনটা ভাববার কোনো কারণ নেই; ওটি ছিল রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায়েরই অভিব্যক্তি। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখার জন্য ১৯১২ সালে যে নাথান কমিটি গঠন করা হয়, তাদেরও সোপারিশ ছিল ইসলামী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দানের। (M. A Rahim, The History of the University of Dacca, Dhaka Bishwabidyalay Prokashona Sangstha, Dhaka, p 16)
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ হ্রাস করে দেবার ঘটনাটিও মোটেই অরাজনৈতিক ছিল না।
বিশ্ববিদ্যালয় যে কতটা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন ছিল সেটা টের পাওয়া পদাধিকার বলে যে গভর্নররা চ্যান্সেলার হতেন তাঁদেরকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেবার হিড়িক দেখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলার লর্ড রোনাল্ডশ'কে ডক্টরেট দেওয়া হয় ১৯২২ সালেই, পরবর্তীতে ওই একই সম্মানে ভূষিত হন লর্ড বুলওয়ার লিটন, স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন এবং স্যার জন এ্যান্ডারসন। যে বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশ চন্দ্র বসু, মুহম্মদ ইকবাল, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিক বিজ্ঞানীকে ডক্টরেট দেয়, সেই একই বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রদেশের গভর্নরদেরকে, তাঁরা শাসনকর্তা এই বিবেচনায় একই সম্মানে ভূষিত করে তখন সম্মাননার গৌরবে টান পড়ে তো বটেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের আবদ্ধ দশাটাও ধরা পড়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যিনি উপাচার্য, ফিলিপ হার্টগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে এবং তাঁর পরবর্তী উপাচার্যদেরকে মেনে নিতে হয়েছিল ওই ব্যবস্থা, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় তার চ্যান্সেলারদেরকে, তাঁরা প্রদেশের শাসনকর্তা এই বিবেচনাতেই সর্বোচ্চ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিতে হতো।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে ১৯১২ সালে ন্যাথান কমিটি সোপারিশ করেছিল যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চলবে যেমন সরকারী অর্থায়নে, তেমনি সরকারী নিয়ন্ত্রণে। বস্তুত কমিটি এটিকে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দেখতে চেয়েছিল। দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল ঔপনিবেশিক। কিন্তু ১৯১৭ সালে গঠিত স্যাডলার কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবেই গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বদলে বিশ্ববিদ্যালয়কে যতোটা সম্ভব স্বায়ত্তশাসন দেবার সোপারিশ এই কমিশনের রিপোর্টে ছিল। ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে আইনটি পাস করা হয় সরকার সেটিতে নাথান কমিটির নয় বরং স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবই গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে নাথান কমিটির প্রধান রবার্ট ন্যাথান ছিলেন একজন ব্যারিস্টার, বোঝা যায় তিনি আর যাই হোন না কেন উদারনীতিক ছিলেন না। আর স্যাডলার কমিশনের প্রধান মাইকেল আর্নেস্ট স্যাডলার ছিলেন একজন সাবেক উপাচার্য, ইংল্যান্ডের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের; বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন, সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়।
স্যাডলার কমিশনের বক্তব্যটি ছিল এই রকমের যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় autonomous হবে, যদিও তার অর্থ এই নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো দায়িত্বজ্ঞান থাকবে না, এবং সে রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক পরিমণ্ডলের বাইরে থাকবে। তবে, They stated that without a certain degree of freedom we do not think that the University of Dacca can even become a living and healthy organization. (ঐ, ঢ় ১৪)
কমিশন শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়েছে, অনেকটা যেন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিপরীতে।
১৯২০-এর এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোর্ট'কে দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণ ক্ষমতা। পরবর্তীতে এই কোর্টকেই সিনেট বলা হয়েছে। প্রথম কোর্টে সদস্য ছিলেন ১৫৮ জন। এঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার তো ছিলেনই, ছিলেন প্রফেসর ও রীডাররাও (পরবর্তীতে এঁদেরকে বলা হয়েছে এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর)। শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল ৩০ জন। পদাধিকার বলে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরাও সদস্য হয়েছিলেন। চ্যান্সেলার মনোনয়ন দিয়েছিলেন ৪০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে। ৫ জন ছিলেন শিক্ষকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। ব্যবস্থা ছিল রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদেরকে যুক্ত করবার; এঁরা নির্বাচন করেছিলেন তাঁদের ২৯ জন প্রতিনিধির; ১৫ জন অমুসলমান, ১৪ জন মুসলমান। কোর্টের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করায় দায়িত্ব ছিল একজিকিউটিভ কাউন্সিলের (পরবর্তী নাম সিন্ডিকেট)। দেখা যাচ্ছে কেবল স্বায়ত্তশাসন নয়, সীমিত আকারে যদিও তথাপি সমাজকেও যুক্ত করার অভিপ্রায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই আইনে। দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের পেছনে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয়দেরকে রাজনৈতিক ভাবে কিছুটা যুক্ত করার পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিটা কাজ করে থাকবে। ভারতীয়দের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ছিল, তার দরুন উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের ভেতর অধিকার-চেতনা শক্তিশালী হয়ে ওঠে; এবং বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলমানদের মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তাকে কিছুটা শান্ত করবার ইচ্ছাটা থেকেই তো নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি রাজনৈতিক ঘটনা; আর প্রতিষ্ঠাকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মেজাজের প্রতিফলন তার আইনে ঘটবে এটাই ছিল স্বাভাবিক।
তবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ তো ছিলই। অর্থায়ন ছিল পুরোপুরি রাষ্ট্রীয়; উপাচার্য, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, এঁরা সরকারের দ্বারাই নিয়োগ পেতেন। বার্ষিক সমাবর্তনে এসে চ্যান্সেলাররা শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক অর্থাৎ অনুগত মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার পরামর্শ দিতে ভুলতেন না।
১৯৪৭-এ ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও দেশভাগের ফলে পাকিস্তান নামে যে নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটলো তাতে অনেক কিছুই বদলে যাবার কথা; বিশ্ববিদ্যালয়ও বদলালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স তখন ২৬ বছরে পড়েছে, সে তার নিজস্বতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, এবং নিজের পথেই এগুচ্ছে; এরই মধ্যে ঘটে গেল রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন। শুরু থেকেই ছাত্রদের শতকরা আশি ভাগই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের, শিক্ষকদের ভেতর অতিঅল্প কয়েকজন বাদ দিয়ে সবাই ছিল অমুসলিম। পাকিস্তান হওয়াতে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষকরা চলে যেতে শুরু করলেন। শিক্ষকদের কেউ ততোদিনে অবসরেও চলে গেছেন; এঁরাও ছিলেন অমুসলিম। বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের যে শিক্ষকরা গিয়েছিলেন, তাঁরাও আর ঢাকা ফেরত এলেন না। অমুসলিম ছাত্রদেরও ব্যাপক দেশত্যাগ ঘটলো। ফলে অনেকের কাছেই রাষ্ট্রের মতো বিশ্ববিদ্যালয়কেও নতুন ও অপরিচিত ঠেকলো, যে কথাটা ঢাকা-ছেড়ে-যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনদের কেউ কেউ বলেছেন তাঁদের স্মৃতিকথায়।


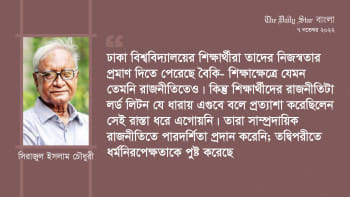
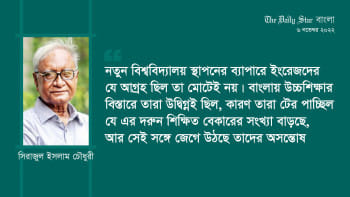








Comments