তরুণদের বিরোধ মোটেই সামান্য নয়

যে কিশোর, তরুণরা আজ পরস্পরকে খুন, জখম করছে, আসক্ত হচ্ছে নানাবিধ মাদকে, এক সময়ে তারা যেমন মুক্তিযুদ্ধে ছিল, তেমনি পূর্ববর্তী রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও ছিল। রাষ্ট্রভাষার জন্য আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে, কিন্তু জয়ের প্রমাণ তো দেখতে পাই না, দেখতে পাই মাতৃভাষা কেবলি কোণঠাসা হচ্ছে। শহীদ দিবসের প্রভাতফেরীকে আদর আপ্যায়ন করে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মধ্যরাতে, সকালের সেই অরুণ আলো মলিন হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারের কাছে তার আত্মসমর্পণ ঘটেছে।
পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য তৎপরতা যে সর্বগ্রাসী হতে চলেছে এ হচ্ছে তারই একটি নিদর্শন। একুশ ছিল রাষ্ট্রবিরোধী এক অভ্যুত্থান, রাষ্ট্র তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার অছিলায় আটক করে ফেলেছে। ওদিকে উচ্চ আদালতে বাংলা নেই, ঠিক মতো নেই উচ্চশিক্ষাতেও। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিভাগে ভর্তি হতে হবে শুনলে শিক্ষার্থীদের মুখ শুকায়, অভিভাবকরা প্রমাদ গোনেন। স্মার্ট ছেলেমেয়েরা বাংলা বলতে অস্বস্তি বোধ করে, শিক্ষিত বয়স্করাও বাংলা বলেন ইংরেজির সঙ্গে মিশিয়ে। প্রমাণ দেয় যে তারা পিছিয়ে নেই। এই অস্বাভাবিকতাই এখন নতুন স্বাভাবিকতা।
একুশে ফেব্রুয়ারির পরিচয় কেন বাংলা ফাল্গুন মাসের তারিখ দিয়ে হবে না, এ নিয়ে বিজ্ঞ মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। ফাল্গুন তার উপেক্ষার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছে। নীরবে। পহেলা ফাল্গুন এখন বেশ ভালোই সাড়া জাগায়। সঙ্গে থাকে ভালোবাসা দিবস। পহেলা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবস, এই দুইয়ের কারও সঙ্গেই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আন্দোলনের কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। উল্টো বিরোধ আছে। পহেলা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবসের উদযাপনের ভেতর দিয়ে তরুণরা তাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উদ্দীপিত হয় না। তাদের আগ্রহটা মোটেই দেশপ্রেমিক নয়, একান্তই ব্যক্তিগত।
ভালোবাসা খুঁজতে বের হয়ে তারা প্রাইভেট হয়ে যায়, পাবলিককে দূরে সরিয়ে দিয়ে। পেছনে তৎপরতা থাকে বাণিজ্যের। ফুল, পোশাক, উপহার, রং, এসবের কেনাবেচা বাড়ে। থাকে বিজ্ঞাপন। ঘটে গণমাধ্যমের হৈচৈ। সমস্ত তৎপরতা নির্ভেজাল রূপে পুঁজিবাদী, এবং সে-কারণে অবশ্যই একুশের চেতনার বিরোধী। আর একুশের চেতনারই তো বিকশিত রূপ হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও যে বাণিজ্যের প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে এমনও নয়।
তিন ধারার শিক্ষা সগৌরবে বহাল রয়েছে। এবং আঘাত যা আসছে তা মূল যে ধারার, বাংলা ধারার, ওপরেই বেশী। সেই ধারার পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষাব্যবস্থা, এসব নিয়ে অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, এবং প্রায় কোনোটাই শিক্ষার্থীদের উপকারে আসছে না। শোনা যাচ্ছে এবার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই নাকি জাতীয় শিক্ষাসূচীর ইংলিশ ভার্সন চালু করা হবে। মাধ্যমিক স্তরে ইংলিশ ভার্সন ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, তাকে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ। নিম্নবিত্ত অভিভাবকরা হয়তো খুশিই হবেন, ভাববেন তাদের সন্তানরা আর বঞ্চনার শিকার হবে না, তারাও ইংরেজিতে শিক্ষিত হবার অধিকার পেয়ে যাবে। ওদিকে করোনাকালে অন্যসব স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কওমি মাদ্রাসা কিন্তু বন্ধ হয়নি। সেখানে ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে। একটি জাতীয় দৈনিক জানাচ্ছে, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি ফের বাড়ল : করোনার মধ্যেও এগিয়ে যাচ্ছে কওমি শিক্ষার্থীরা।" (দৈনিক সমকাল, ১৫.২.২১) আগামীতে নিম্নমধ্যবিত্তের যে অংশটি গরীব হয়ে যাবে তাদের ছেলেমেয়েরা কওমি মাদ্রাসার দিকেই রওনা দেবে। তাতে দেশের ভালো হবে এমন আশা দুরাশা।
তরুণ পুস্তক প্রকাশক ফয়সল আরেফিন দীপন হত্যার অভিযুক্ত আসামীদের ৮ জনের শেষ পর্যন্ত ফাঁসির আদেশ হয়েছে। কিন্তু মূল হোতা বলে অভিযুক্ত যে দুইজন তারা এখনও ধরা পড়েনি। বিজ্ঞান-লেখক অভিজিৎ রায়ের হত্যা মামলার বিচার শেষ হতে প্রায় ছয় বছর সময় লাগলো। সে-মামলায় পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, একজনের যাবজ্জীবন। কিন্তু মূল যে হোতা সেনাবাহিনী থেকে চাকরীচ্যুত মেজর সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক, দীপন ও অভিজিৎ উভয় হত্যাকাণ্ডের জন্যই যে প্রাণদণ্ডাদেশ পেল, সে কিন্তু ধরা পড়েনি। অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডে তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যাও মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কোনোমতে প্রাণে বেঁচেছেন। মামলার রায়ে তিনি সন্তুষ্ট হননি। তার অভিযোগ ধর্মীয় জঙ্গি নির্মূলে সরকার মোটেই আন্তরিক নয়।
অভিজিতের ভাগ্যহীন পিতা প্রফেসর অজয় রায় সন্তান হারালেন, বিচার দেখে যেতে পারলেন না; প্রিয় সন্তানের মৃত্যু তাকে অত্যন্ত কাতর করেছিল, তাঁর জীবনীশক্তির ওপর প্রচণ্ড একটা আঘাত এসে পড়েছিল। তাতে তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে। অভিজিতের মা'ও মারা গেছেন। অসুস্থ ছিলেন, পুত্রশোকে কাতর হয়ে চলে গেছেন। লেখক হুমায়ুন আজাদ হত্যার বিচার এখনও শেষ হয়নি। যে তরুণরা এঁদেরকে হত্যা করেছে তারা যে এঁদের লেখা পড়েছে এমন মনে হয় না। শুধু শুনেছে এঁরা ধর্মবিরোধী, এঁদেরকে হত্যা করলে বেহেস্ত-নসিব সুনিশ্চিত, তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানুষ হত্যার উন্মাদনায়।
পৃথিবী যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। দুর্ঘটনাও নয়। অনিবার্যভাবেই তা ঘটে চলেছে। সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিতদের ভেতর বিভাজনটা অতিপুরাতন। একালে বিভাজনটা সর্বগ্রাসী ও সর্বত্রবিস্তারী হয়েছে, এই যা। ভাগটা ওপরের ও নীচের। ওপরে রয়েছে সুবিধাভোগী অল্পকিছু মানুষ, নীচে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ, যারা শ্রম করে এবং যাদের শ্রমের ফল অপহরণ করেই ওপরের মানুষগুলো তরতাজা হয়। লেখক জনাথন সুইফট তার গালিভার্স ট্রাভেলস বইতে আজব কয়েকটি দেশের কল্পকাহিনী লিখেছিলেন। দেশগুলোর একটিতে শাসকরা থাকে উড়ন্ত এক দ্বীপে, নীচে বিস্তীর্ণ এক মহাদেশ, সেখানে বসবাস প্রজাদের। প্রজারা মেহনত করে, তাদের উৎপাদিত খাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে তুলে নেওয়া হয় উড়ন্ত দ্বীপে; সুযোগসুবিধাভোগী রাজা, তার মন্ত্রী ও পারিষদদের ভোগের জন্য।
প্রজাদের বিস্তর অভিযোগ আছে। সেগুলো শোনার ব্যবস্থাও রয়েছে। উড়ন্ত দ্বীপটি যখন যেখানে যায় সেখানকার মানুষদের সুবিধার জন্য ওপর থেকে সুতো ঝুলিয়ে দেয়া হয়। প্রজারা তাতে ইচ্ছা করলে মনের সুখে নিজেদের অভিযোগগুলো কাগজে লিখে সুতোতে বেঁধে দিতে পারে। কিন্তু সেই কাগজ কেউ কখনো পড়ে বলে জানা যায়নি। তবে প্রজারা যদি ভুল করে কোথাও বিদ্রোহ করে বসে তবে তার জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা সে রাজত্বে রয়েছে। উড়ন্ত দ্বীপটি বিদ্রোহীদের এলাকায় উপরে এসে উপস্থিত হয়; ফলে সূর্যের কিরণ ও বৃষ্টিপাত, দুটো থেকেই নীচের বিদ্রোহীরা বঞ্চিত হয়ে অচিরেই নাকে খত দেয়। বিদ্রোহ দমনের আরেকটি পদ্ধতি উড়ন্ত দ্বীপ থেকে বড় বড় পাথর নীচের মানুষদেরকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা।
নীচের মানুষদের ওপর ওপরওয়ালাদের এই শাসন-শোষণের ছবিটি আঁকা হয়েছিল বেশ আগে, ১৭২৬ সালে। এর প্রায় দু'শ' বছর পরে ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নাটক লিখেছিলেন মুক্তধারা নামে। সেটাও ওই ওপর-নীচ সম্পর্ক নিয়েই। ওপরে থাকেন উত্তরকূটের রাজা-মাহারাজারা, নীচে বসবাস শিবতরাইয়ের প্রজাদের। প্রজারা নিয়মিত খাজনা দেয়। তবে পরপর দু'বছর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় খাজনা ঠিকমতো শোধ করতে পারেনি। শাস্তি হিসেবে ওপর থেকে নীচে বহমান, উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত নদীর পানি আটকে দেওয়া হয়েছে। নদীর ওপরে মস্ত এক বাঁধ কিছুকাল আগেই তৈরি করা হচ্ছিল, এখন তাকে কাজে লাগানো হলো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতদ্রষ্টা ছিলেন, নদীর পানি যে মনুষ্যই নিপীড়নের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে সেটা আগেভাগেই দেখতে পেয়েছিলেন। তবে এটা ভাবা নিশ্চয় তার পক্ষেও সম্ভব হয়নি যে ওপরওয়ালাদের হস্তক্ষেপে তার প্রাণপ্রিয় পদ্মানদীটি তার-দেখা 'ছোট নদী'টিতে নিয়মিত পরিণত হতে থাকবে।
কিন্তু উপায় কি? যেমন চলছে তেমনভাবে তো চলতে পারে না। উপরের সুবিধাপ্রাপ্তদের সঙ্গে নীচের বঞ্চিতদের অপরিহার্য ও অনিবার্য দ্বন্দ্বের মীমাংসাটা কি ভাবে ঘটবে? আপোসে? আপোসের সম্ভাবনা তো কল্পনা করাও অসম্ভব। হ্যাঁ, মীমাংসা হবে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়েই। ওপরওয়ালারা যদি জিতে যায় অবস্থাটা তাহলে অকল্পনীয় রূপেই ভয়াবহ দাঁড়াবে। হাজার হাজার বছরের সাধনায় মানুষ যে অত্যাশ্চর্য সভ্যতা গড়ে তুলেছে তার বিলুপ্তি তো ঘটবেই, মানুষের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে কি না সেটাই হয়ে পড়বে প্রাথমিক প্রশ্ন। ভাঙতে হবে তাই ওপর-নীচের ব্যবধান।
ওপর শুধু সুখ ভোগ করবে, আর নীচ পোহাবে দুর্ভোগ সেটা চলবে না। ভাঙার এই অত্যাবশ্যকীয় কাজটা ওপরের সুবিধাভোগীরা করবে না, এটা করতে হবে নীচের মানুষদেরকেই। বিরোধটা মোটেই সামান্য নয়; অতিপুরাতন, চলমান ও ক্রমবর্ধমান একটি দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে বঞ্চিত মানুষের জেতার সম্ভাবনা না দেখা দিলে অচিরেই ঘোর অরাজকতা দেখা দেবে। সেটা সামলাবে এমন সাধ্য কারোরই থাকবে না।





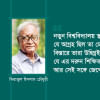


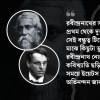

Comments