যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি: অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ কতটা জরুরি

এ সময়টাতেই মূলত যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফল সেমিস্টারে ফান্ডিংয়ের আবেদন করতে হয়। কারণ স্প্রিং সেমিস্টারে (জানুয়ারি-মে) ফান্ডিংয়ের সুযোগ থাকলেও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ফল সেমিস্টারেই সুযোগ বেশি থাকে। তাই সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই আবেদন প্রক্রিয়া শেষ করতে হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন থেকে শুরু করে আবেদন- এই পুরো সময়টা আসলে বেশ দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়া। অনেক কিছু গুছিয়ে নেওয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, প্রফেসর কিংবা অধ্যাপকের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করা। এ নিয়ে অনেকেই জানতে চান যে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদনের আগে প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফান্ডের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় কি না।
আসলে এটা নির্ভর করছে আপনি যে বিষয়ে পড়তে চান, যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করছেন, সেখানকার ফান্ডিং পলিসির ওপর। যেমন- ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বিজ্ঞান বিষয়ক সাবজেক্টগুলোর প্রায় সব কলেজ, বিভাগেই দেখেছি শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফান্ডিং সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেন। অনেক সময় অধ্যাপকের পরামর্শেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেন। আবার আমি নিজে সামাজিক বিজ্ঞানের অধীনে কলেজগুলোয় দেখেছি, মাস্টার্স এবং পিএইচডি, এই দুই ক্ষেত্রেই অধ্যাপকের সঙ্গে আগে যোগাযোগ করে নেওয়া, ফান্ড সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, অতটা প্রয়োজনীয় না। সত্যি বলতে ফান্ডিং আসলে এই যোগাযোগের ওপর নির্ভর করে না।
সামাজিক বিজ্ঞানের অধীনে যেই কলেজ এবং বিভাগগুলো আছে, সেখানে ফান্ডিং মূলত হয়ে থাকে কেন্দ্রীয়ভাবে। তাই সামারে যখন নিয়মিত সেমিস্টার বন্ধ থাকে, সেই পুরোটা সময় এসব বিভাগের শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে মাস্টার্সের ক্ষেত্রে টিচিং এবং রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্টের সুযোগ কিছুটা সীমিত। আর বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর ফান্ডিং পুরো উল্টো। এখানে অধিকাংশ ফান্ডিংই আসে মূলত শিক্ষকের ল্যাব বা গবেষণার প্রজেক্টের ভিত্তিতে। তাই আমি যখন সামারে অন-ক্যাম্পাস জব করেছি, আমার প্রকৌশল, রসায়নসহ নানান বিভাগের বন্ধুদের দেখেছি কোনো রকম নতুন চাকরির চিন্তা ছাড়াই ল্যাবে নিয়মমাফিক কাজ করে চলছেন। তাই সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে যারা আবেদন করতে চাইছেন, তাদের ক্ষেত্রে আগে থেকেই প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে এমনটা নয়।
তবে সেটা সব কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নও হতে পারে। যেমন কিছু বিশ্ববিদ্যালয় যেমন উইসকনসিন ম্যাডিসন, রাটগার্স, ইউটাহসহ প্রায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেই স্পষ্ট করে বলা থাকে, নিজের এসওপিসহ অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে কোন শিক্ষকদের সঙ্গে কাজ করতে চান, তা উল্লেখ করতে। অবশ্যই সেটা উল্লেখ করবার আগে আপনাকে সেই শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, নিজের গবেষণার বিষয়ের কথা জানিয়ে নিতে হবে।
এ ক্ষেত্রে মাস্টার্স এবং পিএইচডি দুটোতেই ভিন্ন যুক্তি রয়েছে। মাস্টার্সের ক্ষেত্রে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু পিএইচডিতেই ফান্ডিং বেশি তাই আপনি যখন মাস্টার্সে আবেদন করবেন তখন প্রফেসরের রিকমেন্ডেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আগে থেকে নিজের গবেষণার বিষয়, আগ্রহের জায়গা জানিয়ে রাখলে সেটা সহজ হয়। আর পিএইচডির ক্ষেত্রে বলা হয়, উচ্চশিক্ষার এই যাত্রাটা খুবই নির্দিষ্ট এবং শ্রমসাধ্য।
আপনি যেই অ্যাডভাইজরের অধীনের কাজ করবেন, তিনি এই পুরোটা সময় আপনাকে একটি প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলবেন। তাই পিএইচডির অ্যাডমিশনের সময়ে শিক্ষার্থী নির্বাচনের সময় কমিটিতে থাকা প্রফেসর গুরুত্বই দেন, যেই শিক্ষার্থীর সঙ্গে তার কাজের ধরনে মিল থাকবে। আর এ কারণেই অনেকেই পরামর্শ দেন যে পিএইচডির মতো এই যাত্রায় আবেদনের আগে প্রফেসরের সঙ্গে ভালোমতো আলাপ করে নেওয়া। ই-মেইল ছাড়াও জুমে ভিডিও কলের মাধ্যমেও আলোচনা করেন অনেকেই।
তাই প্রফেসরের সঙ্গে সবসময়েই যোগাযোগ করে আগে থেকেই ফান্ডিং নির্ধারণ করে নেওয়াটা সবসময় জরুরি না হলেও, যোগাযোগ করাটাই ভাল। এ ছাড়াও যোগাযোগ করতে হবে ডিজিএস কিংবা সেই বিভাগের ডিরেক্টর অফ গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের সঙ্গে। এতে আসলে ওয়েবসাইটে সাধারণভাবে যেসব তথ্য দেওয়া থাকে সেগুলো ছাড়াও আরও অনেক কিছু জানতে পারা যায়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে কোনো তথ্য সাদামাটাভাবে দেওয়া থাকলেও একেকটি বিভাগের পলিসি, আবেদনের জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলো আসলে একেক রকম হয়।
যেমন- ল্যাগুয়েজ টেস্টের স্কোর কিংবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটা ডিগ্রি সম্পন্ন করলেও পরে পিএইচডির জন্য আবার এই পরীক্ষায় বসতে হবে কি না, এগুলো একেবারেই নির্ভর করছে একেকটি বিভাগ কিংবা বিভিন্ন কলেজের পলিসির ওপরে। তাই সময়সাধ্য হলেও সব থেকে ভাল হচ্ছে যোগাযোগের মধ্যে থাকা।
নাদিয়া রহমান: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) ও যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব কেন্টাকির শিক্ষার্থী।











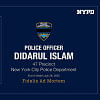

Comments