বিশ্ববিদ্যালয়ে যা আছে যা নেই
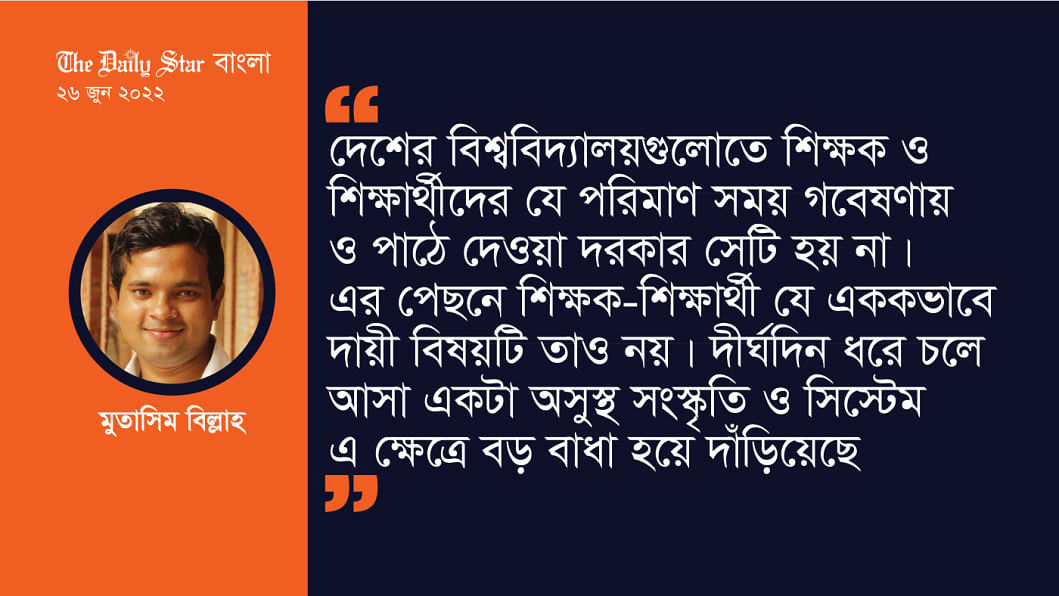
বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নানা সম্পর্ক আছে। কখনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, কখনো ক্রীড়াঙ্গনে, কখনো বা রাজনৈতিক অঙ্গনে। কিন্তু, সবচেয়ে বেশি যেখানে উভয়ের সম্পর্ক অটুট থাকার কথা সেখানে একটা দৃশ্যমান শূন্যতা বিরাজ করছে দীর্ঘদীন ধরে।
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানের, গবেষণার সম্পর্কটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। যতটুকু আছে, তা উভয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। জ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর সঙ্গে চর্চার বড় একটা পার্থক্য আছে এখানে।
দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যে পরিমান সময় গবেষণায় ও পাঠে দেওয়া দরকার সেটি হয় না। এর পেছনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী যে এককভাবে দায়ী বিষয়টি তাও নয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটা অসুস্থ সংস্কৃতি ও সিস্টেম এ ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
একটা অজানা জুজুর ভয় আছে। তাই চাইলেও একজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নিবিড়ভাবে পঠন-পাঠে, গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারছে না। গবেষণায় ও পাঠে সময় দেওয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের চেয়ে শুধুমাত্র মাঠে সময় দেওয়া যারা তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্মে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন। সুযোগ-সুবিধা, পাওয়ার প্র্যাকটিস সবই ভোগ করেন। বরং অধিকাংশ সময় এই মাঠে থাকা মানুষগুলো পাঠ ও গবেষণায় থাকা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হয়রানি করেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাঠের চেয়ে মাঠে থেকে হিরো হওয়াদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভাগভিত্তিক রিসার্চ অর্গানাইজেশন/ক্লাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, রিডিং ক্লাব, ভালো রেজাল্ট ও ভালো গবেষণায় উৎসাহিত করতে বৃত্তি, গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের কল্যাণ ফান্ড নেই। ব্যতিক্রম কিছু জায়গায় থাকলেও এর জন্য বরাদ্দ খুব বেশি নেই। অল্প কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে যা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।
রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে গবেষণা করার যে রসদ শিক্ষার্থীদের পাওয়া দরকার তা তারা পান না। বরং অধিকাংশ বাজেটই ব্যয় হয় অবকাঠামোসহ অন্যান্য কাজে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দৃশ্যমান চোখ জুড়ানো অবকাঠামাতে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে অবকাঠামো গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য খুব একটা কল্যাণ বয়ে আনে না।
বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি থাকলেও শিক্ষার্থীদের টিএসসিমুখী হওয়ার, সেখানে বিভিন্ন ভাষা শেখার, বিভিন্ন সংস্কৃতিকে জানার, চর্চার সুযোগ ও পরিবেশ নেই। ফলে আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠে বিশ্বমানের চিন্তা করার গ্রাউন্ডই শিক্ষার্থীরা পান না।
অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে প্রাথমিক যে জ্ঞান থাকা দরকার সে ফাউন্ডেশন তৈরির সুযোগ এখানে থাকে না। বিভাগগুলোতে বিষয়ভিত্তিক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজনও খুব কম থাকে। ভাষাগত দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক অনলাইন বা অফলাইন কর্মসূচীগুলোও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না। এর ফলে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ভাষাগত ও প্রযুক্তিগত দূর্বলতা থেকে যায়।
গবেষণা প্রবন্ধ বা নিবন্ধ কিভাবে লিখতে হয় সেই হাতেখড়িরও ভালো পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। টেক্সট থেকে বই পড়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারায় জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যে সংযোগ ঘটানো দরকার, জ্ঞানের যে মূল স্বাদ, রূপ, রস, ঘ্রাণ—তা থেকে অনেক সময় বঞ্চিত থাকে শিক্ষার্থীরা। জ্ঞানকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে না পারার কারণে অধিকাংশ সময়ই আমরা জ্ঞানকে নিরস বানিয়ে ফেলি। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে এখনো নকল করার প্রবণতা, আরেকজনের থেকে দেখে লেখার মানসিকতার খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি।
গতানুগতিক প্রশ্নে সিনিয়রদের নোট সহজে মেলায়, তার ওপরই অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে ভরসা করতে দেখা যায়। মূল বই থেকে পড়ার বিষয়ে এক ধরণের নেতিবাচক মানসিকতার সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খুব দাপটের সঙ্গেই আছে। এতে করে জ্ঞানের বিষয়ে, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে একটা নেতিবাচক ধারণা নিয়েই ক্যাম্পাস জীবন শেষ করতে হয় অধিকাংশ শিক্ষার্থীর।
অনেকে আবার চাকরি পাওয়ার মধ্য দিয়েই একটা প্রশান্তি পান যে, জীবনে আর জ্ঞানার্জনের মতো নিরস কাজ করতে হবে না। এমন বেঁচে যাওয়ার ভাবনা থেকে জ্ঞানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের মনো-সংযোগ না থাকার কারণে শিক্ষিত মানুষও দিন দিনে মূর্খ হয়ে যান। তা ব্যক্তি নিজে জানতে না পারলেও তার আচার-আচরণ, কর্মে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ কারণে দেশের শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের কাজের মধ্যে খুব একটা পার্থক্যও দেখা যায় না। বরং কখনো কখনো নিরক্ষর মানুষের চেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন সনদপ্রাপ্ত শিক্ষিত মানুষ।
শিক্ষকের জ্ঞানের রাজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য ট্রেনিং, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের বিষয়ে সর্বোচ্চ আয়োজন, গবেষণা সহায়তাকারী সফটওয়্যার, আন্তর্জাতিক সেরা জার্নালগুলোর পড়ার সুযোগ এখনো অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এতে শিক্ষকরা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা সম্পর্কে জানা-শোনার বাইরে থেকে যান।
অপরদিকে ভাষাগত ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতা শুধু শিক্ষার্থীদের যে বিষয়টি তা নয়, বরং অধিকাংশ শিক্ষকদেরও আছে। এর বিকাশ সাধনে সময়, সুযোগ ও পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। শিক্ষকদের গবেষণা সহকারী না থাকায় আবার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার সিস্টেম চালু থাকায়, গবেষণামূখী কাজের চেয়ে মিড বা ফাইনাল পরীক্ষা দেখা, প্রশ্ন করা, ক্লাস নেওয়া—এতেই দীর্ঘ সময় চলে যায়। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রেজাল্ট তৈরি করতে একটা দীর্ঘসময় ব্যয় হয়। যা গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা।
বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরা শিক্ষক, গবেষককে জায়গা করে দিতে না পারলে বঞ্চিত হবে গোটা জাতি। সেরা শিক্ষকদের গবেষণার প্রণোদনা, উৎসাহ, সহযোগিতা, যথাযথ সম্মান না করলে সৃষ্টিশীল-সৃজনশীল এ মানুষগুলোর কাজও মন্থর গতি পাবে। একটা দেশকে সুস্থ ধারায় পরিচালনা করতে চাইলে রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সঠিকভাবে পরিচালনায় উপযুক্ত, সৎ, যোগ্য, দক্ষ শিক্ষকদের সুযোগ দিতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা, গবেষণাকে দিতে হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। একজন দুস্কৃতিকারীর সন্তান যেমন পরিবারের জন্য ক্ষতিকর, বিপরীতভাবে এলাকার ভালো সন্তান দেশ, রাষ্ট্র, পৃথিবী সবার জন্যই উপকার। তাই দল, মত, ধর্ম, গোত্র, বর্ণের চেয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার, যারা নিজেদের সামগ্রিক জীবনকে সপে দিয়েছে গবেষণায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে।
সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অবাধে মাদক ও সময় নষ্ট করার সংস্কৃতির বদলে পাঠে, গবেষণায়, নিবিড়ভাবে মনোনিবেশের পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে একটি জাতি ও রাষ্ট্র কখনো তার শিখরে পৌঁছাতে পারবে না। দেশও মুক্তি পাবে না দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে।
মুতাসিম বিল্লাহ: শিক্ষক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নেবে না।)





Comments