মফস্বলে সাহিত্য চর্চার সংগ্রাম
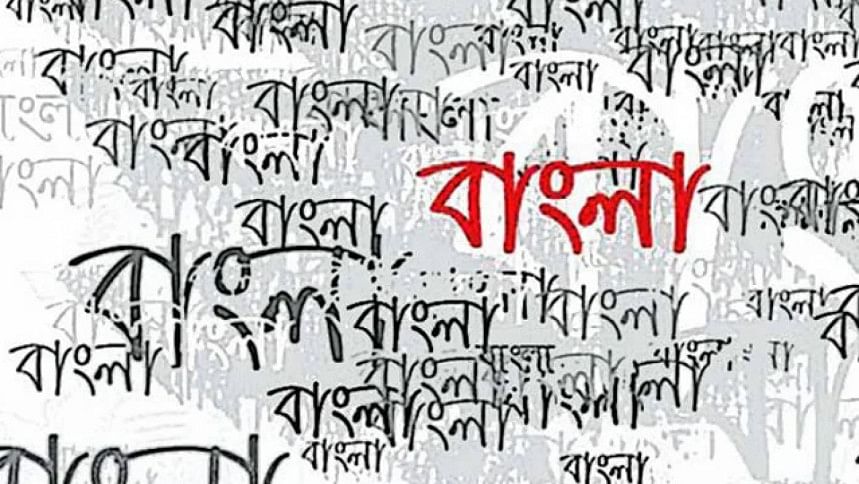
বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা আদতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সাহিত্য। দেশের শতভাগ শিক্ষিত নয়, যে অংশটা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন তাদের সিংহভাগের এই শিক্ষিত মানুষের সাহিত্যে আগ্রহ নেই। তাই এদের সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। আবার এদের বড় একটা অংশ উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশিত সামান্য কিছু সাহিত্যের বাইরে খুব একটা বেশি কিছু পড়ে বলে মনে হয় না। এদের আবাস প্রধানত নগরে।
এ-শিক্ষিত মধ্যবর্গের বাইরে যে বিপুল জনগোষ্ঠী আছে তাদের নিজেদের সাহিত্য-শিল্পকলার চর্চা আছে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাংলাদেশের সাহিত্য বলে প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাসীগণ না-ওয়াকিফ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এ-বর্গের সাহিত্য-শিল্পকলা দেশের সাহিত্য হিসেবে গণ্য হয় না। অন্তত বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে যে ধারণাটি প্রচলিত তাতে এদের সাহিত্যশিল্পকলার উল্লেখ চোখে পড়ে না। আবার ওরাও মধ্যবর্গের সাহিত্য সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে বলে মনে হয় না। এদেরকে যদি দেশের সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের নাম জিজ্ঞেস করা হয় এরা বলতে পারবে না।
এদের জীবনচর্যা নিয়ে লিখে মধ্যবর্গের বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এমন একজন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। অথচ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নাম ওরা শোনে নি। আমাদের এ সময়ের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সাদাত হোসাইনকে ওরা চেনে না। এমনকি ফেসবুকে সক্রিয় থেকে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছেন কবি ইমতিয়াজ মাহমুদ তাঁর নামও এরা জানে না। অথচ ফেসবুক একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।
এখানে কমবেশি সকল বর্গের প্রবেশাধিকার প্রায় সমান। এরা প্রধানত ইউটিউবে অভ্যস্ত। তা-ই রিপন ভিডিও ওদের কাছে বেশি জনপ্রিয়। বাস্তবতা হলো, আমাদের প্রচলিত সাহিত্য এরা পড়ে না। কোনো জরিপ হয় নি তবে আন্দাজ করে একটু বাড়িয়ে না বললেও আমার ধারণা বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা শতকরা দশভাগ মানুষের সাহিত্য। বাকি নব্বইভাগ এ-সাহিত্যের বাইরে থাকলেও সংখালঘুর সাহিত্যকেই আমরা 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলে মেনে নিয়েছি।
দুই
বাংলাদেশের সাহিত্য নাগরিক, শিক্ষিত মধ্যবর্গের সাহিত্য। অতীতে ছিলো, এখনো তাই আছে। প্রযুক্তির কল্যাণে এর পাঠক সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে হয় না। তবে পাঠকদের মধ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার বোধ করি বাড়ছে। আমাদের নগরবিদ নজরুল ইসলাম এ শতকের শুরুর দিকে বলেছিলেন আগামী পনেরো বছরে বাংলাদেশ একটি নগর রাষ্ট্র হয়ে উঠবে। সে হিসেবে বাংলাদেশ নগররাষ্ট্র হয়ে উঠেছে। গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুত চলে গেছে, একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামে মানুষ সিলিন্ডার গ্যাসের চুলা ব্যবহার করছে, জনবসতি নগরের ঘনত্ব ছাড়িয়ে গেছে, ঘরের ভেতরের বাথরুমগুলো টাইলস, কমোডে সজ্জিত হয়ে গেছে। গ্রামের বাজারগুলোতে টাইলসের দোকান, স্মার্ট ফোনের শোরুম, পাকা রাস্তা, বিদ্যুত—সব মিলিয়ে নগরের বাংলাদেশি সংস্করণ আর কি! এরকম বাস্তবতায় বাংলাদেশের সাহিত্য কেবল ছাপা পত্রিকায় সীমাবদ্ধ থেকে যাবে তা মনে করার কারণ নেই। আমাদের হাল আমলের বিপুল পঠিত কবি ইমতিয়াজ মাহমুদ পরিচিতি পেয়েছেন বই প্রকাশ করে নয়, ফেসবুকে কবিতা লিখে। ভাবতে পারেন, একালের বাংলাদেশের একজন কবির ফলোয়ার ৭৮হাজার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ তিনি থাকেন বরিশালে। এ থেকে একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, লেখালেখির ফ্ল্যাটফর্ম পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কেবল বই প্রকাশ করে এখন পরিচিতি অর্জন করা দুরূহ। কেন্দ্র আর প্রান্তের দূরত্ব ঘুচে গেছে। আগে একজন ওমর আলী বা দিলওয়ার কিংবা হোসেন উদ্দিন হোসেন হওয়া যত কঠিন ছিলো এখন আর তা নেই। এখন প্রান্তে আলো জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রযুক্তি এর প্রধান কারণ।
তিন
এমন সম্ভাবনা সত্ত্বেও মফস্বলের সাহিত্যচর্চায় সবচেয়ে বড় সংকট হীনম্মন্যতাবোধ। মফস্বলের সাহিত্যচর্চার প্রধান শক্তি এর নিজস্ব উপাদানগুলো, যেমন এর ভাষা, এর জীবনযাপনের নিজস্ব রূপ। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এ-উপাদানগুলো মফস্বলের সাহিত্যিকদের রচনায় কমই দেখা যায়। বরং মফস্বলের সাহিত্যিকদের ঢাকাকে অনুসরণ করার প্রবণতা তাদের নিজস্বতাকে খর্ব করে। কেন্দ্রের জীবনটা তার নয় তাই অন্ধ অনুকরণ করে যে সাহিত্য তৈরি হয় তা দুর্বল ও মেকি। নিজের প্রাণের স্পন্দন তাতে থাকে না।
এসব সাহিত্য কোনো কাজের হয় না। আল মাহমুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ ছিলেন, ঢাকায় গিয়ে তিনি নিজ মফস্বলকে লিখেছেন। তাই কবি হতে পেরেছেন। উদাহরণ হিসেবে আরেক শহর ফেনীর নাম নেওয়া যায়। ফেনীর কবিদের দেখি না নিজের যাপিত জীবনের বাস্তবতা নিয়ে কলম ধরতে। ফেনীর সবচেয়ে বড় সমস্যা রাজনৈতিক-দস্যুতা। এখানে বাহিনির নাম পুলিশ নয়, 'টাইগার' কিংবা 'ক্লাস'। এখানে ল্যাটিনের যাদুবাস্তবতা নিরেট বাস্তব হয়ে দেখা দেয়।
গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কজের উপন্যাসের মতো প্রেমে পড়লে পানি রঙিন হতে থাকে, সুন্দরী অ্যামাদিউস আকাশে উড়ে যায়, এখানে বুয়েন্দিয়ারা চৌদ্দটি হামলা, তেষট্টিটি অ্যামবুশ, আর একটি ফায়রিং স্কোয়াডের হাত থেকে অলৌকিক ভাবে বেঁচে যায়। একই দলের কর্মীকে হত্যা করে বিপক্ষ দলের কর্মীর নামে মামলা হয়, একটা জ্যান্ত মানুষকে ড্রিলমেশিনে ছিদ্র করে মেরে ফেলা হয়। এখানে পলাতক গ্যাংস্টার নেতার বাড়িতে মানুষ হরিণ, ঘোড়া আর হেলিকপ্টার দেখা যায়। কিন্তু এসব সাহিত্যের বিষয় হয় না। ঢাকার বাইরে যাঁরা লেখালিখি করেন, তাঁরা মনে করতে থাকেন, লেখা ঢাকার মতো হচ্ছে না। ঢাকার বড় কারো সনদ দরকার। ঢাকাকে অনুসরণ করাটাই একমাত্র মোক্ষলাভ। আমি নিজেও মফস্বলে থাকি, অনেকে আমাকে লেখা দেখান। আমি পড়তে গিয়ে হতাশ হই। আমার মনে হতে থাকে ঢাকার অনুকরণে এসব লেখা কেমন যেন আলগা, উপরিতলের, তরল, হাস্যকর রচনা।
ফেনী এতো চমৎকার একটা শহর, খুব কাছেই একটা নিস্তরঙ্গ নদী আছে। কিন্তু এঁদের লেখায় তার প্রতিফলন দেখি না। আল মাহমুদ কবি হয়েছেন তিতাসকে লিখে। কুমিল্লার কান্দিরপাড়ের উপচে পড়া যে জীবন, ক্ষীণতোয়া হয়ে পড়া যে গোমতী কিংবা ক্রমশ রাস্তা হয়ে ওঠা চাঁনপুরের খালটা এঁদের লেখায় উঠে আসে না। ঢাকার প্রতি কাঙালিপনার একটা দৃষ্টান্ত হতে পারে কোনো অনুষ্ঠান করতে হলে ঢাকার অতিথি চাই। অথচ সুনামগঞ্জে বসে বসে গান লিখে হাসন রাজা অমর হয়েছেন, রাধারমণকে ঢাকাকে অনুসরণ করতে হয়নি। নিজের যা আছে তাকে অবলম্বন করা, নিজের দিকে তাকানো ধাতে সয় না। ঘাসের ডগার শিশিরবিন্দু হীরার টুকরো হয়ে জ্বলে ওঠে না এখানে।
অথচ ঢাকায় বসবাসকারী লেখককে দেখেছি মফস্বল শহরের কিংবদন্তি, মিথ বা ইতিহাসের প্রান্তিক রচনা নিয়ে লিখে খ্যাতি অর্জন করছেন। হাল আমলের উদাহরণ হিসেবে নোয়াখালীর 'চৌধুরীর লড়াই' পুথির গল্প ব্যবহার করে শাহীন আখতার লিখেছেন 'সখী রঙ্গমালা'। কুমিল্লার 'নডির মসজিদে'র ঘটনা নিয়ে লেখা 'রাজনটী' লিখে পরিচিতি পাচ্ছেন স্বকৃত নোমান। ভাবতে পারেন এসব রচনা যদি স্থানীয় জীবন-যাপনে অভ্যস্ত কারো হাতে লেখা হতো তাহলে কেমন জীবন্ত হয়ে উঠতো! আমার বলবার বিষয় এই যে, বিষয়, ভাব আর আঙ্গিকের খোঁজে কেন্দ্রের দিকে না তাকিয়ে থেকে নিজের যা আছে তা বেছে নিলে মফস্বলের সাহিত্যের জন্য মঙ্গল ।
চার
মফস্বলে বসবাস করে 'বাংলাদেশের সাহিত্য' চর্চা করা এখন যেমন সহজ হয়ে গেছে তেমনি মফস্বলে থাকার হীনম্মন্যতার বোধ এ-ক্ষেত্রে বেশিদূর এগোতে দিচ্ছে না। এর সঙ্গে আমি জুড়ে দিতে চাই আর একটা জরুরি বিষয়্। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূচনা হিসেবে হিসেবে ধরা হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যকে। মাইকেল হাত বাড়িয়ে নিয়েছিলেন প্রধানত ইউরোপ থেকে। সেকালে ধার গ্রহণ বিষয়ে পরবর্তী পর্বের আধুনিকদের বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ করা যায়।
এমন একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, বিশ্বের সেই 'আদিম উর্বতা' আর নেই। বিশ্বভ্রমাণ্ড ঘুরে ঘুরে বীজ সংগ্রহ না করলে কবিতার নাকি 'কল্পতরু' জন্মায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ্বভ্রমাণ্ডের বীজে কেবল আমাদের চিড়ে ভেজে নি। নিজের ইতিহাস ঐতিহ্যের দিকেও তাকাতে হয়েছে। সেভাবেই জসীমউদদীন আমাদের হয়ে আছেন। আল মাহমুদ আমাদের হয়ে গেছেন। রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কিংবা সৈয়দ শামসুল হক মাঝেমধ্যে মফস্বলের ভাষায় লিখে চমৎকৃত করেছেন।
বাংলাদেশের সাহিত্যে মফস্বলের সাহিত্যিককে টিকে থাকতে হলে অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে হলে সে জন্য দরকার হবে সমসাময়িক সাহিত্যের খোঁজখবর রাখা। সেটা কেবল ঢাকার সাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যের প্রধানপ্রধান প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিফ থাকা। একসময় আধুনিকতার পর্বান্তরে আমাদের আধনিকেরা অনুসরণকে অনুকরণে রূপান্তরিত করেন। ফলে আমাদের সাহিত্য আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরীদের কোনো কোনো কবিতা পড়লে মনে হবে এগুলো ষাটের দশকের মার্কিনী কবির বাংলা রচনা। দেবেশ রায়তো বঙ্কিম থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন পশ্চিমা গল্প কাঠামোর আদলে বাংলাকে ধরতে গিয়ে কীভাবে বাংলা উপন্যাস জীবনকে হারিয়েছে। গল্পের কঙ্কাল হয়ে উঠেছে।
এজন্য এসব পাঠ হবে প্রবণতা বোঝার জন্য অন্ধ অনুকরণের জন্য নয়। নজরুল পশ্চিমের সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কিন্তু তিনি পশ্চিমের নন্দনে আস্থাশীল ছিলেন না। তাই পশ্চিমা নন্দনে তিনি খারিজ হয়ে গেলেও দেশীয় সাহিত্য-সমাজ মহলে ভীষণভাবে তরতাজা হয়ে আছেন। তাই বিম্ভভ্রমাণ্ড ভ্রমণের সময়ে সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলতে হবে। এ-পথটা সৃজনশীল লেখক নিজেই বের করে নেবেন। অঞ্চল থেকে জাতীয়, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিকতার দিকে যেতে চাইলে আরেকটি বিষয়ও মাথায় রাখতে হবে।
বর্তমান জামানায় হারুকি মুরাকামি বিশ্ব চষে বেড়াচ্ছেন। তিনি এ-অর্জন করেছেন এক রকমের বিশ্বজনীনতার বোধ দিয়ে। তাঁর সাহিত্যে আছে জাপান, জাপানের জনপদ কিন্তু তা কখনো সংকীর্ণ আঞ্চলিকতায় আবদ্ধ নয়। মার্কেসের মাকুন্দো বা নাম না জানা গ্রাম্য শহরগুলো কোনোটিই সংকীর্ণ আঞ্চলিক হয়ে ওঠে না। মুরাকামির গল্পে জাপানের অলিগলির নাম থাকলেও ভাব ও ভাষায় এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যে কোনো দেশের পাঠক তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। প্রাচীনকালে লঙ্গিনুস এটাকে বলছিলেন পাঠকের কাছে ''সঞ্চারিত হওয়া। যাপিত-জীবনকে তুলে আনা আর সেটাকে পাঠক-সর্বজনের জন্য বোধগম্য করে তোলাই লেখকের দায়িত্ব। তবেই লেখার সফলতা।








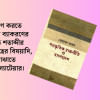

Comments