প্রমিত বাংলা কি বাঙালির দ্বিতীয় ভাষা?
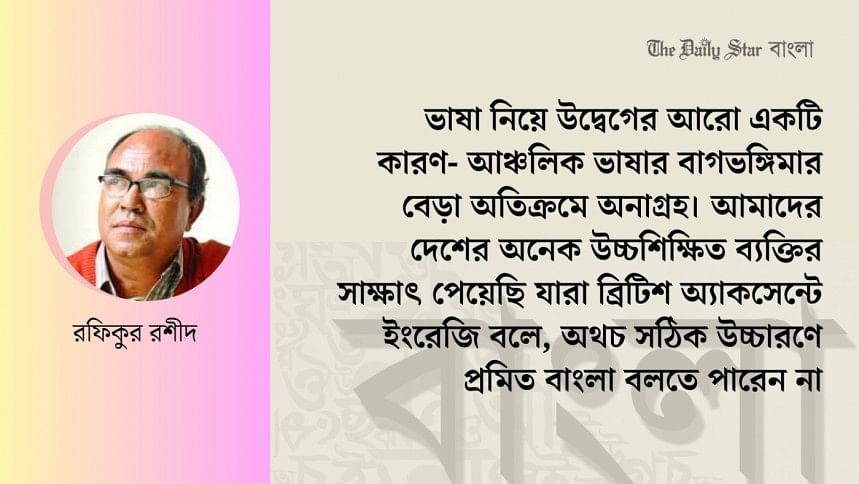
ভাষা নিয়ে ভাবতে গিয়ে এক জায়গায় এসে ভারি খটকা লাগে। মাতৃভাষার সঙ্গে মান-ভাষা বা প্রমিত ভাষার কি বিরাট কোনো বিরোধ আছে? সহাবস্থানের সমান্তরালে কি প্রবাহিত হতে পারে না দুটি ধারা? আমাদের অতি আদরণীয় বাংলা ভাষার কথাই ধরা যাক। এত যে লড়াই-সংগ্রাম, এত যে ত্যাগ-তিতিক্ষা- অশ্রুপাত এই মধুর ভাষার জন্যেই তো!
মায়ের মতো সর্বংসহা এই ভাষার মধ্যেই জন্মগ্রহণ এবং জীবনযাপন করেও সব অঞ্চলের বাংলাভাষী কি সহজ-সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করতে পারছে বাংলা ভাষা? হ্যাঁ মানি বটে, আয়তনে ছোটো হলেও আমাদের এই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় বিশাল বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য ক্ষেত্র- বিশেষে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে দুর্বোধ্য আড়ষ্টতা এবং দূরত্বও সৃষ্টি করেছে। নোয়াখালীর ভাষা খুলনার মানুষ বোঝে না, বরিশালের মানুষ বোঝে না চট্টগ্রামের ভাষা। অথচ বাঙালি আমরা সবাই, বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা ; তাহলে মাতৃভাষা কোনটি?
খুব সহজভাবে বলতে গেলে মায়ের মুখের ভাষাকেই সবাই মাতৃভাষা বলবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। জন্মদাত্রী মানবী- মা এবং দেশমাতার ভাষা কি সর্বদা অভিন্ন হয়? মাতৃদুগ্ধ পান কেমন করে করতে হয়, সেটাও যেমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিখে নেয় শিশু, মাতৃভাষা শেখার ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকমই। ব্যাকরণ বা মাস্টারমশাইয়ের শাসন-বারণ লাগে না।
শিক্ষার্থী বারংবারের চেষ্টায়, নিজে থেকে নিজের ভুল শুধরে নিয়ে ব্যাখ্যাতীত স্বাভাবিকতায় শিখে নেয় তার মাতৃভাষা। জন্মসূত্রে মায়ের মুখের বুলি অনুসরণ করেই মানুষের ভাষা-শিক্ষার সূচনা হয়। যেমন শোনে, তেমনই শেখে ভাষা, আবার সে ভাষার তেমন ব্যবহারেই অভ্যস্ত হয়। সেটাই স্বাভাবিক। উচ্চারণ, বাগরীতি, ক্রিয়াপদের ব্যবহার, বাক্য গঠন ভঙ্গিমা-- এ সব কিছু মানুষ লাভ করে বিশেষ প্রশিক্ষণ বা আলাদা প্রচেষ্টা ছাড়াই তার মায়ের কাছ থেকে। এই ভঙ্গিতেই তার স্বস্তি, আরাম এবং আনন্দও। আর এই আনন্দের ভাষাই মাতৃভাষা।
মাতৃভাষার চেয়ে আনন্দময় এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ- মাধ্যম আর কীইবা হতে পারে! আমাদের দেশের অন্যতম এক প্রধান কবি একদা দাবি করেছিলেন-- চাটগাঁইয়া ভাষাই তার মাতৃভাষা, আর বাংলা তাঁর দ্বিতীয় প্রধান ভাষা। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র তিনি, ইংরেজি সাহিত্যেও বিস্তর দখল তাঁর; কবিতা লেখেন বাংলায়। সে বোধ হয় বছর তিরিশেক পেছনের কথা, তখন খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম বাংলাকে তাঁর দ্বিতীয় ভাষা বলায়। এখন বুঝি তাঁর এ বক্তব্যে সততা ছিল এক শ' ভাগ, সেদিন তিনি অকপটেই উচ্চারণ করেছিলেন-- চাটগাঁইয়া তাঁর মাতৃভাষা।
বড়ো হতে হতে মানুষের কত কিছু বদলায়। ঘষে-মেজে রঙে-রূপে বদলায়। চেহারায় শুধু নয়, চরিত্রেও বদলায়। মানুষ দীরে ধীরে জন্মের আবিলতা ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসে পরিচ্ছন্নতায়। তাই বলে ফেলে আসা আবিলতার কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। প্রয়োজনে মানুষ নিজের উত্তরণ ঘটায়।
শৈশব থেকে বড়ো হতে হতে, স্কুল-কলেজে যেতে যেতে, বই- পুস্তক ও শিক্ষিত মানুষের সংস্পর্শে আসতে আসতে শিশুর স্বাভাবিক ভাষা- প্রবাহ কিঞ্চিত বিঘ্নিত হয়, পরিমার্জিত হয় ; সেই সাথে খানিকটা কৃত্রিমও হয়ে ওঠে। পণ্ডিতেরা বলেন- প্রমিত হয়ে ওঠে। এভাবেই ধীরে ধীরে মানভাষার স্তরে উন্নীত হয়। ভাষার মান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই মান-ভাষায় পৌঁছুতে গিয়ে ভাষার স্বাভাবিকতা ও সাবলীলতা যে ব্যহত হয় এটাও মানতে হবে।
মানুষের মুখের ভাষা তো নদীর স্রোতের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমান। বাধাবন্ধন তার গতি।মানুষ তার প্রয়োজনে নদীকেও শাসন করে, তার স্রোতধারাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। স্বাভাবিক গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে নদীর গতিমুখ পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় মানুষ, অনেক সময় সফলও হয়। ভাষার গতির ক্ষেত্রেও কি এই প্রচেষ্টা সফল হয়! মানবসৃষ্ট সেই কৃত্রিম এবং জগাখিচুড়ি ভাষা যতই বুদ্ধি ও মেধাশাসিত হোক না কেন তা যে কালের বিচারে টেকসই হয় না, সে প্রমাণ ভাষার ইতিহাস ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে। তবে মান- ভাষার ব্যাপারটা আলাদা। পৃথিবীর প্রায় সব উন্নত ভাষাই অসংখ্য আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যময় বাগান থেকে পুষ্পরাজি চয়ন করে নতুন সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে, সুরভিত হয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।
চর্যাপদের ভাষা আর বঙ্কিমের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ভাষা আর জীবনানন্দের ভাষা অভিন্ন সেই বাংলা ভাষাই বটে, তবু সময়ের চাকা ঘূর্ণনে ও ঘর্ষণে কত না পরিবর্তন ঘটেছে এবং জীবন্ত ভাষা বলেই আধুনিক বাংলা ভাষায় এখনো সে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এ পরিবর্তন অনিবার্য, ভাষার বাঁচা-মরার প্রশ্নেই সেটা অনিবার্য। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে পরিবর্তনের নামে আমাদের ঐশ্বর্যময়ই বাংলা ভাষায় বিচিত্র শব্দপ্রয়োগ, বিকৃত উচ্চারণসহ আরও যে সব নর্তন-কুর্দনের আলামত দেখা দেখা যাচ্ছে তাতে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না।
ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের আরো একটি কারণ- আঞ্চলিক ভাষার বাগভঙ্গিমার বেড়া অতিক্রমে অনাগ্রহ কিংবা অক্ষমতা। আমাদের দেশের অনেক উচ্চশিক্ষিত (এমন কি বাংলায় এমএ পর্যন্ত) ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি যারা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলেন, অথচ সঠিক উচ্চারণে প্রমিত বাংলা বলতে পারেন না। ক্লাসরুমের শিক্ষকতায় কিংবা আদালতের ওকালতিতেও অসংকোচে আঞ্চলিক বাংলা উচ্চারণ করেন। এ জন্যে কোনো গ্লানিবোধ নেই। কারণ জানতে চাইলে দিব্যি বলে, 'ছুডুকালের অভ্যাস যে! ' আহা, এখন তো অনেক বড়ো হয়েছেন, ছোটোবেলার অনেক অভ্যাসই তো পরিত্যাগ করেছেন, শিক্ষিত মানুষ হয়েও শুধু মুখের ভাষার বেলাতেই পিছিয়ে থাকবেন? তখনও স্মিতহাস্যে কেউ কেউ অবলীলায় বলেন, ' মায়ের ভাষা মিডা লাগে যে! ' মুখের ভাষার এই মিষ্টতার পরে আর কোনো যুক্তিই চলে না।
মাতৃদুগ্ধের মিস্টতাও তো আমরা এক সময় পরিহার করি, প্রয়োজনে অন্যান্য খাদ্য উপাদানে মিষ্টত্বের সন্ধান করি। ভাষার প্রশ্নেও সেই কথা খাটে। আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক। আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে নয়, সেই ভাষাভঙ্গির সৌন্দর্যসুধা প্রমিত ভাষাভঙ্গিতে যুক্ত করে সবাই মিলে ব্যবহার করতে না পারলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে। একাত্তরে এত বড়ো যুদ্ধজয়ের পরও 'পূর্ববঙ্গের বাঙাল' পরিচয় অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদের পরিচয়ে সত্যিকারের বাঙালি হয়ে উঠতে আর কতদিন লাগবে?
তিরিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে এবং বহু বছরের সাধনায়-সংগ্রামে পাওয়া আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একদা পরিচিতি ছিল 'পূর্ববঙ্গ' নামে। আর এই পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের নিজস্ব ভাষা-বৈশিষ্ট্যের কারণে বলা হতো 'বাঙাল। ' ভারতের বাংলাভাষীরা এখনো সুযোগ পেলেই বাঙাল বলে কটাক্ষ করে। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসের বাস্তবতা হচ্ছে এই বাঙালেরাই বাঙালিত্বের অহংকারে এবং বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দেশে বাংলাভাষী মানুষের বাস আছে ঠিকই, তবু জাতীয়তাভিত্তিক পরিচয়ে এই বাংলাদেশের নাগরিকেরাই মাথা উঁচু করে দাবি জানাতে পারে আমরা বাঙালি, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরাই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছি। তবু কি প্রমিত বাংলা কিংবা মান-ভাষা বাংলা এ দেশের মানুষের কাছে 'দ্বিতীয় ভাষা' হয়েই থাকবে? ইংরেজিসহ যে কোনো বিদেশি ভাষা সড়গড় করে শিখতে পারবে বাঙালি, ব্যবহারও করতে পারবে তার প্রয়োজনে, কেবল নিজের ভাষা বাংলাকেই পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের বাংলাভাষীর কাছে সমান বোধগম্য করে উপস্থাপন করতে পারবে না?





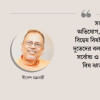




Comments