নদী খুন করে বন্যার জন্য কান্না!
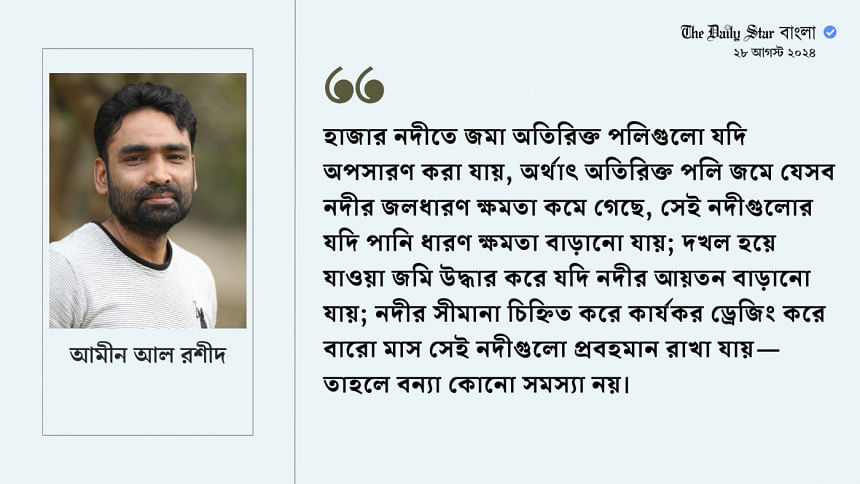
দেশের পূর্বাঞ্চলের ১১টি জেলায় চলমান বন্যাকে অনেকেই অস্বাভাবিক বলছেন। বন্যার কারণ নিয়ে নানাজন নানা বিশ্লেষণ দিচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, নদীমাতৃক দেশের নদীগুলো ঠিক থাকলে কোনো বন্যাই কি আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হতো?
কুমিল্লা, ফেনী ও নোয়াখালী অঞ্চলের নদী, খাল, জলাশয় ও নিম্নাঞ্চলগুলোয় পানির ধারণ ক্ষমতা কেমন? উজানের দেশ ভারত থেকে আসা পানির কারণে হোক কিংবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অতিবৃষ্টির কারণে—বন্যা হলে সেই পানি এসব জলপথ ধরে সমুদ্রে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা কি আছে? বহু বছর ধরে যে পানি ধরে রাখার জন্য রিজার্ভার তৈরির আলোচনা আছে, সেটি কি আদৌ আলোর মুখ দেখবে?
অতএব কুমিল্লা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনীসহ আশেপাশের এলাকায় বন্যা চলাকালীনই এই বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। নদী, পরিবেশ ও প্রাণ-প্রকৃতি সুরক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের জানমাল বাঁচানোর ইস্যুতে আত্মসমালোচনাও জরুরি।
কেমন আছে কুমিল্লা ও ফেনীর নদী?
বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু খবরের দিকে নজর দেওয়া যাক।
১. কুমিল্লার গোমতী নদীর সংযোগ থেকে চাঁদপুরের মেঘনা নদীর সংযোগ পর্যন্ত প্রায় ৬০-৬২ মাইলজুড়ে ডাকাতিয়া নদীর অবস্থান। শুকনো মৌসুমে এ নদী প্রায় পানিশূন্য হয়ে যায়। কুমিল্লার লাকসাম, লালমাই-মনোহরগঞ্জ উপজেলা হয়ে লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর জেলা পর্যন্ত মাইলের পর মাইল এলাকাজুড়ে কচুরিপানা ও পলি মাটি জমে ভরাট হয়ে গেছে। তার ওপর ডাকাতিয়া নদীর দুইপাড়ে স্থানীয় প্রভাবশালীদের জবরদখল। শুকনো মৌসুমে নদী, খাল, বিল, পুকুর, জলাশয়, ডোবা পানিশূন্য থাকে। অর্ধশতাধিক খাল জবর দখলের কারণে মৃতপ্রায়।
২. কুমিল্লার খরস্রোতা গোমতী নদী এখন দখল, দূষণে বিপর্যস্ত। নদীর কোথাও জলের ক্ষীণধারা, কোথাও চর। নদী থেকে বালু উত্তোলন ও অবাধে মাটি কেটে পানি দূষিত করা হচ্ছে। প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ আঁকাবাঁকা এ নদীর দুই পাশের অংশ ধীরে ধীরে দখল করে বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনসহ নানা স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে।
৩. কুমিল্লার তিতাস উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অবৈধভাবে দখল-ভরাটের কারণে অস্তিত্ব হারাচ্ছে কয়েকটি খাল। অনেক খাল এরইমধ্যে শুকিয়ে গেছে। ফলে প্রয়োজনীয় পানি না থাকায় সেচ সংকটে অনাবাদী থাকে হাজারো হেক্টর জমির ফসল। উপজেলার জিয়ারকান্দি ইউনিয়নের গোপালপুর হিন্দুপাড় সংলগ্ন ব্রিজের নিচের খালটি অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে। এক সময় মালামাল নিয়ে ভারী নৌযান চলাচল করলেও দুই পাড় ভরাট হয়ে যাওয়ায় খালটি অস্তিত্ব হারাতে বসেছে।
৪. কুমিল্লা শহরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য গত শতাব্দীর ষাটের দশকে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ বদলে দেওয়া হয়। শহরের অংশটুকুকে লোকে পুরাতন গোমতী নামে ডাকে। কাপ্তানবাজার থেকে চানপুর পর্যন্ত এর বিস্তার। দৈর্ঘ্য ছয় কিলোমিটার। এটি এখন আর নদী নেই। এতে কোনো স্রোত বা নৌচলাচল নেই। কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নদীর ওপর পাঁচটি আড়াআড়ি বাঁধ দিয়েছে মানুষের চলাচলের জন্য। এসব বাঁধ চকবাজার, গর্জনখোলা, থানারোড, চৌধুরীপাড়া ও কাপ্তানবাজার এলাকায়। বাঁধবন্দী নদীটি সাতটি বড় ডোবার চেহারা নিয়েছে। গভীরতা কোথাও কোথাও ১০০ ফুটের নিচে নেমেছে। দুই তীরের বাসিন্দারা বছরের পর বছর ধরে নদী দখল করে বাড়িঘর তৈরি করেছে। বাঁধগুলোতে গেলে বোঝা যায়, তাঁদের গৃহস্থালি বর্জ্য ফেলার মূল জায়গা এই নদী। তারা বালু-সুরকি-মাটিও ফেলেন। নদী ভরাট করে জমি বাড়ান।
৫. নদীর দুই পাশের জায়গা প্রভাবশালীরা দখলে নিয়ে পাকা স্থাপনা নির্মাণ করায় পরিবর্তন হয়ে গেছে মুহুরি নদীর গতিপথ। ভারতের উজানে সামান্য বৃষ্টি হলে প্রবল পানির চাপে নদীর বেড়িবাঁধের বিভিন্ন স্থানে ভাঙন দেখা দেয়। উপরন্তু নদীর অন্তত ২৮ কিলোমিটার বাঁধের দুই পাশেই দখলদারদের রাজত্ব।
৬. দখল-দূষণে ফেনী শহর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে পুকুর ও জলাশয়। পানির প্রবাহ হারিয়ে মৃতপ্রায় প্রতিটি খাল। ফেনী শহর থেকে গত দুই দশকে তিন শতাধিক জলাশয় বিলীন হয়েছে। খাল ও পানির প্রবাহগুলো ভরাট হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
উন্নয়নের দোহাই দিয়ে নদী খুন
রাজধানীর চারপাশ ঘিরে থাকা বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর দুই তীরে গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানার বর্জ্যে যখন এই নদীগুলো বিপন্ন, তখন শিল্প-কারখানার মালিক এমনকি অনেক সময় সরকারের নীতিনির্ধারকদেরও অনেকে এর সাফাই গাইতে গিয়ে বলেছেন, উন্নয়ন চাইলে নদী ও পরিবেশের সঙ্গে আপোস করতে হবে।
বুড়িগঙ্গা দূষিত হয়েছে বলে রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি সরিয়ে নেওয়া হলো হেমায়েতপুরে। কিন্তু তাতে বিপন্ন হয়েছে ধলেশ্বরী। ঢাকার অদূরে গাজীপুরের তুরাগ, লবনদহ, চিলাইসহ আরও অনেক নদী বিপন্ন হয়েছে শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য এবং কারখানা গড়ে তুলতে নদীর দুই পাড় দখল করার কারণে। অথচ নদীর জায়গা দখল করে স্থাপনা গড়ে না তুললে, নদীকে নদীর মতো বইতে দিলে এবং কারখানার বর্জ্যগুলো ইটিপিতে পরিশোধন করে নদীতে ফেলা হলে নদীগুলো বিপন্ন হতো না। যেসব কারখানায় ইটিপি বা বর্জ্য শোধনাগার আছে, সেখানেও অধিকাংশ সময় এগুলো বন্ধ থাকে খরচ বাঁচানোর জন্য। কিন্তু উৎপাদন খরচ বাঁচাতে গিয়ে কারখানার মালিকরা যে দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ নদী ধ্বংস করে ফেলছেন—সেই খবর রাখেন না।
একটি নদী দখল করে তার ওপর অবকাঠামো নির্মাণ করে কিছু মানব বসতি কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দোহাই দিয়ে কিছু কল-কারখানা বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সাদা চোখে বা টাকার অংকে যে লাভ দেখা যায়, চোখের আড়ালে থেকে বা হিসাবের বাইরে থেকে যায় আরও অজস্র ক্ষতি। আমরা এই অংকটা করি না যে, নদী দখল করে দশ কোটি টাকা দিয়ে একটি শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব হলেও একশো কোটি টাকা দিয়েও একটি নদী বানানো যায় না।
শিল্প-কারখানা দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে। কিন্তু শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার নামে গত পাঁচ দশকে দেশের কতগুলো নদী ও খাল হত্যা করা হয়েছে; বিপন্ন করা হয়েছে এবং ওই শিল্প-কারখানাগুলো দেশের অর্থনীতির বিকাশে যে ভূমিকা রেখেছে তার বিনিময়ে পরিবেশ ও প্রাণ-প্রকৃতির যে ক্ষতি করলো, তার পরিমাণ কত—সেই হিসাব কি কারও কাছে আছে?
বছরের পর বছর ধরে উন্নয়নের নামে, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ছোট ছোট সেতু ও কালভার্ট বানানোর ফলে তার নিচ দিয়ে এখন আর ছোট বা মাঝারি আকারের নৌযানও চলতে পারে না। কেননা ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, এসব নদী ও খাল দিয়ে আর কোনো মানুষ ও পণ্য পরিবহন করা হবে না। কেননা পিচঢালা রাস্তা চলে গেছে তৃণমূল পর্যন্ত। এর প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেই সড়ক, সেতু ও কালভার্ট বানাতে গিয়ে যে বাংলাদেশের লাইফ লাইন অসংখ্য নদী ও খাল যে ধ্বংস করা হলো—তার অর্থনৈতিক ক্ষতি নিরূপণ করা কি সম্ভব?
বন্যা কি অভিশাপ?
বাংলাদেশ মূলত প্লাবন-ভূমি ও ভাটির দেশ। অর্থাৎ উজানের দেশ ভারতে অতিবৃষ্টি কিংবা অন্য কোনো কারণে বন্যা হলে সেই পানি নিচের দিকে অর্থাৎ ভাটির দিকে নেমে আসবে, এটিই পানির ধর্ম। আবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও অতিবৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে বন্যা হতে পারে।
বাংলাদেশের যে ভৌগলিক অবস্থান এবং এখানের যে জলবায়ু, তাতে প্রতি বছর এখানে এক বা একাধিকবার এখানে বন্যা হওয়াটা স্বাভাবিক। তাছাড়া বাংলাদেশের যে ভূপ্রাকৃতিক গঠন, তাতে এখানের মাটি ও জলাধারে বন্যা একটি বিরাট আশীর্বাদ। কেননা হাওরে যদি পানি না আসে তাহলে মাছের প্রজনন বন্ধ হয়ে যাবে। বন্যা মূলত মিষ্টি পানির প্রবাহ। এই প্রবাহ নোনা পানির স্রোতকে সরিয়ে দেয়।
হাওর অঞ্চলের কৃষিতেও বন্যার বিরাট প্রভাব রয়েছে। বন্যার সঙ্গে শুধু পানি আসে না, প্রচুর পলি আসে। যে পলি এই ভূখণ্ডের মাটিকে উর্বর করে। অর্থাৎ বন্যা না হলে মাটির ক্ষমতা বাড়বে না। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে। কিন্তু এই বন্যাই আশীর্বাদের বদলে অভিশাপে পরিণত হয় যখন বন্যার পানি আটকে থাকে বা উজান থেকে নেমে আসা, পাহাড়ি ঢল বা অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যার পানি ধরে রাখার মতো ক্ষমতা নদী, খাল ও জলাশয়গুলোর না থাকে। বন্যার পানি যদি নদী-খাল-পুকুর-ফসলের মাঠ হয়ে ভূগর্ভ ও সমুদ্রে চলে যেতে না পারে, তখনই বন্যা আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।
সমাধান কী?
নদী খুন করে বন্যার জন্য কান্না কোনো সমাধান নয়। বরং বাংলাদেশ যে হাজার নদীর দেশ, সেই হাজার নদীতে জমা অতিরিক্ত পলিগুলো যদি অপসারণ করা যায়, অর্থাৎ অতিরিক্ত পলি জমে যেসব নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমে গেছে, সেই নদীগুলোর যদি পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যায়; দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধার করে যদি নদীর আয়তন বাড়ানো যায়; নদীর সীমানা চিহ্নিত করে কার্যকর ড্রেজিং করে বারো মাস সেই নদীগুলো প্রবহমান রাখা যায়—তাহলে বন্যা কোনো সমস্যা নয়।
অতিবৃষ্টি, পাহাড়ের ঢল কিংবা উজানের দেশ থেকে বাড়তি পানি এলেও নদী যদি সেই পানি ধারণ করতে পারে এবং প্রতিটি নদীর সঙ্গে যদি অন্য নদীর সংযোগটা কার্যকর থাকে; নদীর উৎস মুখ ও মোহনায় যদি কোনো ধরনের বাধা না থাকে এবং পানি যদি নদীপথ ধরে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে—তাহলে বন্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।
বাংলাদেশের জন্য বন্যা কোনো অভিশাপ নয়, বরং আশীর্বাদ এবং বন্যা একটি ব্যবস্থাপনার বিষয়। সেজন্য রিজার্ভার খুব জরুরি। দেশের উত্তরাঞ্চলে যদি কয়েকটি বড় রিজার্ভার তৈরি করা যায় যেখানে বর্ষা ও বন্যার মৌসুমে অতিরিক্ত পানি এলেও ওই রিজার্ভার সেসব পানি ধরতে সহায়ক হবে, অন্যদিকে শুকনো মৌসুমে সেই রিজার্ভারের পানি কৃষিকাজের ব্যবহৃত হবে। কিন্তু বাংলাদেশের একটা বড় সমস্যা হলো ছোট্ট আয়তনের দেশে ১৮ কোটি মানুষের বসবাস। যে কারণে প্রচুর বাড়ি-ঘর ও স্থাপনা তৈরি করতে হয়। ফসলি জমিতে কোনো স্থাপনা গড়ে তোলা যাবে না বলে রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় থেকে বারবার নির্দেশনা দেওয়া হলেও তা আমলে নেওয়া হয়নি। প্রচুর প্লাবনভূমি, জলাধার, নিম্নাঞ্চল ভরাট করে নানারকম উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে। আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। সুতরাং, এরকম আত্মঘাতী উন্নয়ন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কথা বলা এখন সময়ের দাবি।
উজানের দেশ ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন ও নদী ব্যবস্থাপনায় যেসব বিরোধ ও মতদ্বৈততা রয়েছে, সেগুলো সুরাহা করতে কার্যকর নদী কূটনীতিরও বিকল্প নেই। প্রয়োজনে বাংলাদেশ-ভারত নদী সমস্যার সমাধানে তৃতীয় কোনো দেশ বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রাখতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের নদীগুলো সচল ও প্রবহমান থাকলে; নদীতে পানির ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো গেলে; রিজার্ভার তৈরি করা গেলে এবং সর্বোপরি উন্নয়নের নামে যেসব প্লাবন ভূমি, নিম্নাঞ্চল, বিল ও জলাধার ভরাট করা হয়েছে, সেগুলো উন্মুক্ত করা গেলে বন্যা নিয়ে কান্নার প্রয়োজন হবে না।
আমীন আল রশীদ: সাংবাদিক ও লেখক










Comments