কী শিখেছি এতো বছরে
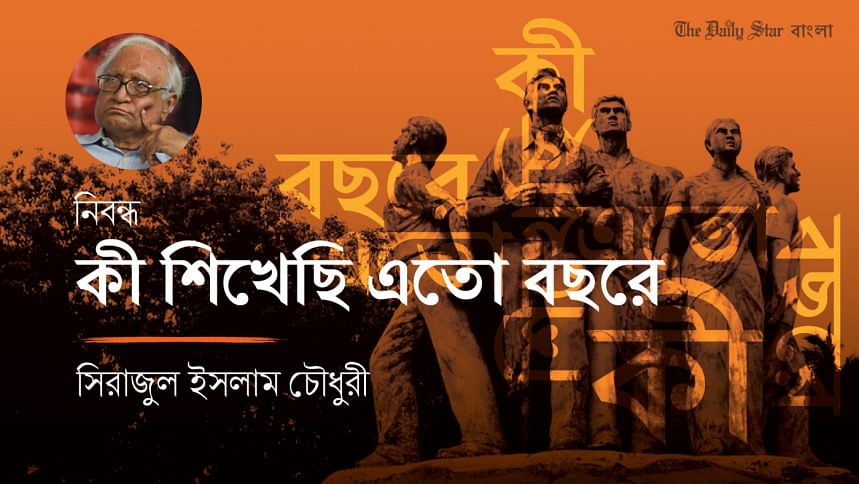
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমার প্রবেশ বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বছরে। তারপরে অনেক ঘটনা ঘটেছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে। কিন্তু সেই যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা, সেখান থেকে আর সরা হয়নি। ইচ্ছে করেই সরিনি। কিন্তু কি শিখেছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে? এক কথায় বলতে গেলে, বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি দুটি ব্যাপারে। একটি গ্রন্থমনস্কতা অপরটি সামাজিকতা। আলাদা আলাদাভাবে নয়, এক সঙ্গেই। ওই দুই বস্তু আমার ভেতর কতটি ছিল জানি না, যতটুকু ছিল তারা উভয়েই যে বিকশিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।
আমরা ঢাকায় এসেছি ১৯৪৮ সালে। তখন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশেই এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ভেতরেই পারিবারিকভাবে আমার বসবাস। কিশোর বয়সে যখন বাইরে থেকে দেখেছি, ছাত্র হয়ে ভেতরে প্রবেশ করিনি, তখন পুরাতন কলা ভবনের পাশ দিয়ে নিত্য যাতায়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি প্রতিষ্ঠান আমাকে খুব টানতো। একটি এর গ্রন্থাগার, অপরটি মধুর ক্যান্টিন। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির সকালে আরও অনেকের সঙ্গে আমিও পুরাতন কলা ভবনের আমতলা, গ্রন্থাগার ও মধুর ক্যান্টিনের মাঝখানে ঘটনা বিখ্যাত জায়গাটিতে ছিলাম। টিয়ারগ্যাসের তাড়া খেয়ে বাসায় ফিরে আসি। কিছুক্ষণ পরে শুনলাম গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। তখন আমি আই.এ. পরীক্ষার্থী। বছরের শেষ দিকে ফল প্রকাশ পেলো এবং আমি ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলাম।
আমার পিতা চেয়েছিলেন আমি অর্থনীতি পড়ি। আমার ভয় জমে ছিল গণিতে। অর্থনীতি বিদ্যাটি সে সময়ে আকীর্ণ ছিল গণিতের দ্বারা। তাই ও মুখো হওয়ার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। ভেতরে ভেতরে ইচ্ছা ছিল বাংলা বিভাগে ভর্তি হবো। তার কারণ সাহিত্যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। পরে পিতাপুত্রে সমঝোতা হয়েছে, আমি ইংরেজিতে ভর্তি হয়েছি। ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা তখন খুবই সহজ ছিল। হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টই ছাত্র বাছাই করতেন। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সফল শিক্ষার্থীদের একটা তালিকা তার টেবিলে থাকত। সেটা দেখেই অনুমতি দিয়ে দিতেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেই একেবারে হাতের কাছে পেয়ে গেলাম হাতছানি দেওয়া গ্রন্থাগার ও মধুর ক্যান্টিনকে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে গ্রন্থাগারে যাওয়া, সেখান থেকে বের হয়ে মধুর ক্যান্টিনে চা-সিঙ্গারা খেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে সম্ভব হলে আবার গ্রন্থাগারে ফিরে আসা। গ্রন্থাগার পুষ্ট করেছে আমার গ্রন্থমনস্কতাকে, আর মধুর ক্যান্টিন ছিল সামাজিকতার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র।
বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবনের ৪ বছরে শ্রেষ্ঠ সময় ছিল অনার্স পরীক্ষার আগের কয়েকটি মাস। পরীক্ষা দেওয়ার ঘটনাটা মোটেই আনন্দদায়ক হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু প্রস্তুতিটা ছিল নিজের ভেতর একটা জাগরণের মতো। তখন আমরা থাকতাম আজিমপুর সরকারি কর্মচারীদের আবাসিক এলাকায়। রোজ বিকেলে চলে আসতাম গ্রন্থাগারে। ফিরতাম রাতে, ৯টায় যখন গ্রন্থাগার বন্ধ হতো তার পরে। অজানা, কিন্তু নাম শোনা সব বই পড়ছি, নোট নিচ্ছি, ক্লাসে যেসব টেক্সট পড়ানো হয়েছে সেগুলো নতুনভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সে একটি মস্ত চাঞ্চল্য। ভুলবার নয়।
ও দিকে ১৯৫২ সালে ভর্তি হওয়ার মাস কয়েক পরেই দেখতে পেলাম, আমি হল সংসদের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গেছি, সদস্য পদে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বছরটা সবে মাত্র কেটেছে, মুসলিম লীগ বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলেছে। সেই ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে আমরা যারা দাঁড়িয়েছিলাম তারা সবাই অতি সহজেই নির্বাচিত হয়ে গেছি। এর আগে আজিমপুরে আমরা ছাত্রসংঘ গড়েছিলাম। সেখানেও একটা সামাজিক পরিসর তৈরি হয়েছিল। হল সংসদে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমি আরও বড় একটি সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম।
বিশ্ববিদ্যালয় তখন এত বড় হয়নি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বোধ করি আড়াই হাজার হবে, শিক্ষক ছিলেন মনে হয় দেড়শ জনের মতো। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জীবনটি ছিল প্রাণবন্ত। আবাসিক হলে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হতো, নির্বাচন তো ছিল রীতিমতো উৎসব। নিয়মিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো, হল বার্ষিকী প্রকাশিত হতো, তাতে আমরা লিখতাম। মতাদর্শিক তর্কবিতর্ক চলতো। কাছেই ছিল বেতার কেন্দ্র, বেতার অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগও পেয়েছি।
ওই যে আমার দুটি প্রবণতা—বই পড়ার আগ্রহ এবং সামাজিক হওয়ার ইচ্ছা, এরা পরস্পরের পরিপূরক ছিল গ্রন্থাগার ও মধুর ক্যান্টিনের মতোই। ছাত্রজীবন শেষ করে যখন শিক্ষক হলাম তখন আর মধুর ক্যান্টিনে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু পুরাতন কলা ভবনের ওপরেই ছিল শিক্ষকদের ক্লাব। ক্লাবকে মধুর ক্যান্টিনেরই উন্নত সংস্করণ বলে মনে হতো আমার। অন্য বিভাগের সমবয়স্ক শিক্ষকরা তো অবশ্যই, সরাসরি যারা আমার শিক্ষক ছিলেন তারাও প্রশ্রয় দিতেন। একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ক্লাবে যাতায়াতের দরুন। বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থমনস্ক ছিলেন বি.সি. রায়। তার সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হতো গ্রন্থাগারে, কিন্তু তিনি ক্লাবে আসতেন না। আমাদের অধিকাংশেরই ক্লাবে গিয়ে চা ও ডিমের অমলেট না খেলে চলতো না।
পেছনে ফিরে দেখি বই পড়ার ঝোঁক আমাকে যে গ্রন্থকীটে পরিণত করতে পারেনি, তার কারণ হলো সামাজিকতার বোধ। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তা নয়, বিশ্ববিদ্যালয় তারচেয়েও বড়। সে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও। বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে যে কোনো বৃদ্ধিই একাকী ঘটার নয়, তার জন্য অন্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বই তো আমাদেরকে বড় জগতেই নিয়ে যায়; অনুভবের, কল্পনার জগতের অনিঃশেষ যে পরিধি সেখানে প্রবেশের আহ্বান জানায়। প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।
বলছিলাম প্রথম বছরেই নির্বাচনে দাঁড়ানোর ব্যাপারটি ঘটেছিল। সেটি আকস্মিক নয়, বরং ছিল খুবই স্বাভাবিক। তারপরে সভা, সমিতি, আন্দোলন, সম্মেলন, পত্রিকা সম্পাদনা, বহু রকমের কাজ করেছি। কিন্তু বই আমাকে ছাড়েনি, আমিও বইকে ছাড়ার কথা ভাবতে পারিনি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে নানা রকমের প্রতিষ্ঠান আছে। শিক্ষকতা কালে তার অনেক কটিতেই আমি প্রার্থী হয়েছি। কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বাধ্য হয়ে। নির্বাচনে দাঁড়ানোটা কিন্তু অপরিহার্যই ছিল। পদের জন্য নয়, প্রতিবাদের জন্য। রাষ্ট্র ছিল স্বৈরাচারী, আমরা দাঁড়াতাম তার বিরুদ্ধে। আমাদের পূর্ব প্রজন্মের মানুষ ছিলেন সাতচল্লিশের দেশভাগের উপকারভোগী এবং ভুক্তভোগী, দুটোই। আমাদের প্রজন্ম বড় হয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। ওই আন্দোলনের প্রেরণাটি ভেতরে রয়ে গেছে, যে জন্য অবস্থান বদলানো সম্ভব হয়নি।
বলা হয়ে থাকে যে শিক্ষার মান নেমে গেছে। সেটি কতটি সত্য সেটা পরিমাপ করে বলা কঠিন। তবে গ্রন্থমনস্কতায় ও সামাজিকতায় যে ঘাটতি পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি কাঙ্ক্ষিত ছিল না। একাত্তরের বিজয়ের পরে মনে হয়েছিল একটি জাগরণ এসেছে। কিন্তু তাকে ধরে রাখা সম্ভব হলো না। আমরা পারলাম না, হেরে গেলাম। বইয়ের ব্যবহার কমেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে সাংস্কৃতিক জীবন নিতান্ত সীমিত। অবিশ্বাস্য হলেও তো সত্য এটা যে গত ২৬ বছর ধরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ছাত্র সংসদ নেই। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম এমনটা ভাবতেই পারতাম না। আমাদের জন্য শিক্ষার ৩টি জায়গা ছিল—ক্লাসরুম, গ্রন্থাগার ও ছাত্র সংসদ। মধুর ক্যান্টিন ছিল ছাত্র সংসদেরই অংশ।
সাংস্কৃতিক জীবনের স্তিমিত দশার পেছনে মূল কারণটি অবশ্য আর্থ-সামাজিক। সমাজে হতাশা দেখা দিয়েছে, শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের দিকে তাকালে আলো যত না দেখে তার চেয়ে অধিক দেখতে পায় অন্ধকার। তারা পড়ালেখায় উৎসাহ পায় না। হল সংসদে নির্বাচন নেই। বার্ষিকী প্রকাশিত হয় না। নাটক, গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা এসবের প্রতিযোগিতা প্রায় উঠেই গেছে। খেলাধুলায় নিয়মিত অনুশীলন ঘটে না। কিন্তু ব্যর্থতার দায়ভার কেবল অন্যদের ঘাড়ে চাপানোর উপায় নেই। আমরা যারা শিক্ষকতা করি তারাও পারিনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক জীবনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে। সামাজিক জীবন সাংস্কৃতিক জীবনেরই অংশ, একে অপরের ওপর নির্ভরশীলও বটে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই, সেই কথাটাই জোর দিয়ে বলবো। যদি দ্বিতীয় জীবন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তবে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকবো এ কথাই বলতাম।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়





Comments