তোমরা মর, আমরা বাঁচি!
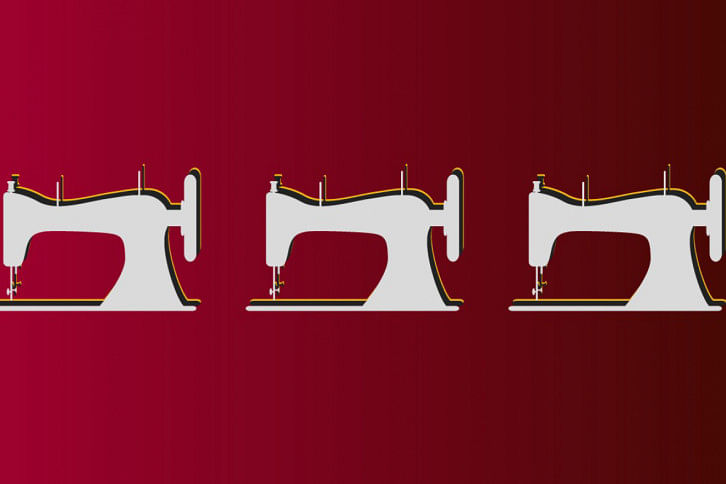
করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত পুরো বিশ্ব। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা বেছে নিয়েছে ‘তোমরা মর, আমরা বাঁচি’ নীতি। তারা আটকে রেখেছে বাংলাদেশি পোশাক রপ্তানিকারকদের পাঁচ বিলিয়ন ডলার। সেই সঙ্গে আশঙ্কা, ভবিষ্যতে কার্যাদেশ না পাওয়ার। সব মিলিয়ে ডুবতে বসেছে খাতটি। বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।
মূল্যছাড়, দেরিতে মূল্য পরিশোধ, নিলাম কিংবা কার্যাদেশ বাতিল!
এই বিকল্পগুলোই বাংলাদেশি পোশাক প্রস্ততকারক ও রপ্তানিকারকদের সামনে রাখছে আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও আমদানিকারকরা। করোনাভাইরাস মহামারির দুর্যোগ পুরোপুরি কেটে না গেলেও নিয়ন্ত্রণে এনে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে শুরু করেছে ইউরোপ। করোনা মহামারিতে যে বাণিজ্যিক ক্ষতি হয়েছে, তা প্রস্ততকারকদের পাওনা অর্থ থেকে পুষিয়ে নিচ্ছে আন্তর্জাতিক পোশাক ব্যবসায়ীরা।
ইউরোপ এবং আমেরিকায় করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার কয়েকমাস আগে পাঠানো পণ্যের দাম নিয়ে ত্রিমুখী সংকটে, ভাগ্যবান কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেশিরভাগ বাংলাদেশি পোশাক প্রস্ততকারক। অন্তত ২৫ জন পোশাক প্রস্ততকারকের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই জানতে পেরেছে দ্য ডেইলি স্টার।
তিন ধরনের সংকটে বাংলাদেশের পোশাক প্রস্ততকারকরা। প্রথম সংকট, যে পণ্যগুলো ইতোমধ্যে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে গেছে, কিন্তু তার মূল্য পরিশোধ করেনি- সেগুলো নিয়ে। দ্বিতীয় সংকট, যে পণ্যগুলো এখনও পড়ে আছে বন্দরে- সেগুলো নিয়ে। তৃতীয় সংকট, যে পণ্যগুলো এখনও বাংলাদেশের কারখানায় প্রক্রিয়াধীন- সেগুলো নিয়ে।
রপ্তানিকারকরা বলছেন, জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে তিন বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য পাঠানো হয়েছে, তার বেশিরভাগই ইউরোপীয় ও মার্কিন বন্দরে পড়ে আছে। এ ছাড়াও, আরও অন্তত দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রয়েছে ক্রেতাদের দোকানে। ২০১৯ সালের এই সময়ে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করা হয়েছিল, এবারও তাই হয়েছে। কিন্তু, গত বছরের মতো এবছর মূল্য পরিশোধ করেনি ক্রেতারা।
প্রায় সব ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে একই ধরনের উত্তর পাচ্ছেন রপ্তানিকারকরা। ক্রেতাদের মতে, করোনাভাইরাসের কারণে কয়েক মাস ধরে দোকান বন্ধ থাকায় কোনো বিক্রি হয়নি। এই বাণিজ্যিক ক্ষতির ভার নিতে হবে রপ্তানিকারকদেরও। কারণ, তারাও এই ব্যবসার অংশীদার।
যেসব পণ্য ইতোমধ্যে ক্রেতাদের দোকানে পৌঁছে গেছে, সেগুলোর দামও এখনই পরিশোধ করতে চাইছে না তারা। সেসব পণ্যের দাম তারা ছয় মাস পরে পরিশোধ করবে বলে চাপ দিচ্ছে। অনেকে আবার চাপ দিচ্ছে সেগুলো বিক্রি হওয়ার জন্য বছরের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।
বন্দরে আটকে থাকা পণ্য নিয়ে বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে হওয়া যোগাযোগ স্পষ্ট না। এগুলোর জন্য তিনটি বিকল্প আসছে রপ্তানিকারকদের সামনে। প্রথমটি, এসব পণ্যের জন্য হওয়া চুক্তিমূল্যের অর্ধেক দিতে চাইছে ক্রেতারা, সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দ্বিতীয়, পণ্যগুলো ফেরত নিয়ে আসতে হবে। আর তৃতীয়, ওই বন্দরেই পণ্যগুলো নিলামে বিক্রি করতে হবে।
যেসব পণ্য আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে পাঠানো হবে বলে বাংলাদেশে কারখানায় রয়েছে, সেগুলোর দামও ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হতে পারে।
উদাহরণ হিসেবে ধরা যায় যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠান দেবেনহামসের কথা। বাংলাদেশের ৩৫টি কারখানা গত দু’মাসে দেবেনহামসের জন্য ২৭ মিলিয়ন ডলারের পণ্য পাঠিয়েছে। অ্যাপারেল ইনসাইডার ডটকমের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেবেনহামস ইতিমধ্যে তার দোকানে থাকা ২০ মিলিয়ন ডলারের পণ্যের মূল্য দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে এবং বন্দরে থাকা সাত মিলিয়ন ডলারের পণ্যের জন্যও ১০ শতাংশ মূল্যছাড় চাইছে।
বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে রপ্তানিকারকরা। তাদের সামনে থাকা বিকল্পগুলো একেবারেই অযৌক্তিক। ক্ষতির ভাগ নিজেদের কাঁধে নেওয়ার মত পরিমাণে লাভ তারা করেনি। আর ক্রেতাদের কাছ থেকে পণ্যের মূল্য না পাওয়ার অর্থ কারখানাগুলো লে-অফ করে দিতে বাধ্য হবে মালিকরা।
বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সভাপতি রুবানা হক বলেছেন, ‘ইতোমধ্যে এক হাজার ১৫৩টি কারখানার তিন দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলারের কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘এর কারণে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে ২২ লাখ শ্রমিকের জীবনে। সেই সঙ্গে তাদের পরিবার তো আছেই।’
জানুয়ারি মাসে এবং ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে উইনার্স ক্রিয়েশনস লিমিটেডের পাঠানো প্রায় ১৮ মিলিয়ন ডলারের পণ্য এখনো পড়ে আছে উত্তর আমেরিকার বন্দরে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক দুর্জয় রহমান বলেন, ‘আমি ক্রেতাদের বারবার পণ্যগুলো নেওয়ার জন্য এবং অর্থ পরিশোধ করার জন্য বলছি।’
চট্টগ্রামের ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তাফিজ উদ্দিন দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, তার পণ্যের ক্রেতারা মূল্য পরিশোধের জন্য ১৮০ দিন বাড়তি সময় চেয়ে ইতোমধ্যে চিঠি পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, ‘এটা গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব না।’
সত্যিই, কয়েক দশক ধরে পোশাক ব্যবসা যেভাবে চলছে সেভাবে চলা উচিত ছিল না। এখানে ক্রেতা এবং আমদানিকারকরা ব্যবসার নিয়ম নির্ধারণ করে। যে নিয়মের মধ্যে দায়বদ্ধতা বা ঝুঁকি শুধুই পোশাক নির্মাতাদের কাঁধে।
লেটার অব ক্রেডিটের (এলসি) মাধ্যমে একটি টাকাও বিনিয়োগ না করে ক্রেতারা ব্যবসা করে যাচ্ছে। আক্ষরিক অর্থেই তারা অনৈতিক সুবিধা নিচ্ছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত থেকে। এলসির মাধ্যমে পোশাক নির্মাতাদের অর্থে পণ্য তৈরি করে সেগুলো পাঠানো হয় ক্রেতাদের কাছে। পণ্য পাওয়ার কয়েক মাস পরে নির্মাতাদের মূল্য পরিশোধ করে ক্রেতারা।
এর অর্থ দাঁড়ায়, তারা বাকিতে পণ্যগুলো কিনে নিয়ে বিক্রি করে। বিক্রি হওয়ার পর বিক্রিলব্ধ অর্থ থেকে পরিশোধ করে নির্মাতাদের পাওনা পরিশোধ করে। তাদের বিক্রি খারাপ হলে নির্মাতাদের কাছে ছাড় চায় এবং বাধ্য হয়ে নির্মাতারা তা মেনে নেয়। বছরের পর বছর ধরে এভাবেই চলছে।
এই ধারাতে ক্রেতারাই এখন ব্যবসার নিয়ম-নীতি ঠিক করছেন। ৭৫৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক বাজার এক বছরে করোনাভাইরাসের কারণে কতটা ক্ষতির মুখে পরবে, তা এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। তবে, রপ্তানি করা পণ্যের পাঁচ বিলিয়ন ডলার যদি শিগগির পরিশোধ করা না হয়, তাহলে বাংলাদেশের বেশিরভাগ পোশাক প্রস্ততকারক প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাবে বলে আশংকা করছেন রপ্তানিকারকরা।
বাংলাদেশের পাঁচ হাজার কারখানার প্রায় ৮০ শতাংশই সস্তায় পোশাক সরবরাহ করে বিশ্ব বাজারে। টি-শার্টের মতো অনেক পণ্যের জন্য ২০ বছর আগে যে দাম দিতো এখনও সেই একই দাম দেয় ক্রেতারা। এই সামান্য লাভের মধ্যে কারখানাগুলো কোনোরকমে টিকে আছে। সেখানে এই করোনার কারণে হওয়া লোকসানের বোঝা কাটানোর সাধ্য তাদের নেই। সেঞ্চুরি ডিজাইন অ্যান্ড ফ্যাশনস লিমিটেডের এক লাখ ডলার আটকে রেখেছে ক্রেতারা। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আজহারুল হক জানেন না কীভাবে ও কবে এই টাকা তিনি পাবেন।
আগামী তিন মাস সোয়েটার কারখানাগুলোর জন্য ব্যবসার মৌসুম। ক্রাউন ফ্যাশনস এবং ক্রাউন এক্সক্লুসিভসের মালিক রেজাউল আহসান কাঁচামাল এবং আনুষঙ্গিক সংগ্রহের জন্য প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডলারের কার্যাদেশের ৬০ ভাগ বিনিয়োগ করে ফেলেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় সোয়েটার রপ্তানিকারক এই প্রতিষ্ঠানের পুরো বিনিয়োগ এখন ঝুঁকির মুখে। তিনি বলেন, ‘আমি প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছি।’
পোশাক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো করোনা মহামারির মধ্যেও ছুটির মেয়াদ কমিয়ে কারখানা চালু করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই সবার মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন, তারা কেন এত মরিয়া?
এর কারণ সম্ভবত, রপ্তানিকারকরা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের জানাতে চাইছেন ‘আমরা প্রস্তুত’।
অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, ‘পোশাক নির্মাতাদের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনাম করোনার প্রকোপ থেকে দ্রুত বের হয়ে এসেছে। তারা ব্যবসার জন্য প্রস্তুত। বাংলাদেশের নির্মাতাদের কাছে যে কার্যাদেশ আছে তা ভিয়েতনামের কাছে চলে যাক তা তারা চায় না।’
বাংলাদেশের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের এই খাতটির জন্য সরকার ৫৮৯ মিলিয়ন ডলারের সহজ ঋণ ঘোষণা করেছে। তবে শুধু এই প্যাকেজ অবরুদ্ধ এই খাতটিকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বিজিএমইএ সভাপতি উল্লেখ করেছেন, এই শিল্পে প্রায় ৩৬ লাখ শ্রমিকের মাসিক বেতন ৪২৩ মিলিয়ন ডলার।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন অন্বেষণের চেয়ারম্যান রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর মনে করেন, মহামারির পর বিশ্ব বাজারে টিকে থাকার জন্য এই খাতের একটি টেকসই বেলআউট ফর্মুলা প্রয়োজন। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের মতো প্রতিষ্ঠান, নির্মাতা, ক্রেতা, সরকার এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলো একত্রিত হয়ে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের সূত্র তৈরি করেছে। এবারও একইভাবে কাজ করতে হবে।
তিনি সতর্ক করে জানান, এটা না করা হলে একটি বিশাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে।
নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাওয়া এই খাতটি সম্পর্কে নেতিবাচক চিত্র রয়েছে জনসাধারণের মনে। সবাই ভাবে, পোশাক প্রস্ততকারকরা শ্রমিকবান্ধব নয়, খুবই সামান্য বেতন দেয় এবং নিজেরা প্রচুর লাভ করে।
কিন্তু, বাস্তবতা হচ্ছে ২০১৩ সালের পর খাতটি বেশ কিছু সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং অনেক এগিয়েছে। এখন সময় এসেছে এই শিল্পকে সহায়তা করার। আর্থিক সহায়তা যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন কৌশলগত সহায়তা।
দীর্ঘমেয়াদী বেলআউট ফর্মুলার সাহায্যে দেশের চালিকা শক্তি হিসেবে পোশাক নির্মাণ শিল্পকে ফিরিয়ে আনা যাবে। একটি স্বল্পমেয়াদী অপরিকল্পিত সহায়তা এই শিল্পকে স্যালাইনের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা শিল্পে পরিণত করবে।
গার্মেন্টস খাত কি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পাবে? সে ভার সরকারের ওপর।
(সিনিয়র বিজনেস রিপোর্টার রেফায়াত উল্লাহ মৃধা তথ্য দিয়ে এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন)





Comments