সময়ের দুঃসাহসী কথাশিল্পী শহীদুল জহির

বাংলা সাহিত্যে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী শহীদুল জহির। পরিচিত এ অর্থে যে তিনি সমগ্র বাংলা কথাশিল্পে লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তবরীতির একনিষ্ঠ সাধনা করে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার রচনায় প্রথম এ রীতির প্রয়োগ ঘটেছে, না কি তার পূর্বেও কেউ কেউ এ রীতিতে লেখার চেষ্টা করেছেন, লিখেছেন, তা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও একবাক্যে শহীদুল জহির ও জাদুবাস্তবতা সমার্থক।
প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পারাপার' তাকে পরিচিতি দেয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে এই নূতন রীতির আমাদানি ও কারুকাজে 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাস ও 'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প' ছোটগল্প লেখায় যে পরিবর্তন আসে, তাতে পাঠক-সমালোচক চমকে ওঠেন। সাড়া পড়ে আমাদের শিল্প-সাহিত্যের চৌহদ্দিতে। অন্যদিকে শহীদুল জহির দ্রুতই উচ্চতর শিক্ষায় পাঠ্য হয়েছেন। দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ রয়েছে সেখানে তার ছোটগল্প কিংবা উপন্যাস অথবা উভয়ই পড়ানো হয়। তার সাহিত্য উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে।
প্রশ্ন হতে পারে, জাদুবাস্তবতা কী? এবং শহীদুল জহিরে এ রীতির রূপায়ণইবা কীরূপ? এই রীতির আমদানিতে আমাদের কথাসাহিত্য কি সমৃদ্ধ হয়েছে? না কি উন্মূল, ভাঙাচোরা ও জটিলতর হয়েছে কথাশিল্পের ফর্ম? এ রীতির উপযোগিতাইবা কতোটুকু? পরাবাস্তব ও জাদুবাস্তব কি একই ফর্ম, না কি ভিন্ন রীতি? শহীদুল জহির আমাদেরকে নূতন নূতন চিন্তায় চিন্তিত করে তুলেছেন!
জাদুবাস্তবতা হলো একটি সর্বভুক ও সর্বভূজ শিল্পফর্ম। প্রাচীন কালের বাচিক গল্প, লোককথা, রূপকথা, লোকশ্রুতি, ধাঁধা থেকে শুরু করে আধুনিক কালের উদ্ভট, ব্যাখ্যাহীনতা, পরাবাস্তবতা, প্রবল রহস্যময় অধিবিদ্যা, গোলকধাঁধা ইত্যাদি ছাড়াও সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চমকপ্রদ এই শিল্পপ্রয়াসে লুকিয়ে থাকে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল। এখানে শিল্পী যেন জাদুকর। জাদুর ইন্দ্রজালে বাস্তবকে উধাও করেন। পাঠক বা শ্রোতা প্রবেশ করেন জাদুর ইন্দ্রজালে বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে অন্য কোনো কল্পনার রাজ্যে। স্বাদ ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন ভিন্ন কিছুর। এ রীতির গল্প উপন্যাস পাঠান্তে পাঠক বাস্তবে ফিরে আসলে প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেন না গল্প বা উপন্যাসটির গূঢ়ার্থকথা। তবে গল্প বা উপন্যাসটি যে অন্যরকম তা উপলব্ধি করতে পারেন ঠিকই।
পরাবাস্তবতার সঙ্গে জাদুবাস্তবতার মৌলিক পার্থক্য হলো পরাবাস্তবের জগত ব্যক্তির ভেতরে তৈরি হয় আর জাদুবাস্তবের জগত সৃষ্টি হয় বাহিরে, সমষ্টির চারপাশের মধ্যে। ব্যক্তি এখানে গুরুত্বপূর্ণ; আবার ব্যক্তির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলও সমষ্টিগত মানুষ। ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে প্রবেশের এ এক অভিনব শিল্পরীতি। একসময় মার্কসবাদী সাহিত্য যে সমষ্টি চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে, জাদুবাস্তবরীতি সেই সমষ্টিগত চৈতন্যকে নূতন মাত্রা দান করেছে। যে কারণে 'পারাপার'-পর্বের মার্কসবাদী শহীদুল জহির জাদুবাস্তবরীতিকে আত্তীকরণ করতে পেরেছেন খুব সহজেই এবং পরবর্তীকালে এ রীতিতে সাহিত্যচর্চা করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই।
শহীদুল জহিরে জাদুবাস্তবতার যে রূপায়ণ ঘটেছে, তা অবশ্যই তার স্বদেশ ও রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে সংযুক্ত। বিশেষত রাষ্ট্রভাবনা ও রাজনৈতিক বিবেচনার বাহিরে গিয়ে তার কথাশিল্পকে বিশ্লেষণ করলে সেখানে অভিনবত্ব আর জাদুবাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা, এক সময় জার্মানে পোস্ট এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের চিত্রকর্মের মাধ্যমে জাদুবাস্তবতার জন্মই হয়েছিলো রাজনৈতিক ভঙ্গুরতা ও হিংস্রতার পরিপ্রেক্ষিতে। পরবর্তীতে লাতিন আমেরিকার বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক বাস্তবতায় তা সাহিত্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে শহীদুল জহির মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পরিপ্রেক্ষিতে যাপিত জীবনের বৃত্তাবদ্ধতাকে উন্মোচন করেছেন কিছুটা। যেমন :
উদ্ধৃতি-১ :
তখন দুটো জিনিস গ্রামের লোকদের একসঙ্গে মনে হয়, তারা প্রথমে বুঝতে পারে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার এই নির্বাচন করা হলো না এবং দ্বিতীয়ত, প্রায় পঞ্চাশ বছর ক্রমাগত অপেক্ষা করার পর এবার তারা হয়তো ভোট দেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াবে। কিন্তু সুহাসিনীর মানুষদের এই অপেক্ষার শেষ হয় না, কারণ কয়েক দিন পর তারা জানতে পারে যে, উপজেলা চেয়ারম্যানের পদের জন্য মাত্র একটি মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়, সেটা ইদ্রিস খাঁর মনোনয়ন, ফলে ভোটের আর প্রয়োজন পড়ে না; ইদ্রিস খাঁ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। ['সে রাতে পূর্ণিমা ছিল']
উদ্ধৃতি-২ :
পরবর্তী সময়ে এইসব মহল্লার লোকেরা বলে যে, ভজহরি সাহা স্ট্রিট বা ভূতের গলির লোকেরা এরকম সন্দেহ করে যে, তারা সময়ের একটি চক্রাবর্তের ভেতর আটকা পড়ে গেছে। কারণ কোনো একদিন, তখন, কোদাল হাতে মাটি কেটে আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ির ভেতরের একটি পাতকুয়ো বন্ধ করতে গেলে তারা দেখতে পায় যে, তাদের জীবনে সময়ের কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে, বর্তমান অতীতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে গেছে অথবা অতীত, বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। [কাঁটা, 'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প']
সমষ্টিগত মানুষের জীবনমানের আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে সাতচল্লিশের পর একাত্তর যে জাতীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি; সমষ্টিগত মানুষ যে দীর্ঘসময় ধরে কেবলই গোলকধাঁধায় ঘুরপাঁক খায়, খাচ্ছে, খেয়েই চলেছে; তারা যে আটকা পড়েছে একটি বৃত্তে, একটি ছকে, একটি কুয়োয়, একটি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কালনিরপেক্ষ সময়খণ্ডে, একটি অপরিবর্তনশীল নিয়তির চক্রাবর্তে, তা শহীদুল জহিরের গল্প উপন্যাসে বিচিত্রভাবে ইংগিতমুখর হয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিরা যে স্বাধীনতার পরপরই দেশে ফিরে আসে, সাধারণ ক্ষমার বদৌলতে সহাবস্থান করার সুযোগ পায়, রাজনীতিতে যে তাদের পুনর্বাসন ঘটে, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক চারটি মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার চারাগাছ যে অল্প সময়েই বিনষ্ট হয়। নির্বাচনহীনতার অপসংস্কৃতি যে নেতাদের পেয়ে বসে, প্রান্তিক পর্যায় থেকে উঠে এসেও যে মহান নেতারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ক্ষমতার মোহে, গণতন্ত্রচর্চার বিপরীতে হয়ে ওঠেন একনায়ক, স্বৈরশাসক ও স্বেচ্ছাচারী ইত্যাদি জাতীয় সংকট ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা শহীদুল জহিরের চিন্তাকে দেশ ও সমাজসংলগ্ন করে তোলে।
শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসে আশির দশক, 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' উপন্যাসে সত্তরের দশক এবং 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসে নব্বইয়ের দশক প্রেক্ষাপট হয়েছে। স্বাধীনতার পরের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে তার ছোটগল্পগুলোও। একমাত্র 'কাঁটা' গল্পে সাম্প্রদায়িকতার অভিঘাত ও সংখ্যালঘুদের জীবনবাস্তবতা ধরতে গল্পকার আশির দশকের পাশাপাশি আশ্রয় নিয়েছেন চৌষট্টি ও একাত্তরে। সে হিসেবে চৌষট্টি থেকে পুরো নব্বই পর্যন্ত কিংবা আরও কিছু পরের সময়কাল পল্লবিত হয়েছে তার কথাশিল্পে।
এই দীর্ঘ সময়ে দেশ জাতি সমাজ ও সংবিধানে পরিবর্তন এসেছে। রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু, শহীদুল জহির যে চিত্র আঁকলেন তাতে খুব একটা পরিবর্তন নেই। কেননা, তিনি বাহ্যিক পরিবর্তনের বিপরীতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন গুণগত পরিবর্তন। আমাদের সুবিধাবাদী রাজনীতিচর্চা সেই গুণগত পরিবর্তন আনতে পারেনি, এটাই হয়েছে তার মনোযন্ত্রণা এবং তার কথাসাহিত্যের গূঢ়ার্থকথা।
জীবন, রাজনীতি ও রাষ্ট্র অবলোকনে শহীদুল জহির যেমন ছিলেন নির্মোহ ও নিরপেক্ষ, তেমনি শিল্পসৃষ্টিতে ছিলেন চরমভাবে পেশাদার। যে কারণে বিশেষ কোনো দল, মত ও প্রতীকে তিনি বাঁধা পড়েননি। বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া দলটিকেই প্রথম দাঁড় করেছেন অভিযোগের কাঠগড়ায়। তেহাত্তরের সাধারণ ক্ষমা, চুয়াত্তরের একদলীয় শানসব্যবস্থা, ছেয়াশির নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির সঙ্গে নির্বাচনী জোট বাঁধা ইত্যাদি রাষ্ট্র ও দলটির জন্য যে ছিলো বড় ধরনের রাজনৈতিক ভুল, তা তিনি উপলব্ধিতে এনেছেন বারংবার।
বঙ্গবন্ধুর ছায়াপাতে সৃষ্ট 'ডুমুরখেকো মানুষ' গল্পের মোহাব্বত আলি জাদুগির এবং 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' উপন্যাসের মফিজুদ্দিন মিয়া হত্যাকাণ্ডের পূর্বাপর বিষয়াদি বিচার-বিশ্লেষণে বলা যায়, স্বাধীনতার মহানায়ককে তিনি রাজনীতিতে মডেল করেছেন বটে, কিন্তু আইডল করেননি।
রাজাকার ও সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠীর কদর্যতা ও নৃশংসতা শহীদুল জহিরের গল্প-উপন্যাসে ব্যাপক। সাত্তার ও জিয়া সরকারের সৌন্দর্যতত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা তার 'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই' গল্পে রয়েছে। তিনি যে প্রচণ্ডভাবে এরশাদবিরোধী ছিলেন, তাও আমাদের অজানা নয়। 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' গল্প এবং 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু' উপন্যাস এর বড় প্রমাণ। কিন্তু তিনি সর্বশেষ 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসে যে মুখ ও মুখোশ এঁকেছেন, তা বিশ্লেষণ করতে আমাদের আরও কিছু সময় প্রয়োজন। এভাবে শহীদুল জহির হয়ে ওঠেছেন মানহীন ভঙ্গুর রাজনৈতিক সময়াবহের এক দুঃসাহসী কথাশিল্পী। তবে তিনি প্রথাসিদ্ধভাবে প্রতিবাদী হননি। তার সৃষ্ট চরিত্ররা প্রতিবাদ করে না। বিষণ্ন, ক্লান্ত, বিভ্রান্ত, আতঙ্কিত ও সন্দেহগ্রস্ত চরিত্রগুলো শুধু দিন পার করে।
ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কথাশিল্পী শহীদুল জহিরের গল্প ও উপন্যাস যথার্থ অর্থেই অভিনব। বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির গুণে, জীবন ও রাষ্ট্রকাঠামো অনুসন্ধানে, গল্প-কাহিনি উপস্থাপন ও পরিবেশনার চমৎকারিত্বে এবং আঞ্চলিক ভাষাব্যবহারের নৈপুণ্যে তিনি বড় কথাশিল্পী। তার এই শিল্পপ্রয়াসে নূতন জাদুবাস্তবরীতির যে রূপায়ণ ঘটেছে, তা একদিন জাতীয় রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন এনে রাষ্ট্রকে সঠিক পথ দেখাবে বলে বিশ্বাস করি।





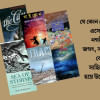

Comments