স্বাধীনতা যেমন জরুরি, পাশাপাশি মুক্তিও
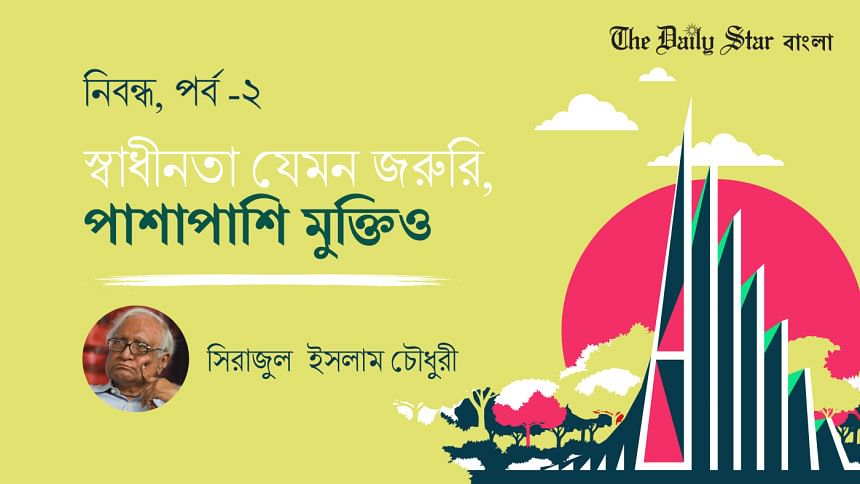
স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল নতুন সমাজ গড়বার জন্যই। এই দাবিটা কোনো বিলাসিতা ছিল না। ছিল প্রাণের দাবি। আশা ছিল এই যে, জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলে, শ্রেণি প্রশ্ন মীমাংসা করাটা সহজ হবে। কিন্তু শ্রেণি এমনই বস্তু যে সে মীমাংসিত প্রশ্নকেও অমীমাংসিত করে দেয়। বাংলাদেশ হবার পর যারা অনেক টাকা করেছে এবং পাকিস্তান আমলে কিছুটা সুযোগসুবিধা পাবার দরুন ও কিছুটা সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার কারণে যারা পাকিস্তানপন্থি ছিল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষাকারী যে প্রতিষ্ঠান বিএনপি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের অনুকরণে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধ্বনি তুলেছে।
অন্যদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ যে আওয়ামী লীগ তারাও সমগ্র জনগণকে নিজের সঙ্গে নিতে পারছে না। জনগণ দূরে থাকছে, কেননা তারা গরিব, তারা এক হবে কি করে ধনীদের সাথে? সমাজে বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। পাকিস্তান আমলে বৈষম্যটাকে স্থানীয়-অস্থানীয়র বৈষম্য বলে চিহ্নিত করা যেতো এখন সেটা করা সম্ভব নয়, কেননা এখন সকলেই স্থানীয়। বস্তুত জাতি এখন আর এক থাকছে না, দুই জাতিতে পরিণত হচ্ছে। আমরা এক নতুন দ্বি-জাতি তত্ত্বের দিকে এগুচ্ছি। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম জাতি গড়ছে না, শ্রেণি গড়ছে, জাতিকে সংহত না করে শ্রেণিকেই সংহত করছে।
মুক্তি আসেনি। আসছে না। না আসার প্রমাণ ও লক্ষণ বেশ স্পষ্ট। সংবিধান থেকে ধর্মরিপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ওই দু'টি দাবি এসেছিল মুক্তির জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা থেকেই। পাকিস্তান আমলে-তৈরি সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণিগত বিভাজনকে নাকচ করে দিতে চেয়েছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। মূলনীতি দু'টি যে বিদায় করে দেয়া হলো সেটা কোনো দুর্ঘটনা নয়, স্বাভাবিক ঘটনা বটে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ, আমাদের ইতিহাসের একমাত্র জনযুদ্ধ। জনযুদ্ধ জনতার জয় হয়েছিল। কিন্তু বিজয়ী জনতা ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছিল ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে, ক্ষমতা আগের মতোই চলে যাচ্ছিল অল্পকিছু মানুষের হাতে। পঁচাত্তরের নৃশংস পটপরিবর্তনের পর নতুন যারা ক্ষমতায় এলো তারা শুধু ক্ষমতাই বুঝেছে, অন্যকিছু বুঝতে চায়নি। তারা জনগণের লোক নয়, জনগণের আদর্শ তাদের নয়। তাদের আদর্শে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের স্থান ছিল না। তারা তাদের আদর্শকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তারপর ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই যারা ক্ষমতায় এসেছিল এবং আছেও তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে পরিচিত। কিন্তু কই তারাও তো সরিয়ে-দেয়া মূলনীতি দু'টি ফেরত আনে নি। ফেরত আনা পরের কথা, তারা সাংবিধানিক বৈধতাও দিয়ে দিয়েছে। এই উদাসীনতা তাৎপর্যহীন নয়। বাস্তবতা বদলে গেছে। জনগণ যে স্বপ্ন দেখেছিল তা এখন অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হয়তো-বা অতীতের স্মৃতিতেই পরিণত হবে, কারো কারো হয়তো মনে এমন আশা রয়েছে।
মূল সত্যটা হচ্ছে এই যে, জনগণের কাছে ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা থেকে তারা অনেক দূরে। সামরিক সরকারের আমলে দূরে ছিল, নির্বাচিত সরকারের আমলেও সেই দূরেই রয়ে গেছে। এই দুরত্ব আগামীতে বাড়বে না, বরঞ্চ কমে আসবে, এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি? তা তো বলা যাবে না। জনগণের ন্যূনতম চাহিদাগুলো মেটাবার জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচী কই? কর্মসংস্থানের উদ্যোগ কোথায়?
রাষ্ট্রক্ষমতায় যে বড় পরিবর্তন এসেছে সেগুলো এমনি এমনি ঘটেনি, বিত্তবানদের কারণেও ঘটেনি। প্রত্যেকটির পেছনেই জনগণ ছিল। ১৯৪৬-এ সাধারণ মানুষ ভোট দিয়েছে। ১৯৭১-এ সাধারণ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। তাতেই রাষ্ট্র বদলেছে। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা ছিল অপূর্ণ; ওই স্বাধীনতায় মুক্তি এলো না। উল্টো মানুষে মানুষে বৈষম্য বাড়লো। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা ভিন্ন প্রকারের, তার সামনে মুক্তির লক্ষ্যটা ছিল আরো স্পষ্ট, আরো প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই স্বাধীনতা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে কি? মুক্তি এসেছে কি মানুষের? সে তো মনে হয় অনেক দূরের ব্যাপার।
মুক্তি না-আসার কারণটি হচ্ছে এই যে, সংগ্রাম জনগণই করেছে এটা ঠিক, কিন্তু নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল না। জনগণের হাতে নেতৃত্ব থাকার অর্থ কি? জনগণ তো ব্যক্তি নয়, এক নয়, তারা বহু, অসংখ্য, কে নেতা হবে কাকে ফেলে? জনগণের হাতে নেতৃত্ব থাকার অর্থ হলো জনগণের স্বার্থ দেখবে এমন সংগঠনের হাতে নেতৃত্ব থাকা। স্বার্থটাই আসল কথা। আওয়াজ উঠতে পারে নানাবিধ, আওয়াজ মানুষকে উদ্বুদ্ধও করে নানাভাবে, কিন্তু ধ্বনি যথেষ্ট নয়, কার স্বার্থে ধ্বনি উঠেছে সেটাই জরুরি।
বাংলাদেশের জন্য গ্রামই ছিল ভরসা। আন্দোলনে গ্রাম না এলে জয় আসেনি। বিপদের সময় গ্রাম যদি আশ্রয় না দিতো তবে বিপদ ভয়াবহ হতো। গ্রামেই রয়েছে উৎপাদক শক্তি। গ্রামবাসীর শ্রমে তৈরি উদ্বৃত্ত মূল্য লুণ্ঠন করেই ধনীরা ধনী হয়েছে। এখনও গ্রাম কাজে লাগছে বিদেশ থেকে সাহায্য, ঋণ, দান ইত্যাদি এনে তার সিংহভাগ আত্মসাৎ করার অজুহাত ও অবলম্বন হিসেবে।
একাত্তরে আমারা গ্রামে গেছি। বাড়িঘর, মজা পুকুর, হারিয়ে-যাওয়া ক্ষেত, মৃতপ্রায় গাছপালা-এসবের খোঁজখবর করেছি। শহর তখন চলে গেছে শত্রুর কবলে, যাকগে, আমরা গ্রামেই থাকবো-এই সিদ্ধান্ত ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। শহরের পতন ঘটেছে সর্বাগ্রে, গ্রামের ঘটেনি, যদি ঘটতো তাহলে আমাদের পক্ষে অত দ্রুত জেতা সম্ভব হতো না।
কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র গ্রামে যারা গিয়েছিল তারা যত দ্রুতগতিতে গেছে তার চেয়ে দ্রুত গতিতে ফেরত চলে এসেছে। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া বাড়িঘর, কারখানা, অফিস, পদ, গাড়ি যে যেটা পেরেছে লুণ্ঠন করেছে। পাকিস্তানিরা অব্যাহতভাবে লুণ্ঠন করেছিল ২৪ বছর, বিশেষ করে নয়মাসে তাদের তৎপরতা সীমাহীন হয়ে পড়েছিল, তারা ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল সবকিছু। স্বাধীনতার পরে সুবিধাভোগীরা শোধ নিয়েছে। লুটপাট করেছে স্বাধীনভাবে। এখনও করছে।
গ্রাম রইলো সেখানেই যেখানে ছিল। বস্তুত খারাপই হলো তার অবস্থা। পাকিস্তানিরা হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন সব করেছে। ঘর পুড়িয়েছে, ফসল জ্বালিয়েছে। স্বাধীনতার পরে গ্রামবাসী পুরাতন জীবন ফিরে পায়নি। অবকাঠামো গিয়েছিল ভেঙে। বন্যা এলো। এলো দুর্ভিক্ষ। বিপুলসংখ্যক মানুষ একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লো।
গ্রাম এখন ধেয়ে আসছে শহরের দিকে। আশ্রয়দাতা হিসাবে নয়, আসছে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে। তার হাত দু'টি মুক্তিযোদ্ধার নয়, হাত তার ভিখারীর। ফলে শহর এখন বিপন্ন মনে করছে নিজেকে। ভাবছে আবার তার পতন ঘটবে- এবার পাকিস্তানিদের হাতে নয়, গরিব বাংলাদেশীদের হাতে। মনে হচ্ছে আবারও একটা মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন হবে।
না, তেমন যুদ্ধ ঘটবে না। কেননা মুক্তিযুদ্ধ তো চলছেই কোনো না কোনোভাবে। মানুষ যে মুক্ত হয়নি সেটা কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়। ওই যুদ্ধকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেটা বড় রাজনৈতিক দল দু'টি করবে না। তার জন্য বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন হবে। ডানদিকের নয়, বামদিকের।
বলা হয়, গণতন্ত্রের মানে হচ্ছে সংখ্যাগুরুর শাসন। কিন্তু আমাদের দেশে সংখ্যালঘুরা, অর্থাৎ ধনীরা শাসন করে সংখ্যাগুরুকে, অর্থাৎ গরিবকে। গণতন্ত্রের স্বার্থেই এই ব্যবস্থা চলা উচিত নয়। এটা চলবেও না। এই জন্য যে সংখ্যাগুরু সচেতন ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। তারা মুক্তি চায়। পরিবর্তন একটা ঘটবেই। প্রশ্ন হলো, কবে এবং কিভাবে। স্বাধীনতা ওই বড় পরিবর্তনের জন্যই প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নিজেই দুর্বল হয়ে পড়বে যদি জাতীয় মুক্তি না আসে।
মুক্তির প্রশ্নটি এখন আর আঞ্চলিক নয়। দ্বন্দ্ব এখন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নয়, প্রশ্নটি এখন শ্রেণিগত, দ্বন্দ্ব এখন বাঙালি ধনীর সঙ্গে বাঙালি গরিবের। বিষয়টা এমন পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেত না বাংলাদেশ যদি স্বাধীন না হতো। স্বাধীনতা আমাদের খুবই জরুরি ছিল, সমষ্টিগত অগ্রগতির পথে প্রথম সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ হিসাবে।





Comments